
দিনরাত্রিগুলি
সৈয়দ মনজরুল ইসলাম
প্রচ্ছদ: সব্যসাচী হাজরা
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের দিনরাত্রিগুলি উপন্যাসে লেখক গল্প বলতে চেয়েছেন। ব্যক্তির গল্প। গল্পটা সেখানে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু গল্প বলাটা, মানে বলার ভঙ্গিটা, মোটেই কম গুরুত্বের নয়। উপন্যাসে তো লেখকেরা গল্প বলেনই, লিখে বলেন। এখানে বলা হয়েছে মুখে। ফেলে আসা অতীতের নানা জটিলতা অপেক্ষাকৃত গোছানো বর্তমানে এসে হানা দিতে থাকলে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মনের চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়। তাকে ‘ইতিহাস’টা খুলে বলতে হয়। যে ঘটনাগুলো দীর্ঘমেয়াদি সংকটের কারণ হয়ে বর্তমান আর ভবিষ্যৎটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, সেগুলোতে বেশি আলো ফেলতে হয়। কথাগুলো এমন কাউকেও বলা যায়, যিনি লেখক; মানুষের মন নিয়ে কারবার করেন—আর সে কারণেই মানুষের কথা শোনার আগ্রহ বা ধৈর্য তার আছে। এ উপন্যাসের পোড় খাওয়া মানুষটি তা-ই করেছে। তার ইতিহাসটা শুনিয়েছে চিকিৎসক আর লেখককে। আমরা ফাঁকতালে শুনে নিয়েছি।
এই যে বলা আর শোনা—দিনরাত্রিগুলি উপন্যাসে এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। কেবল ভঙ্গির আরাম নয়, আরও বেশি কিছু। স্মৃতি ধারাবাহিকতা মেনে কাজ করে না। আর সেই স্মৃতি যদি বর্ণিত হয় মনের গোলমাল শনাক্তির কাজে, তাহলে তো গৌণ-মুখ্যের রদবদল হবেই। কার্যকারণ-সম্পর্কের হিসাব মেলানোর দরকারে ঘটনার ক্রম বদলে যাবে। এই দুই বস্তু মিলে গল্পটা সারল্যের আরাম হারিয়েছে; কিন্তু আয় করে নিয়েছে আবশ্যিক জটিলতার সৌন্দর্য। এখানে গল্পকথকের পরিচয়টাও দরকারি। সমাজবিজ্ঞানের পিএইচডির এই মার্জিত ভদ্রলোক ঠিক সমাধানের আশায় চিকিৎসকের কাছে যাননি। নিজের সমস্যা তিনি ভালোই জানেন। এ-ও জানেন, অতীতের যেসব দুর্ঘটনা তাকে স্মৃতি-রোমন্থনের আরাম থেকে চিরবঞ্চিত রেখেছে, সেগুলোর দায় তার নিজের নয়। যদিও সে ফলভোগী। নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ ঘটনাগুলো বয়ান করে সে। নিজের স্বরে। ব্যক্তির স্বরের আধিপত্য এ উপন্যাসের ভাষাভঙ্গির সবচেয়ে গুরুতর বৈশিষ্ট্য। সে এমনই যে অন্যের কথা—এমনকি সংলাপও—কথকের নিজের স্বরে-সুরে উচ্চারিত হয়। তাতে উপন্যাসসুলভ বহুস্বরতায় টান পড়ে। কিন্তু তৈরি হয় অন্য ধরনের উপভোগ্যতা—না চটুল না ভারী, এমন এক প্রমিত বাংলায় জটিল এক গল্প অনায়াসে বলা হয়ে যায়।
দিনরাত্রিগুলি উপন্যাস নানা কারণে আকর্ষণীয়। গল্পের আকার বা প্লটে নতুনত্ব আছে। ঝকঝকে স্মার্ট ভাষার সৌন্দর্য আছে। আরও আছে ব্যক্তির গল্পে সমাজ-প্রতিবেশকে যথাসম্ভব এঁকে দেওয়ার সাফল্য। কিন্তু বাংলাদেশের সমসাময়িক কথাসাহিত্যে এ উপন্যাসের বিশেষ অর্জন মুক্তিযুদ্ধের এক নিরাসক্ত কথকতায়। আমাদের বলা হয়েছে, গল্পকথক ছোটবেলা থেকেই ওস্তাদ গল্প-বলিয়ে। আরও জানানো হয়েছে, নিজের গল্প নয়, সে বলতে পছন্দ করে অন্যের গল্প। মুক্তিযুদ্ধে নিজের অংশগ্রহণের যে অভিজ্ঞতা সে বর্ণনা করেছে, তা এ অর্থে অন্যের গল্পই বটে। অন্যের বলেই নিজের। দশের সঙ্গে একের একাকারতা আর তার মধ্যেই একের স্বাতন্ত্র্য—এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক প্রস্তাব। মুক্তিযুদ্ধের মতো বড় ঘটনা, যেখানে বিদ্যমান সমস্ত সম্পর্ক নতুন করে নানা মাত্রায় বিন্যস্ত হতে থাকে, যেখানে বর্তমানের প্রচণ্ডতা অতীত আর ভবিষ্যৎকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেয় না, সেখানে ব্যক্তি-সমষ্টির অধীন হবে —এ-ই তো স্বাভাবিক। লেখক অবশ্য শুরু করেন একটু আগে থেকে। সেখানে কথককে আমরা শ্রেণী-রাজনীতিতে সক্রিয় দেখতে পাই। এখানে শ্রেণী-রাজনীতির মূল্যায়ন আছে। সিদ্ধান্ত আছে। এই মূল্যায়ন বা সিদ্ধান্ত যথেষ্ট গভীরতা পায়নি বলেই মনে হয়। কিন্তু বিকল্প রাজনৈতিক ধারাগুলো সত্তরের নির্বাচনের পর যে কার্যত জাতীয়তাবাদী জোশের আওতায় এসেছিল, সে কথা সত্য। যুদ্ধের কিছু অপারেশন-চিত্র আছে এ উপন্যাসে। সুন্দর। বানানো।
জাদুর মতো বাস্তব ওই সময়টাতে যে রকম হয়েছিল বা হওয়া সম্ভব—ঠিক সে রকম। ঘটনা বা সময়কাল হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ যথোচিত মহিমান্বিত হয়েছে। তাতে যুক্ত হয়েছে দুটি বিশিষ্টতা—আমাদের মুক্তিযুদ্ধচর্চায় যা খুব সুলভ নয়। এক. প্রচলিত মহাবয়ানকে ক্ষেত্রবিশেষে চাপে ফেলে দেওয়া বা সীমানা প্রসারিত করা; দুই. মুক্তিযুদ্ধকে শয়তান-ফেরেশতার স্থির-নির্দিষ্ট ছকে বিন্যস্ত না করা। হুমায়ূন আহমেদের কথাসাহিত্য-সিনেমা-নাটকে এ বস্তু দেখা গেছে। আরও দু-চারজনের গুটিকতক রচনায়ও। দিনরাত্রিগুলি এ বিরল তালিকায় যুক্ত হলো। ব্যক্তির গল্প বলার আন্তরিকতা সবল কবজিতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলেই এ অর্জন সম্ভবপর হয়েছে।
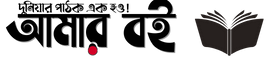

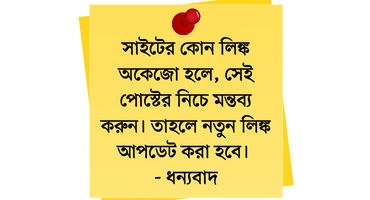
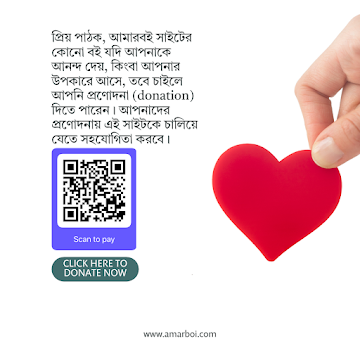






![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)








