 রঙরুট - বরেন বসু (উপন্যাস)
রঙরুট - বরেন বসু (উপন্যাস)যাঁরা বরেন বসুকে মনে রেখেছেন, তাঁরা মূলত এই উপন্যাসটির জন্যই রেখেছেন। ‘রঙরুট’ কথাটা এসেছে ইংরেজি রিক্রুট থেকে, রিক্রুটই ফৌজি জিহ্বাতে বিকৃত হয়ে রঙরুটে রূপান্তরিত। যদিও উপন্যাসে সন-তারিখের উল্লেখ নেই, বুঝতে পারি হিটলার-স্টালিনের ১৯৩৯-এ সম্পন্ন মৈত্রী চুক্তি ভেঙে ১৯৪১-এ জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ আর পয়লা ডিসেম্বর জাপানের পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণের ঘটনা থেকে ‘রঙরুট’-এর শুরু। একদিকে তখন জাতীয় কংগ্রেস যুদ্ধে ভারতীয়দের যোগ দিতে বারণ করছে, কারণ যুদ্ধে যোগ দেওয়া বা সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখানো মানে ব্রিটিশ শাসনকে শক্তি জোগানো, অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ডাক দিচ্ছে ফ্যাসিস্ট-নাত্সিদের অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য মিত্র বাহিনীতে তথা জনযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে। এই দুই বিপরীতমুখী আকর্ষণে দীর্ণ হতে হতে ‘রঙরুট’-এর নায়ক অমল বেকারত্বের জন্য বাড়ির গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে, যুদ্ধের বাজারে মওকা বুঝে দাঁও মারার পথে যাওয়ার সুযোগ ছেড়ে, শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীতেই যোগ দেয়।
প্রশিক্ষণের প্রথম পর্বেই অমল জেনে যায় ট্রেনিং সেন্টার মানে সরাইখানা, সোলজার মানে স্লেভ, মিলিটারি মানে স্লেভারি আর সেনাবাহিনীর কোম্পানি স্লটারহাউস। হাত তুলে নমস্কার করার ‘সিভিলিয়ান কায়দা এখানে চলে না’। প্রশিক্ষণ শেষে কোম্পানি ক্যাম্প থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে ট্রেনে করে যাত্রা অসম সীমান্তের অভিমুখে। সংবেদনশীলতা, সহানুভূতি, হৃদয়বৃত্তি ইত্যাদি ছাড়তে ছাড়তে অমল ক্রমশ নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে তার নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, বুঝতে শেখে যে, উপরের অফিসাররা সর্বদা সচেষ্ট থাকে যাতে নিচের স্যাপার সৈনিকদের মধ্যে কোনও ঐক্যবন্ধন গড়ে না ওঠে, তাদের মধ্যে যেন বিবাদ-বিভেদ-বিভাজন বজায় থাকে।
তাদের ট্রেন যখন পার্বতিপুর জংশনের ইয়ার্ডে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তখন অসম থেকে এল এক ট্রেন বোঝাই মুর্গিঠাসা-দশায় ইভ্যাকুয়ি, জাপানিদের হাত থেকে কোনওমতে দেহখানি নিয়ে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু প্রাণটুকু কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবে জানে না। পরদিন অমলরা পৌঁছল আমিনগাঁও। ফাঁক পেয়ে ব্রহ্মপুত্রের ফেরিঘাটে গিয়ে দেখল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত ছেঁড়াখোঁড়া উর্দিধারী বুভুক্ষু সশঙ্ক ইভ্যাকুয়ি সেনারা জাহাজ থেকে নামছে টলতে টলতে। তাদের একজন মাটিতে পড়ে গেলে আর-একজন জখমি সেনা নির্বিকারভাবে জানাল, মাটিতে যে একবার পড়ে সে আর ওঠে না, তার বুকের ওপর দিয়েই পেছনের জন এগিয়ে যায়। এই পর্যন্ত পড়েই আমরা সেনাবাহিনীর বহুঘোষিত গৌরব-মহিমার আড়ালে লুকনো নিষ্ঠুর বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপ চিনতে পারি। যুদ্ধের বীভত্স ঘূর্ণাবর্ততেও মধ্যে মধ্যে দেখা যায় উষ্ণ হৃদয়বত্তার ঝলক- নিজের মেয়েকে ইভ্যাকুয়েশনের পথে হারিয়ে মা-বাপ হারানো আর-একটি মেয়েকে বুকে তুলে নেওয়ার কাহিনি।
অমলদের কোম্পানি পাণ্ডুতে পৌঁছলে খবর পেল আগস্ট বিপ্লবের। ভারতীয় সেনাদের জীবনে সে এক মহাসংকট! ওখানে বিপ্লবীরা যুদ্ধ করছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আর এখানে তারা কিছু টাকা আর অফিসারদের গালি-লাথির বিনিময়ে যুদ্ধ করছে ব্রিটিশদের কায়েম করার জন্য। ক্যান্টিনের রেডিয়োতে বা মণিপুর রোড স্টেশন বাজারে যুদ্ধের খবরাখবর তারা সবই জানতে পারে আর তাদের সূত্রে তেতাল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত, মানে যুদ্ধকালীন বিশ্ব তথা দেশ ও বিদেশের জীবন ও সময় সম্বন্ধে একটা জীবন্ত তথ্যচিত্র আমরা পেয়ে যাই ‘রঙরুট’-এ। যে-ঘটনাস্থলে অমল উপস্থিত নয়, বিশেষত জাপানিদের নাগা পাহাড়গুলো দখলের উত্তেজক বৃত্তান্ত বিশদভাবেই পরিবেশিত হয়েছে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে। উত্তর আফ্রিকায় জার্মানিকে ঘায়েল-করা দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ সেকেন্ড ডিভিশনও পর্যুদস্ত হল জাপানিদের হাতে, তখন পাঠানো হল ফিফ্থ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ডিভিশনকে, তারা নাগা পাহাড়গুলো পুনর্দখল করল, কোহিমাকে বলা হল এশিয়ার স্টালিনগ্রাড।
অনেক নাটকীয় ঘটনা, বিচিত্র বিভিন্ন চরিত্রের কুশীলব, কাহিনিস্রোতে প্রচুর মোড়-মোচড়, ১৯৫০-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসের মূল ঘটনাবলি সকলের জানা থাকলেও লেখার গুণে শেষ পর্যন্ত পড়ার জন্য পাঠকের আগ্রহ সারাক্ষণ টান-টান থাকে, এমনকী পঁয়ষট্টি বছর পরেও। যেসব চরিত্র উপন্যাসের শুরুতে ভবিষ্যত্ সম্বন্ধে অনিশ্চিত ছিল, সন্ত্রস্ত ছিল অফিসারদের দাপটে, আস্তে আস্তে তারাও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিখল, যুদ্ধশেষে অফিসারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে আওয়াজ তুলল, ‘ব্রিটিশ-ভারত ছাড়।’ অভিজ্ঞতার অভিনবত্বে, ঘটনার ঘনঘটায়, পটভূমির বিশালতায়, চরিত্রের প্রাচুর্যে ও বর্ণাঢ্যতায়, যুদ্ধের বিরোধিতায় ও শান্তির সমাচারে ‘রঙরুট’ পেয়েছে এক মহাকাব্যিক উচ্চতা। দেশকে জাপানি কবলমুক্ত করার পরেও অমলের বিভ্রান্তি কাটে না। ‘প্রশ্নের পর প্রশ্ন বারবার তাকে খোঁচা দিচ্ছে, কেন এই মানুষগুলো মরেছে। কি জন্যে মরেছে? কার জন্যে মরেছে? মৃত্যুর এই বিরাট জৌলুস তার মনকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছে। যুদ্ধের নামে এই নরমেধ যজ্ঞ কার হিতার্থে? কোথায় বসে কারা এই ষড়যন্ত্র ফেঁদে চলেছে?’ এইসব প্রশ্ন ‘রঙরুট’ পড়া শেষ করার পরেও পাঠককে খোঁচা দিতে থাকে।
Download and Join our Facebook Group
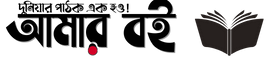

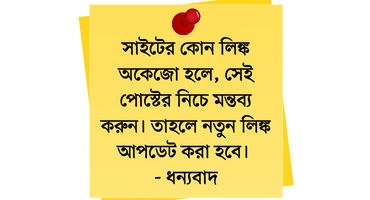
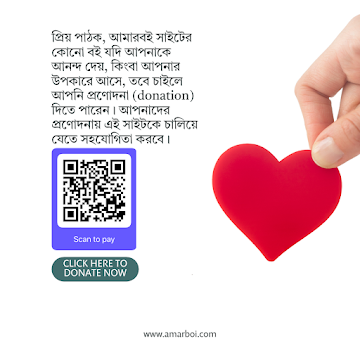







![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)









0 Comments