 ঢাকাইয়া কুট্টি ভাষার অভিধান
ঢাকাইয়া কুট্টি ভাষার অভিধানসংকলন ও সম্পাদনা:
মোশাররফ হোসেন ভূঞা
ঐতিহ্য ।
ঢাকার কুট্টিদের সম্বন্ধে বহু বাঙালিরই একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। অনেকেই মনে করেন, কুট্টিরা ঢাকার ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান। ওটাই তাদের একমাত্র পরিচয়। কিন্তু যাঁরাই ঢাকাকে জানেন, বা ঢাকার ভাষার ইতিহাসটা কিছুমাত্র জানেন, তাঁদের পক্ষে একথা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, কুট্টি বলতে ঢাকার ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদেরই কেবল বোঝায় না। এরা ছাড়াও নানান কারিগর, ঠ্যালাওয়ালা, রিকশাওয়ালা, যারা ধান কোটার কাজ করে বা করত, এমনকী যারা ইটভাটার কর্মী অর্থাত্ যারা ইট ভাঙার বা কোটার কাজ করে, তারাও কুট্টিশ্রেণিভুক্ত মানুষ।
‘কুট্টি’ কথাটার উত্পত্তি সম্বন্ধে নানা মত শোনা যায়। কেউ বলেন, ‘কুঠি’ থেকেই কুট্টি এসেছে। আর-একটা মত, ধান বা ইট কোটার কাজ করত বলেই এদের কুট্টি বলা হয়ে আসছে। একসময় শহরতলিতে বাস করত এরা। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র, সর্বত্র। এদের উদ্ভব মোগল আমলে। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে চাল ছিল পূর্ববঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি-পণ্য। বহু মানুষ ধান ভানার বা কোটার কাজে নিযুক্ত হত। এরাই আদি কুট্টি। এই মত পাওয়া যায় রঙ্গলাল সেনের ‘রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তরকাল’ বইয়ে। এর সমর্থন পাওয়া যায় হাফিজা খাতুনের ‘Dhakaiyas on the Move’ বইয়েও।
কুট্টিদের ভাষা ঢাকাইয়া ভাষার একটা প্রধান উপাদান। ঢাকার মানুষের সঙ্গে অবাঙালি ব্যবসায়ী কারিগর প্রভৃতির ভাষার মিশ্রণের ফলই কুট্টি ভাষা। অর্থাত্ কুট্টিরা প্রায় প্রথম থেকেই একটা মিশ্র ভাষায় কথা বলত। অতএব বলাই যায় যে, কুট্টি ভাষা এক ধরনের ‘ক্রিয়োল’। কুট্টিদের ভাষা প্রথম দিকে ছিল প্রান্তিক মানুষের ভাষা, তাই এই ভাষা শহুরে শিক্ষিত লোক, রাজকর্মচারী প্রভৃতি মানুষজন তেমন ব্যবহার করত না। কালক্রমে কুট্টিদের বাসস্থান আর পেশা দুইয়েরই বদল ঘটেছে। ফলে যাঁদের উত্পত্তি কুট্টি থেকে, তাঁরা আজ বহু মর্যাদাশালী পেশায় নিযুক্ত। অনেকসময় তাঁরা মনেই রাখেন না যে, তাঁরা কুট্টি সম্প্রদায়েরই উত্তরপুরুষ। আর তাঁদের ভাষায়ও ঘটেছে বিস্তর রূপান্তর, বলা বাহুল্য সেই রূপান্তরের ঝোঁকটা পরিশীলনের দিকে।
অবশ্য এই কথাটা মানতেই হবে যে, গরিব ঢাকাইয়া কোচওয়ান বা গাড়োয়ানরা কুট্টি ভাষার আদি রূপটি বজায় রেখেছেন। এই ভাষায় রয়েছে বাংলা উর্দু হিন্দির মিশেল। ফারসিও এসেছে বটে, তবে মূলত উর্দুর মারফতে। অবশ্য মূল উপাদান উপভাষিক বাংলা। বলতেই হয়, কুট্টি ভাষার আদি রূপটি এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে। আজ কুট্টি বলতে যে-মানুষদের বুঝি, তাঁরাও যে-ভাষায় কথা বলেন তা মূলত কুট্টি ভাষা থেকে সরে এসেছে অনেকটাই। ঢাকাইয়া কুট্টিদের রঙ্গরসিকতা এখনও মরে যায়নি অবশ্য। ভাষাগত কারণে এবং সামাজিক কারণে কুট্টি ভাষা অবশ্যই সংরক্ষণীয়।
কুট্টি ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও দু’-চার কথা বলা দরকার। এই ভাষায় ঘৃষ্ট চ-বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনির কিছুটা তীব্র উচ্চারণ শোনা যায়। ঘৃষ্ট সঘোষ জ হয়ে যায় দন্তমূলীয় সঘোষ উষ্মধ্বনি অর্থাত্ z বা জ়। তালব্য শ প্রায়ই হ-তে রূপান্তরিত। শালা হয়ে যায় হালা। প্রতিবেষ্টিত তাড়িত ড় হয়ে যায় দন্তমূলীয় কম্পিত র। অপিনিহিতির প্রভাব খুবই বেশি। আইজ, কাইল, থাউক, জ়াউক ইত্যাদি। মহাপ্রাণতার ক্ষীণতাও একটা বৈশিষ্ট্য। ঝ >জ, ঘ > গ, ভ > ব।
কুট্টি ভাষা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে এই আক্ষেপ শোনা যায় প্রায়ই। তাকে ধরে রাখার একটা প্রয়াস দেখতে পাওয়া গেল মোশাররফ হোসেন ভূঞা-র ‘ঢাকাইয়া কুট্টি ভাষার অভিধান’ বইটির প্রকাশে। স্বীকার করতেই হবে, এই প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রায় চার হাজার মুখশব্দের বিবৃতি আছে এতে। সংকলক স্বীকার করেছেন, তিনি শব্দ সংগ্রহ করেছেন প্রধানত বইপত্র দেখে। ক্ষেত্রজরিপের মাধ্যমে শব্দ সংগৃহীত হলে শব্দ যেমন বাড়ে, তেমনই তার বিশ্বাসযোগ্যতাও বাড়ে। কেননা, এসব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজরিপই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। বিষয়টা সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত। এর সঙ্গে বার্নস্টাইন-এর ঘাটতিতত্ত্ব (deficit theory) আর সমাজভাষার (sociolect) একটা সম্পর্ক আছে।
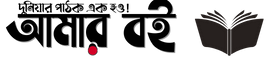

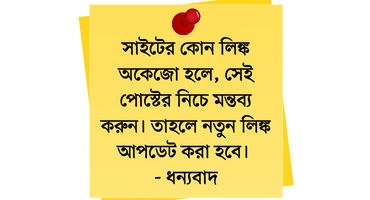
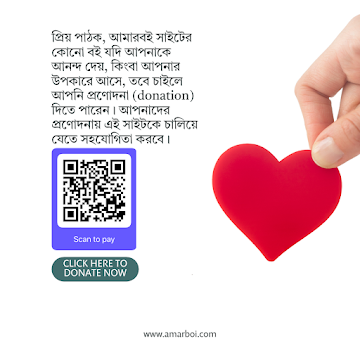






![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)








