
ঠাকুরের সহিত বিচার
বাংলা বানানে হ্রস্ব ইকার
সলিমুল্লাহ খান
‘আজ ৮০-৯০ বছর পর্যন্ত বাংলা বানানে হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ নিয়ে যত আলোচনা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, এত আর কোনো বানান নিয়ে হয়নি।’
-মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (বাংলা বানান, দে’জ ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৫) আমার ‘বাংলা বানানের যম ও নিয়ম’প্রবন্ধ (নতুনধারা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭) বাহির হইবার পর দাতা হিতৈষী ও পরোপকারী বন্ধুরা বলিয়াছেন, ‘তুমি উষ্ণ হইয়াছ যে? এই বয়সে মানুষের শোণিত তো শীতল হইবার কথা, কথা শীতল হইবার কথা।’ আপনারা আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। জানিবেন রক্তে বসন্তরোগের শিকার আমি একা হই নাই। এই বিষয়ে আমার উত্তমর্ণ আছেন।
“যে পণ্ডিতমূর্খেরা ‘গভর্ণমেন্ট’ বানান প্রচার করতে লজ্জা পাননি তাঁদেরই প্রেতাত্মার দল আজও বাংলা বানানকে শাসন করছেন- এই প্রেতের বিভীষিকা ঘুচবে কবে? কান হলো সজীব বানান, আর কাণ হলো প্রেতের বানান এ কথা মানবেন তো?’
-কে লিখিয়াছিলেন এই সকল কথা? আর কেহ নয়, স্বয়ং মহাত্মা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯৮-৯৯) বাংলা বানানের রাষ্ট্রে ‘বিপ্লব’আনিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার তুলনা তিনি নিজেই। একান্ত কাঁহারও সহিত তাঁহার তুলনা করিতেই হয়- তো আমি শুদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ বিদ্যাসাগরের নাম লইব। ১৮৫৫ ইংরেজি [সংবৎ ১৯১২] সালে বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ছাপা হয়। প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরের উপরে যাহা লেখা গিয়াছিল তাহাতে এসায়ি উনিশ শতকের বিপ্লব চরমে দেখা যায়। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ লিপিকালে এই বিপ্লব সম্পন্ন হয়।
‘বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋকার [রিকার] ও দীর্ঘ ৯ কারের [লিকারের] প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য, ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর, চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এ জন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে’ (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১২৪৯)
অন্যূন কুড়ি বছরের ভিতর বর্ণপরিচয়ের কমসে কম ষাটটি সংস্করণ হইয়াছিল। ষাটি সংস্করণের বিজ্ঞাপনেও সেই ঘটমান বর্তমানের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন: ‘প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ, এই দুই বর্ণস্থলে স্বরের অ, স্বরের আ, বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা, সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ, এইরূপ বলে, তদ্রুপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।’ (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১২৫০)
প্রসঙ্গ যখন উঠিলই বলা অবিধেয় হয় না, আমার- মানে এই গরিব লেখকের- জন্ম বর্ণপরিচয়ের একশত কয়েক বছর পর। কিন্তু আমাকে সেই সদুপদেশ কেহ দেন নাই। আমিও স্বরের অ, স্বরের আ-ই বলিয়া থাকিব। সন্দেহ কি? যাহা বাছুরকে দেওয়া হয় নাই তাহা ষাড়ে দিয়া কোন লাভের মুখ দেখা যায় না। তথাপি বিদ্যাসাগরের গৌরব ম্লান হইতেছে না। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হইতেছে। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা লিখিয়াছেন :
‘যে সকল শব্দের অন্ত্য বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত, উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত-কর, খল, ঘট, জল, পথ, রস, বন ইত্যাদি। অকারান্ত- ছোট, বড়, ভাল, ঘৃত, তৃণ, মৃগ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ শব্দ মাত্রেই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।’(বিদ্যাসাগর রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১২৫০)
মনে পড়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩০৫ ও ১৩০৮ সালে রাজা রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ ধরিয়া তাঁহার সহিত এই হলন্ত ও অকারান্ত উচ্চারণ বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ৫৫, ৯১) দশ বছর পরও তিনি রামমোহনের উল্লেখ করিয়া একই কথা সামান্য ঘুরাইয়া লিখিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরের উল্লেখই করিলেন না। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ১৩৮)
শুদ্ধ কি তাহাই? তাঁহার আয়ু যখন ৭৭ বছরে পড়িয়াছে তখনও রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি ছাড়েন নাই। তখনও তিনি তত্ত্ব করিলেন, বাংলা ভাষায় দুই অক্ষরবিশিষ্ট বিশেষণ পদ প্রায়ই স্বরান্ত হইয়া থাকে। ঠাকুর লিখিলেন, “তার কোনো ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় অতি অল্প।”(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭১)
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কোথাও বিদ্যাসাগরের ঋণ স্বীকার করিলেন না, যদিও একেলা ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’গ্রন্থেই পাঁচ জায়গায় বিদ্যাসাগরের উল্লেখ প্রসঙ্গত পাওয়া যাইবে। ভাবিতেছিলাম, শুদ্ধ স্বদেশে কেন স্বকালেও যোগী মাঝে মাঝে ভিখ্ পাইবেন না।
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপর সংযোজন, বাংলা তকারের ত ও ৎ এই দ্বিবিধ কলেবর। দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড তকার। ‘ঈষৎ, জগৎ, প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময়, খণ্ড তকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে তকারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।’ (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, খ.২, পৃ. ১২৪৯-৫০)
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরোপকারবৃত্তি স্বীকার করুন আর নাই করুন রবীন্দ্রনাথের নিজের সৎকর্মের তালিকাও কিন্তু হ্রস্ব নহে। তাঁহার দেওয়া অনেক। তাঁহার বাংলা সম্পত্তির মধ্যে বানান সংস্কারও পড়িবে। ঠাকুরের খ্যাতি জগৎ জুড়িয়া। কিন্তু আমরা যাঁহারা নিতান্ত গৃহকোণজীবী তাঁহাদের কাছে তিনি আরো। বাংলা ভাষার দশ স্রষ্টার একজন। আর দশ শব্দের কথা ছাড়িয়াও যদি দিই খোদ “বাংলা”শব্দটির বানান তো আর ছাড়িতে পারি না। বানানটি ব্যবহার প্রথম করিয়াছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৫৭)
এই বিষয়ে ঠাকুরের জবাবদিহি শুনিবার মতন: ‘আমার প্রদেশের নাম আমি লিখি বাংলা। হসন্ত ঙ-র চিহ্ন ং। যেমন হসন্ত ত-য়ের চিহ্ন ৎ। “বাঙ্গলা”মুখে বলি নে লিখতেও চাই নে। যুক্তবর্ণ ঙ্গ-এ হসন্ত চিহ্ন নিরর্থক। ঙ-র সঙ্গে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া চলে, কিন্তু দরকার কী, হসন্ত চিহ্ন যুক্ত ঙ-র স্বকীয়রূপ তো বর্ণমালায় আছে- সেই অনুস্বরকে আমি মেনে নিয়ে থাকি।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯৭)
বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়ে? পড়ে বটে। তিনিও তো ‘বাঙ্গালা’-ই লিখিয়াছিলেন। সত্যের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কবিতার ব্যবসায়ী হয়েন নাই। আর রবীন্দ্রনাথ শেষ বিচারে কবিই। কিন্তু তিনি হাল ছাড়িয়া দিবার মত, কবিজনোচিত ধাতুদৌর্বল্যে ভুগিবার মত অস্থিরমতি ছিলেন না। তাই রক্ষা।
এখনও অনেকের মনে দুঃখ। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ ‘বাংলা’বানান তাঁহারা এখনও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা লেখেন “বাঙ্লা”। ঘটনা কি? মণীন্দ্রকুমার ঘোষ পূর্ব বাঙালির দুঃখ খানিক ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। মাত্র ১৯৭৬ সালেও তিনি লিখিয়াছেন :
‘উচ্চারণের খাতিরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি মাত্র শব্দে ‘ঙ্গ’থেকে ‘গ’বিচ্ছিন্ন করে ‘ঙ’কে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন বটে কিন্তু সেসব শব্দ ছিল তদ্ভব- তৎসম শব্দে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নি। ‘বঙ্গ’শব্দ থেকে ‘বাঙ্গালা’‘বাঙ্গলা’-আমরা দুই বানানেরই সাক্ষাৎ পাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। রবীন্দ্রনাথ ‘বাঙ্গলা’না লিখে প্রথমে লিখলেন ‘বাঙ্লা’, পরে ‘বাংলা’। ‘বাঙ্গালী, কাঙ্গালী, ভাঙ্গা, রাঙ্গা’রবীন্দ্রনাথের হাতে হল ‘বাঙালি, কাঙালি, ভাঙা, রাঙা’। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে ‘গ’লোপ পেয়েছে ঠিকই, তবে পূর্ববঙ্গের কণ্ঠ থেকে কিন্তু অদ্যাপি ‘ঙ্গ’ধ্বনির কোনো বর্ণ স্খলিত হয় নি।” (বাংলা বানান, পৃ. ৩২)
এই তো মাত্র শুরু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন দানকে বাংলাদেশ (ভারতের কথা বলিতে পারিব না) অস্বীকার করিবে? ১৯৩১ সনে রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭০ বছর পূরা হইয়াছিল। তাঁহাকে বাড়াইয়া লইবার জন্য বাংলাদেশের সাধুব্যক্তিরা ৮ মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়ায় জনসভা ডাকিয়াছিলেন। মূলসভা নহে, পরামর্শ সভা। সভায় সভাপতির পাট লইয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিলেন আমাদের মনের কথাটাই :
‘সাহিত্য-জগতের এমন কোন বিভাগ নাই যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেন নাই, কিন্তু গীতিকাব্য জগতে তিনি যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ত অপরিমেয়। তাঁহার রচনাবলী জীবন্ত তাঁহার বিদ্রুপ তীক্ষ্ণ এবং তাঁহার ব্যঙ্গ তীব্র হইয়াছে। তিনি প্রাচীন কবিদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহার ব্যাকরণ জ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞান আমাদের অধিকাংশকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।’(চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, খণ্ড ১, পৃ. ২৩)
ঠাকুরের জগজ্জোড়া খ্যাতি বাংলা বানান সংস্কার আন্দোলনে তাঁহার সহায়ও হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা হইতেও তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ‘বহু দূরের স্কান্ডিনেভিয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দেশবাসী তাঁহার জন্য কি করিয়াছেন?’- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহার ৮ মে তারিখের বক্তৃতাতেই আছে: ‘আমরা যদি তাঁহার প্রতিভা-প্রসূত দানসমূহকে গ্রহণ ও উপলব্ধি করি, তাহাতেই তাঁহার প্রতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে।’ ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ ‘প্রাকৃত বাংলায় যা শুচি, সংস্কৃত ভাষায় তাই অশুচি।’
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮২)
বানান সংস্কার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে ‘কর্ণধার’মনে (বৃথা যদিও) করিয়াছিলেন সেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই তাঁহাকে ‘ব্যাকরণিয়া’উপাধি দিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক পুঁথির মধ্যে এক পুঁথির নাম ‘মনীষী স্মরণে’। সেখানে রামমোহন রায়ের উপাধি হইয়াছে ‘ব্যাকরণকার’আর রবীন্দ্রনাথের হইয়াছে ‘ব্যাকরণিয়া’। ‘বৈয়াকরণ’কথাটি সুনীতিকুমার কাঁহারও ভাগেই বরাদ্দ করেন নাই।
রামমোহন পুরাদস্তুর একখানা ব্যাকরণ বই লিখিয়াছিলেন, যথাক্রমে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ তাহা না করিলেও এই বিষয়ে তাঁহার মোট লেখা কম নহে। বিশেষ, শেষের দিকে লেখা ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’প্রবন্ধের লেখককে তাঁহার ধাঁচায় ‘ব্যাকরণিয়া’বলা অবৈধ হইতেছে না। তিনি যদি কোনদিন এই কথা বলিয়া থাকেন, ‘বাংলাদেশকে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে চিরজীবন আমি সেবা করে এসেছি,’ তবে তিনি অনেক কম দাবি করিয়াছেন ধরিতে হইবে।
বাংলা ব্যাকরণে বা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ যাহা দিয়াছেন তাহার সারাংশ লেখাও শক্ত। কতর্ব্যরে দোহাই দিয়া বলিব- সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন অর্থাৎ নিয়মের নিগড় হইতে বাংলা ব্যাকরণের মুক্তি প্রার্থনা তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্তি। জীবনের উপান্তে পৌঁছিয়া ঠাকুর লিখিয়াছেন, ‘এতকাল ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য না নিয়ে যে বহুকোটি বাঙালি প্রতিদিন মাতৃভাষা ব্যবহার করে এসেছে এতকাল পরে আজ তাদের সেই ভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। এই জন্য তাদের সেই খাঁটি বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮১)
একই জায়গায় তিনি দাবি করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা না জানিলে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা যাইবে না এমত দাবি অস্বাভাবিক এবং অত্যাচারের শামিল। যত শীঘ্র পারা যায় এই কঠোর বন্ধন, ‘পাণ্ডিত্যাভিমানী বাঙালির’এই নূতন কীর্তি, শিথিল করিয়া দেওয়া উচিত। তাঁহার ভাষায়, ‘বস্তুত একেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮১)
তিনি অনেক দূর গিয়াছেন। সবটুকু যাইতে পারেন নাই বলিয়া তাহার যতটুকু কৃতিত্ব তাহা তো অস্বীকার করা যাইবে না। রাজশেখর বসুকে ১৯৩১ সাল নাগাদ তিনি লিখিয়াছিলেন,
‘ভেবে দেখলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই। যাকে তৎসম শব্দ বলি উচ্চারণের বিকারে তাও অপভ্রংশ পদবীতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্তু বলি শোত্তো। মন শব্দ যে কেবল বিসর্গ বিসর্জন করেছে তা নয় তার ধ্বনিরূপ বদলে সে হয়েছে মোন্। এই যুক্তি অনুসারে বাংলা বানানকে আগাগোড়া ধ্বনি-অনুসারী করব এমন সাহস আমার নেই- যদি বাংলায় কেমাল পাশার পদ পেতুম তা হলে হয়তো এই কীর্তি করতুম- এবং সেই পুণ্যে ভাবীকালের অগণ্য শিশুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হতুম। অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব ও দীর্ঘহ্রস্বের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনিস্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়কার করব।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯৮)
মনে করিবার কারণ ঘটে নাই, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতের মর্যাদা কমাইয়া দেখিয়াছেন। তিনি রুই মাছের অমর্যাদা করেন নাই, শুদ্ধমাত্র পুঁটি মাছের জন্য দুঃখ পাইয়াছেন। রুই মাছ অগাধ জলে বিহার করে। তাহার বিকার নাই। পুঁটি গণ্ডুষমাত্র জলে ফরফর করিয়া বেড়ায়।
বাংলার উপর সংস্কৃতের চাপ বা প্রভাব বলিয়া একটা কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ জানিয়াছেন এই চাপ প্রাচীনকালের নয়। নিতান্ত আধুনিক যুগের ঘটনা। যে যুগে ভারতবর্ষের নানান এলেকায় নানা প্রকার প্রাকৃত অর্থাৎ মৌখিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল তখন সেই সকল ভাষা লেখার সময় সংস্কৃত ভাষার নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই। মুখের ভাষাকেই লিখিত ভাষার আদর্শ ধরা হইয়াছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে নতুন ধর্মের বাণী ছড়াইয়া দিতে হইলে তাহাই ছিল কার্যকর পন্থা। এই কার্যবুদ্ধি ও ন্যায়পরতা সমান হইয়াছিল সেই যুগে।
বর্তমান যুগের আদর্শ কেন তাহা হইবে না? প্রাচীন পণ্ডিতদের তিনি শ্রদ্ধা করিয়াছেন। ঠাকুর লিখিয়াছেন: ‘যাঁরা সমাধান করেছিলেন তাঁরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁরা বোঝার মতো চাপিয়ে যান নি জনসাধারণের ’পরে। যে অসংখ্য পাঠক ও লেখক পণ্ডিত নয় তাদের পথ তাঁরা অকৃত্রিম সত্যপন্থায় সরল করেই দিয়েছিলেন।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮১)
এ কালের পণ্ডিতরা, কবির নালিশ, সেই ধর্ম ভুলিয়াছেন। ‘তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯৩) রবীন্দ্রনাথ বাংলা বানান সংস্কারে বাদী হইয়াছিলেন এই দুঃখেই। তিনি জানিতেন, ‘বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুলপরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্ভাবিত বলিয়া বাংলা বানান, এমন-কি, বাংলা পদাবিন্যাস প্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৬) কামনা করিয়াছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ইহাতে হাত দিন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান সংস্কার সমিতির বিধানকর্তা হইবার মতো জোর আছে। রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধমাত্র যুক্তির জোরে নহে, সেই জোরের জোরেও আস্থা রাখিতেন।
সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় চিত্তের যে আভিজাত্য, যে তপস্যা আছে তাকে বাংলা ভাষায় পুরাপুরি গ্রহণ করিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ। যদি না করি তবে আশঙ্কা, ‘আমাদের সাহিত্য ক্ষীণপ্রয়ণ ও ঐশ্বর্যভ্রষ্ট’ হইবে। শুদ্ধ ভাবের দিক হইতেই নহে, ‘শব্দের দিক’ হইতেও ‘বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কাছে নিরন্তর আনুকূল্যের অপেক্ষা না করে’ থাকিতে পারে না। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৪২)
রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধমাত্র বাংলার স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা পাইবে এই প্রার্থনা করিয়াছেন। ১৩৩৮ সালে সংস্কৃত কলেজ কবিকে ‘কবি সার্বভৌম’উপাধি দেন। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষাতত্ত্ব নতুন করিয়া বয়ান করিলেন। বলিলেন, ‘একদিন ছিল ভারতবর্ষে ভাষা-বোধের একটা প্রতিভা। ভারতবর্ষ পানিনির জন্মভূমি।’ তিনি আরো বলিলেন :
‘তখনকার দিনে প্রাকৃতকে যাঁরা বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন পরম পণ্ডিত। অথচ প্রাকৃতের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকরণের চাপে তাঁরা প্রাকৃতকে লুপ্ত-প্রায় করেন নি। তার কারণ ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ছিল সহজ বোধশক্তি। আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে ভুলে যাই যে বাংলার একটি স্বকীয়তা আছে। অবশ্য সংস্কৃত থেকেই সে শব্দ-সম্পদ পাবে, কিন্তু তার নিজের দৈহিক প্রকৃতি সংস্কৃত দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা অসংগত। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কখনো সে চেষ্টা করেন নি।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৪১)
রবীন্দ্রনাথকে কেহ কেহ বসন্তরোগে পাইয়াছে কিনা সন্দেহ করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি শীতলা মায়ের পূজা বিশেষ দিয়াছিলেন বলিয়া জানি না। তিনি কোন কোন ‘আধুনিক’পণ্ডিতকে ‘পণ্ডিতমূর্খ’কেন বলিয়াছিলেন, এখন বোঝা যাইতেছে। কারণ তাঁহারাই তো গভর্ণমেন্ট, কাণ, বানান প্রভৃতি বানান লিখিতেন। কবির উষ্মার কারণ এই সংস্কৃতের চাপে বাংলাকে লুপ্তপ্রায় করনেওয়ালারা অর্বাচীন। তাহাদের দোষ পশ্চিমের দোষ মাত্র।
‘যারা মনে করেছেন বাইরে থেকে বাংলাকে সংস্কৃতের অনুগামী করে শুদ্ধিদান করবেন, তাঁরা সেই দোষ করেছেন যা ভারতে ছিল না। এ দোষ পশ্চিমের। ইংরেজিতে শব্দ ধ্বনির অনুযায়ী নয়। ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে উদ্ভূত শব্দে বানানের সঙ্গে ধ্বনির বিরোধ হলেও তাঁরা মূল বানান রক্ষা করেন।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৪১)
কেহ কেহ বলিতে কসুর করেন নাই, রবীন্দ্রনাথের ‘অনুগত’ পণ্ডিতগণ সমভিব্যবহারে বানান সংস্কার সমিতি গঠিয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই কমিটি বিচারের উপরে উঠে নাই-একথা সত্য। পুরাতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দ কহিয়াছিলেন, ‘বাঙ্গালা ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান।’ (‘কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম,’ মাসিক বসুমতী ১৩৪৪) তদুপরি, কমিটির অন্যতম সভ্য বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের কথানুসারে, ‘সে সময়ে বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মন কষাকষির ভাব চলিতেছিল।’শুদ্ধ তাহাই নহে, ‘অনেক মুসলমান লেখক বাংলা ভাষায় নূতন নূতন আরবী ফারসী শব্দ এবং অপূর্ব-প্রচলিত বাগভঙ্গী আমদানী করিয়া বাংলা ভাষার ‘সংস্কার’-এ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।’ আর রবীন্দ্রনাথ ‘ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন’। (বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি, মুদ্রণ ২, পৃ. ৩৭-৩৮)
কি শোচনীয় এই দেশ! যে দেশের শতে পঞ্চাশের বেশি লোক সেই বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে, যে দেশের বাদবাকির শতকরা ৮০ জনই তপশিলি হিন্দু তাঁহাদের একজন প্রতিনিধিও বাংলা বানান সংস্কার কমিটিতে দেখা যায় নাই। ইহা কেমন ন্যায়বিচার? কেমন কাণ্ডজ্ঞান? কোন কোন লোকের ধারণা বানান কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান এবং প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও ছিলেন। (নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, পৃ. ৩৪)
প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার ধারণা মার্ক টোয়েনের মৃত্যু সংবাদের মতো সামান্য অতিরঞ্জিত হইয়াছে। এই যা। রসিকতার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছিলেন, ‘নব্য বানান-বিধাতাদের মধ্যে তিন জন বড় বড় ভট্টাচার্যবংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৬)
সমিতির সাধারণ সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকেও যদি হিসাবে লওয়া অবৈধ না হয় তবে আমি তো ভট্টাচার্য পাইতেছি চারিজন- বাকি তিনের মধ্যে বিধুশেখর, দুর্গামোহন ও বিজনবিহারী রহিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি, পৃ. ২১-২২)
এই বানান সমিতিও কবির কথা ষোলো আনা রাখেন নাই। কান, সোনা, কোরান, গভর্নর প্রভৃতি শব্দও যাহাতে কবির ইচ্ছানুযায়ী বামুন, গিন্নী, শোনা, করেন, করুন প্রভৃতির মতন দন্ত্য ন দিয়া লেখা হয় তাঁহার আদেশ হইল। দুঃখের মধ্যে, প্রতিবিধানও একই সঙ্গে রহিল। ‘ “রাণী”বানান অনেকেই রাখিতে চান, এ জন্য এই শব্দে বিকল্প বিহিত হইয়াছে’-সমিতি বলিলেন তাহাই সই। (নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, বানান বিতর্ক, পৃ. ৩১৪)
বিধানকর্তারা নিতান্ত অবিবেচক নহেন। সবার উপরে রবীন্দ্রনাথও বুঝিলেন, ‘তাঁহাদের মনেও ভয় ডর আছে, প্রমাণ পাওয়া যায়।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৫) প্রমাণ- সমিতি লিখিয়াছেন-‘বিকল্প বাঞ্ছনীয় নয়, তথাপি যেখানে দুই প্রকার বানানের পক্ষেই প্রবল অভিমত পাওয়া গিয়াছে সেখানে বিকল্পের বিধান করিতে হইয়াছে।’(বানান বিতর্ক, পৃ. ৩১৩)
একপ্রস্ত উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝান যাইতে পারে। ‘বাংলা বানানের নিয়ম’দ্বিতীয় সংস্করণে (সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার সমিতি বিধান দিয়াছিলেন, ঢাকি, ঢুলি, বাঙ্গালি, ইংরেজি, হিন্দি, রেশমি, পশমি, মাটি, ওকালতি, একটি, দুটি প্রভৃতি তদ্ভব, স্ত্রীলিঙ্গ ও অন্য শব্দে কেবল হ্রস্ব-ই বা হ্রস্ব-উ হইবে। (বিধি ৭)
তৃতীয় সংস্করণে পুনরাদেশ হইল: ‘স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা-“কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী”। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা: “ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চল্তি”। “পিসী, মাসী”স্থানে বিকল্পে ‘‘পিসি, মাসি’’ লেখা চলিবে।’ (বিধি ৫)
তৃতীয় সংস্করণের পায়ে পায়ে প্রকাশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, ‘সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন’এ দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়।’ (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৮৬)
‘গৃহবিচ্ছেদের আশংকা’আছে বলে রবীন্দ্রনাথও সমিতির অনেক সিদ্ধান্ত কষ্টে মানিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালের ২ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে ‘বিশ্বভারতীয় কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রচিত বাঙ্গালা শব্দের নূতন বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি এবং বাঙ্গালা পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন।’ (রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, খ. ২, পৃ. ১৫৫)
মণীন্দ্রকুমার দারুণ বলিয়াছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল হ্রস্ব-ইকারের দিকে, সুনীতিকুমারের আসক্তি দীর্ঘ-ঈকারের প্রতি।’রবীন্দ্রনাথ ‘জরাজনিত মনোযোগের দুর্বলতা’ হেতু ‘দায়ী’কে ‘দায়ি’ লিখিতেন আর সুনীতিকুমার ‘খেয়াল ছিল না’ বলিয়া রিপোর্টকে ‘রীপোর্ট’লিখিতেন। মণীন্দ্রকুমার লিখিতেছেন, ‘অর্থাৎ খেয়াল না থাকলে রবীন্দ্রনাথের কলমে আসে হ্রস্ব ই-কার, সুনীতিকুমারের আসে দীর্ঘ-ঈকার।’ (বাংলা বানান, পৃ. ৩৫-৩৬) কথাপ্রসঙ্গে সুনীতিকুমার নাকি একদিন বলেওছিলেন ‘দীর্ঘ-ঈকার (ী) লেখা সোজা।’ মণীন্দ্রকুমারের মন্তব্যও তাঁহার অনুকূলই: ‘বাস্তবিকই বাংলা বর্ণবিন্যাসে স্বরচিহ্নের মধ্যে হ্রস্ব-ইকার (ি) লেখাই সর্বাধিক কষ্টদায়ক।’(বাংলা বানান, পৃ. ৩৬)
রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ‘ভাষাচার্য’ উপাধি দান করিয়া যে পুঁথিটি তাঁহার করকমলে তুলিয়া দিলেন, তাহাতেই দেখি লেখা আছে,
‘খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যাভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ই-কারকে মানব। ‘ইংরেজি’ বা ‘মুসলমানি’ শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই- অসংকোচে হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্-ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্ দিন কোনো পণ্ডিতাভিমানী লেখক ‘মুসলমানিনী’কায়দা বা ‘ইংরেজিনী’রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশংকা থেকে যায়।’(বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৮৬-৭; নিুরেখা যোগ করা হইয়াছে, বানান রবীন্দ্রনাথের)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তো রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য প্রকাশের এক যুগ আগেই তাঁহার সমর্থনসূচক কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বিচারে তদ্ভব ও দেশজ বাংলা শব্দে সবখানেই হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব উ হওয়াই নিয়ম। দীর্ঘস্বরের জন্য বাংলা ভাষায় আলাদা হরফেরই দরকার নাই। দীর্ঘস্বর বুঝাইবার জন্য আদৌ কোন চিহ্নও দরকার হইবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে শহীদুল্লাহ বাংলা ১৩৩১ সালে জানাইয়াছিলেন,
‘যেমন সংস্কৃত ইত্যাদির রোমান অক্ষরে অনুলেখনে (Transliteration) স্বরবর্ণের উপর দীর্ঘ চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালায় তাহার কোন দরকার নাই। বাঙ্গালা উচ্চারণের নিয়মেই হ্রস্ব দীর্ঘ ধরা পড়ে- যেমন হসন্ত বর্ণের আগের স্বর দীর্ঘ হয়। বাস্তবিক সেখানে আমরা সংস্কৃতের অনুকরণে হ্রস্বদীর্ঘ লিখি, বাঙ্গালা উচ্চারণ অনেক জায়গায় তাহার বিপরীত, যেমন “সীতা” এবং “মিতা”। এখানে “সী” ও “মি” উভয়েরই উচ্চারণ হ্রস্ব। “মীন” “দিন” এখানে “মী” ও “দি” উভয়েরই উচ্চারণ দীর্ঘ। কাজেই “শিতা” “মিন” লিখিলে বাঙ্গালা উচ্চারণ দস্তুরমত বুঝা যাইবে।’ (ভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৮৬)
মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁহার ‘ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’ নামক প্রসিদ্ধ পুঁথিযোগে আরো অধিক গিয়াছেন। তাঁহার মতে দেশজ, বিদেশি, সংস্কৃত ও সংস্কৃতভব সকল বাংলা শব্দেই হ্রস্ব ই আর হ্রস্ব উ ব্যবহার করাই সংগত। যথা: গাভি, বুদ্ধিজিবি, নিড়, অনুসারি, অনুরূপ, ইত্যাদি। কেবল বিদেশি শব্দ বাংলা অক্ষরে লিপিকালে ইহার অন্যথা হইতে পারে। (পৃ. ৬৪৬; পরেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙলা বানানবিধি, পৃ. ২৮)
বাংলা শব্দের, স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় একদা “ন্” ছিল, যেমন: নাতিন, মিতিন, ঠাকুরন ইত্যাদি, পরেশচন্দ্র মজুমদার এ কথা মানেন। কিন্তু তাঁহার মতে, ‘সংস্কৃত প্রভাবেই তা ক্রমে ক্রমে –নী (অর্থাৎ ন+ঈ) প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে।’ (বাঙলা বানানবিধি, পৃ. ২৩) এই যুক্তিতে তিনি বাদী হইলেন, বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈকারযুক্ত প্রত্যয় রাখিতে হইবে। তাঁহার ধারণা সংস্কৃতের চাপ এখনও আছে। যেখানে তৎসম শব্দের বেলায় যথারীতি ঈ/নী প্রত্যয় থাকিতেছে সেখানে বাংলা শব্দের বেলায় ই/নি চালু করা হইলে ‘দ্বৈধ প্রবণতার সংগ্রাম’ সূচিত হইবে।
ইহার বাহিরেও কথা আছে। ওড়িয়া, ভোজপুরি, অহমিয়া, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় তদ্ভব শব্দের বানানে এখনও সংস্কার করা হয় নাই। সেখানে এখনও ঈ/নী চলিতেছে। তাই বাংলায় বিচ্ছিন্ন সংস্কার করা উচিত হইবে কিনা তিনি নিশ্চিত হইতে পারিতেছেন না। (বাঙলা বানানবিধি, পৃ. ২৩) দুই বানানের আবদার ‘পণ্ডিত বলেন, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে তুমি ঈ ছাড়িয়া হ্রস্ব ই ধরিলে যে? আমি বলিব ছাড়িলাম আর কই। একতলাতেই যাহার বাস তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, নীচে নামিলে যে, সে বলিবে, নামিলাম আর কই- নীচেই তো আছি। ঘোটকীর দীর্ঘ-ঈতে দাবি আছে; সে ব্যাকরণের প্রাচীন সনন্দ দেখাইতে পারে- কিন্তু ঘুড়ির তাহা নাই। প্রাচীন ভাষা তাহাকে এই অধিকার দেয় নাই। কারণ, তখন তাহার জন্ম হয় নাই। তাহার পরে জন্মাবধি সে তাহার ইকারের পৈতৃক দীর্ঘতা খোয়াইয়া বসিয়াছে।
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ১১২)
পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি পণ্ডিতের আপত্তি যেন রবীন্দ্রনাথ আগে হইতেই আন্দাজ করিয়া থাকিবেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, ‘একটা বিষয়ে বাংলাকে বাহাদুরি দিতে হবে। য়ুরোপীয় অনেক ভাষায়, তা ছাড়া হিন্দি হিন্দুস্থানি গুজরাটি মারাঠিতে, কাল্পনিক খেয়ালে বা স্বরবর্ণের বিশেষত্ব নিয়ে লিঙ্গভেদপ্রথা চলেছে। ভাষার এই অসংগত ব্যবহার বিদেশীদের পক্ষে বিষম সংকটের। বাংলা এ সম্বন্ধে বাস্তবকে মানে। বাংলায় কোনোদিন ঘুড়ি উড্ডীয়মানা হবে না, কিংবা বিজ্ঞাপনে নির্মলা চিনির পাকে সুমধুরা রসগোল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে না। কিংবা শুশ্রূষার কাজে দারুণা মাথাধরায় বরফশীতল জলপটির প্রয়োগ সম্ভাবনা নেই।’ (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৮৬)
তাহা ছাড়াও ‘খাপছাড়াভাবে সংস্কৃতের নী ও ঈ প্রত্যয়ের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাবার রীতি বাংলায় আছে, কিন্তু তাকে নিয়ম বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণেও মেনে চলবার অভ্যেস তার নেই। সংস্কৃতে ব্যাঘ্রের স্ত্রী ‘ব্যাঘ্রী’, বাংলায় সে ‘বাঘিনী’। সংস্কৃতে ‘সিংহী’ই স্ত্রীজাতীয় সিংহ, বাংলায় সে ‘সিংহিনী’।’(বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৮৪)
শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথেরই জয় হইল। ১৯৮০ সালের দশক হইতে বাংলাদেশে এবং ভারতে বাংলা ভাষার বানান, লিপি ও লেখনরীতির সংস্কার আন্দোলন শুরু হইবার পর ভাষায় হ্রস্ব ইকারের অধিকার বেশি করিয়া স্বীকার করা হইতেছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমি যে সকল সংস্কার প্রস্তাব পাস করাইতে সমর্থ হইয়াছেন সেইগুলিতে হ্রস্ব ইকার প্রবণতারই জয় হইয়াছে। সাধারণভাবে এই সত্যে সন্দেহ করিবার কোন স্থান নাই। তবে ইহাও মিথ্যা নহে যে সংস্কৃতের চাপ কোথাও কোথাও এখনও রহিয়া গিয়াছে।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ব্যাপক সমতার জন্য সিদ্ধান্ত লইয়াছেন স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানোর ক্ষেত্রে হ্রস্ব ইকার/নিকারের ব্যবহার হইবে। (বানানবিধি, স. ৫, বিধি ১১.৪)
‘তাই লেখা হবে কাকি(-মা) কামারনি খান্ডারনি খুকি খুড়ি খেঁদি গয়লানি’ চাকরানি চাচি ছুঁড়ি ছুকরি জেঠি (-মা) ঝি ঠাকুরানি দিদি (-মা) নেকি পাগলি পিসি (-মা) পেঁচি বাঘিনি বামনি বেটি ভেড়ি মামি (-মা) মাসি (-মা) মুদিনি মেথরানি রানি সাপিনি সোহাগিনি স্যাঙাতনি ইত্যাদি।’
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির তুলনায় বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি খানিক পিছনে আছেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের ‘প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ‘তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার দেওয়া যেতে পারে। যেমন : রানী, পরী, গাভী।’ (নিয়ম ২.০১) ভারতের বাংলা আকাদেমিও কম যাইবেন কেন? তাঁহারাও ব্যতিক্রম অনুমোদন করিয়াছেন। বিধান হইল :
‘সংস্কৃত-ঈয় প্রত্যয় যদি বিশেষণার্থে বিদেশি শব্দ বা অ-তৎসম শব্দ বা শব্দাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার বজায় রাখতে হবে। যেমন : অস্ট্রেলীয় আর্টেজীয় আলজেরীয় ইউরোপীয় ইতালীয় এশীয় কানাডীয় ক্যারিবীয় ক্যালাডোনীয় জর্জীয় পোলিনেশীয় লাইবিরীয় সাইবেরীয় ইত্যাদি।’ (বিধি ১১.৮)
কোন যুক্তিতে এই ব্যতিক্রম? যুক্তি আর যাহাই হোক বিশেষ্য-বিশেষণ উচ্চারণ ভেদের যুক্তি হইতে পারে না। বাংলা ও সংস্কৃতের ভেদই শুরু হইয়াছে উচ্চারণ ভেদ হইতেই। রবীন্দ্রনাথ সে সত্যে সম্পূর্ণ সজাগ : ‘বাংলা ভাষা শব্দ সংগ্রহ করে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু ধ্বনিটা তার স্বকীয়। ধ্বনিবিকারেই অপভ্রংশের উৎপত্তি।’
এই সত্যটাই চাপা দেওয়ার সুবিধা জোগায় বাংলা শব্দের বানান। রবীন্দ্রনাথের মতে এই বানান ব্যবসায়ের জোরেই বাংলা আপন অপভ্রংশত্ব চাপা দিতে চাহে। ‘এই কারণে বাংলা ভাষার অধিকাংশ বানানই নিজের ধ্বনিবিদ্রোহী ভুল বানান।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৬৪)
একই কথাটা উল্টা দিক হইতে দেখিলে কি দাঁড়ায়? পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ‘ধ্বনিবিদ্রোহী ভুল বানান’কেও ‘মান্যতা’ দিতে আগ্রহী। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ‘বাংলা ব্যাকরণসম্মত প্রত্যয়-ব্যবহারে, সমাস-ব্যবহারে বা সন্ধি-সূত্রানুসারে কোনো কোনো বানান বাংলায় দীর্ঘকাল যাবৎ ঈষৎ স্বতন্ত্রতা লাভ করেছে। সেগুলিকেও তৎসম শব্দানুরূপ মান্যতা দেওয়া যেতে পারে।’(বিধি ৩.২, নিুরেখা আমরা দিয়াছি)
রবীন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ‘যদি প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম। প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণের কেমাল পাশা হবার দুরাশা আমার নেই কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ। উক্ত পাশা এ দেশেও দেহান্তর গ্রহণ করতে পারেন।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৫)
বলি, ঠাকুরের আত্মা শান্তিতে থাকিবেন। আপনার পাশা এখনও এই দেশে দেহান্তর গ্রহণ করেন নাই। বোধ হয় তিনি বিশ্রামে আছেন। তবিয়তে বহাল আছেন অসত্য বানান। মান্যতা পাইয়াছেন নতুন করিয়া। কোন কোন বাংলা বানানকে তৎসম শব্দস্বরূপ মান্যতা দিবার দৃষ্টান্ত: অধিকারী অধিবাসী অভিমুখী আততায়ী একাকী কৃতী গুণী জ্ঞানী তন্ত্রী দ্বেষী ধনী পক্ষী মন্ত্রী রোগী শশী সহযোগী ইত্যাদি।
আবার এগুলি বাংলায় আসিলেও সংস্কৃতের পোঁ ছাড়ে নাই। তাই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মেই পরিবর্তিত হইবে। যথা: গুণিজন, পক্ষিকুল মন্ত্রিসভা শশিভূষণ বা একাকিত্ব সহযোগিতা প্রভৃতি। সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্যতিক্রমও স্বীকার করা কর্তব্য হইয়াছে। তাই পাইবেন দীর্ঘ ঈকারওয়ালা শব্দভাণ্ডার। যেমন : আগামীকাল আততায়ীদ্বয় ধনীসমাজ পরবর্তীকাল প্রাণীবিদ্যা যন্ত্রীদল হস্তীদল ইত্যাদি। (বিধি ৪.২)
এই রকম আরও চিত্তরঞ্জিনী বিধির প্রদর্শনী আছে। বাংলা বানানে আমোদ নামে নতুন প্রবন্ধ কেহ লিখিলে মন্দ হইবে না। এই প্রসঙ্গে জানাইয়া রাখি একালের সংস্কারবাদী কর্তারাও রবীন্দ্রনাথের সেই দেহান্তর লওয়া কেমাল পাশা মোটেই নহেন। তাঁহাদিগকে বড় জোর খলিফা আবদুল হামিদ উপাধি দেওয়া যাইতে পারে।
মজার কথা এই- ঢাকা ও কলিকাতার সংস্কর্তারা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ বা প্রেরণা অমান্য করিয়াই এখনও সংস্কৃত ব্যাকরণের দাসত্ব করিতেছেন। শুদ্ধমাত্র বাংলায় চলিত ‘সংস্কৃতসম’শব্দেই নহে, এই দাসত্বের শিকলি তাহারা ‘সংস্কৃতভব’শব্দেও ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে লাগাইয়া রাখিয়াছেন।
আবার এই সংস্কর্তারাই কারণে অকারণে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যত্রতত্র দীর্ঘ-ঈকার বসাইয়া ‘কী’লিখিয়া উল্লাস করিবার সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই নজির হাজির করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া দেবপ্রসাদ ঘোষ ১৯৩৭ সনে একবার বলিয়াছিলেন, ‘আপনি অদ্বিতীয় সাহিত্য-স্রষ্টা, কিয়ৎ পরিমাণে ভাষাস্রষ্টাও বটেন, কিন্তু বিশ্লেষণ বিষয়ে আপনার যেন কিঞ্চিৎ অপাটব লক্ষ্য করিতেছি। বোধ করি সৃষ্টি এবং বিশ্লেষণে বিভিন্ন প্রকার প্রতিভার আবশ্যক হয়।’ (বানান বিতর্ক, স. ৩, পৃ. ১৪৬)
আমাদের আশংকা দেবপ্রসাদের এই নির্দেশ হয়তো বা অমূলক নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার একাধিক পত্রিকা ব্যবহারে ও ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’প্রবন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করিয়া দীর্ঘ-ঈকারযোগে ‘কী’লিখিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই তো স্থানে স্থানে, অজ্ঞানে খণ্ডন করিয়াছেন। আমাদের তাহা খণ্ডন করিবার প্রয়োজন হইতেছে না।
রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন, ‘কি শব্দের সর্বনাম প্রয়োগ ও অব্যয় প্রয়োগে বানানভেদ করিলে অর্থাৎ একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝাবার সুবিধা হয়।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯০)
আরেক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, ‘তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমন-কি প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দূর হয় না।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮৪)
ঠাকুরের এই ধারণাটাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি ১৯৩৬ সনে (২য় সংস্করণে) গ্রহণ করিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন, “অব্যয় হইলে ‘কি’, সর্বনাম হইলে বিকল্পে ‘কী’বা ‘কি’হইবে, যথা : ‘তুমি কি যাইবে? তুমি কী (কি) খাইবে বল’। (নিয়ম ৭) অর্থাৎ সর্বত্র ‘কি’লিখিলেও অন্যায় হইবে না।
ব্যাখ্যাচ্ছলে জানানো হইয়াছিল, ‘অর্থপ্রকাশের সুবিধার নিমিত্ত ‘কি’ও ‘কী’র ভেদ বিকল্পে বিহিত হইল। অন্যত্র ঈ ই প্রয়োগের হেতু দেখা যায় না, কেবল ই উ লিখিলে বানান সরল হইবে।’(নিয়ম ৭) ইহা কি প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের আবদার যুগপৎ প্রত্যাখ্যান ও অনুমোদন দুইটাই ছিল না? ইহাতেই তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগে তিনি পালন করিয়া চলিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। তাই না? আমরা ইহার অর্থ করিতে পারি কেহ ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজনে ‘কী’লিখিতে পারিবেন, তবে অন্যদের লিখিতে বাধ্য করা যাইবে না। এতদিনে আমাদের বাধ্য করা হইতেছে, ইচ্ছা এখন অধিকারকে হটাইয়াছে।
ইতিহাসের অনুরোধে স্মরণ করিতেছি এই দীর্ঘ ঈকারযুক্ত কী বানানের দাবি প্রথম তুলিয়াছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁহাদের ‘চ’ল্তি ভাষার বানান’ নামক প্রবন্ধে জানানো হইয়াছিল
‘সাধুভাষা ও চল্তি ভাষা দুয়েতেই প্রশ্নসূচক অব্যয় কি [হ্রস্ব] ই-কার দিয়ে লেখা হবে। নির্দেশক সর্ব্বনাম “কী” [দীর্ঘ] ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: তুমি কি খাবে? [অব্যয়], তুমি কী খাবে? [সর্ব্বনাম], তুমি কী কী খাবে [সর্ব্বনাম]।’সঙ্গে আরো জানান হইয়াছিল, ‘পুরানো বাঙলা পুঁথীতে “কী”বানান অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।’ (বানান বিতর্ক’, পৃ. ৩০৯-৩১০)
বানানের তফাত না থাকিলে ভাবের তফাত নিশ্চিত করা যাইবে না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ‘কি’বানান হইতে ‘কী’বানান আলাদা করিতে চাহেন। ‘তুমি কি জানো?’ এই প্রশ্নে দুই দুইটা ভাব প্রকাশ হইতে পারে। একটা ভাবে প্রশ্ন করা হয় শ্রোতা জানেন কি জানেন না। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম রাখিয়াছেন ‘জানা সম্বন্ধে’প্রশ্ন। দ্বিতীয় ভাবে একটা সন্দেহ করা হয় মাত্র। সন্দেহের বিষয় শ্রোতা জানেন কি জানেন না এই বিকল্প নহে। বিষয় তিনি কতখানি জানেন তাহাতেই সীমিত। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম রাখিলেন ‘জানার প্রকৃতি বা পরিমাণ সম্বন্ধে’প্রশ্ন। ভাবের এই তফাত নিশ্চিতরূপে আন্দাজ করিতে হইলে বানানের তফাত করিতে হয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব। দেবপ্রসাদ ঘোষের কাছে লেখা দ্বিতীয় পত্রিকায় ঠাকুরের প্রতিপাদ্য ইহাই। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮৪-৮৫)
ছয় বছর আগের- জীবনময় রায়কে লিখিত-চিঠিতে পরিমার্জিত রূপও বাংলা শব্দতত্ত্ব বইয়ে পাওয়া যায়। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ব্যাকরণের ‘পদ’অর্থেও জাতি শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন। বলিয়াছেন ‘কি’শব্দ অব্যয় হইলে এক জাতি, সর্বনাম হইলে অন্য জাতি। জাতির মতন অর্থেরও ভেদ হয়। এই ভিন্ন জাতিধর্ম আর ভিন্ন অর্থধর্ম বুঝবার সুবিধা হয় বলিয়াই তিনি বানানের তফাত দরকার বোধ করেন। তাঁহার আশঙ্কা, ‘এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯০)
এক্ষণে কবির উদাহরণ ‘কি রাঁধছ?’ অথবা “কী রাঁধিছ?”- এই প্রশ্নেও দুই অর্থ প্রকাশ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “বলা বাহুল্য এ দুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র।” বাক্যের এক ব্যঞ্জনা- শ্রোতা রাঁধিতেছেন কি রাঁধিতেছেন না সেই দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় ব্যঞ্জনা, তিনি রাঁধিতেছেন নিশ্চিত তবে জানার ইচ্ছা হইতেছে কোন ব্যঞ্জন রাঁধিতেছেন। এই দুই ব্যঞ্জনার তফাত করিতে হইলে বানানের তফাতে সাহায্য হইবে। ইহার একটি বিকল্পও রবীন্দ্রনাথের মনে আসিয়াছিল: “যদি দুই ‘কি’-এর জন্যে দুই ইকারের বরাদ্দ করতে নিতান্তই নারাজ থাক তা হলে হাইফেন ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত: ‘তুমি কি রাঁধ্ছ’ এবং ‘তুমি কি-রাঁধ্ছ’।” (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ, ২৯০)
দুর্ভাগ্যবশত এই বিকল্পটি প্রয়োগের কথা তিনি বেশিদিন মনে রাখেন নাই। অর্থের প্রভেদ করার সমস্ত দায় তিনি বানানের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিচার করিয়া দেখিতে হয়, এই দায় সত্য সত্যই বহন করা বানানের ক্ষমতায় কুলাইবে কিনা।
জীবনময় রায়কে লিখিত ১৯৩১ সালের পত্রিকায় তিনি আরো একটি পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কবি বলিতেছিলেন ভাষায় অতিরিক্ত যতিচিহ্ন ব্যবহার করার দরকার নাই। তাঁহার কথায়, “চিহ্নগুলো ভাষার বাইরের জিনিশ।”এইগুলি অগত্যা ব্যবহার করিতে হয় মাত্র। ভাষার গতি হইলে করিতে হয় না: “সেগুলোকে অগত্যার বাইরে ব্যবহার করলে ভাষায় অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়।” কবি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, “প্রাচীন পুঁথিতে দাঁড়ি ছাড়া আর-কোনো উপসর্গ ছিল না। ভাষা নিজেরই বাক্যগত ভঙ্গিদ্বারাই নিজের সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধি করত।”(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮৮)
কবি বলিতেছিলেন প্রশ্নবোধক আর বিস্ময়চিহ্নের তো প্রয়োজনই নাই। ‘কে, কি, কেন, কার, কিসে, কিসের, কত প্রভৃতি এক ঝাঁক অব্যয় শব্দ তো আছেই তবে চিহ্নের খোশামুদি করা কেন।’কবি বলিলেন, ‘তুমি তো আচ্ছা লোক’-এই বাক্যে তো শব্দই যাহা বলিবার বলিতেছে। তাহার পর আর বিস্ময়চিহ্ন বা প্রশ্নচিহ্ন যোগ করা বাহুল্য মাত্র। কবির ভাষায়, ‘ইঙ্গিতের পিছনে আরো একটা চিহ্নের ধাক্কা দিয়ে পাঠককে ডব্ল চমক খাওয়ানোর দরকার আছে কি। পাঠক কি আফিমখোর।’
আরো উদাহরণ দিয়াছেন তিনি। ‘রোজ রোজ যে দেরি করি আসো’-এই বাক্যের বিন্যাসেই নালিশের যথেষ্ট জোর আছে। বিস্ময়বোধক চিহ্ন বসাইবার কাজটিই বরং কবির বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। তিনি বাতলাইয়াছেন, ‘যদি মনে কর অর্থটা স্পষ্ট হল না তা হলে শব্দযোগে অভাব পূরণ’কর। ‘করলে ভাষাকে বৃথা ঋণী করা হয় না-যথা, ‘রোজ রোজ বড়ো-যে দেরি করে আস’।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮৯)
বাংলা ভাষার এই দোষ নতুন, পশ্চিমের দোষ। পরাধীনতার কুফল। রবীন্দ্রনাথের হাতের ভাষায় এই ‘হাকিমী সাহেবিয়ানায় পেয়ে বসেছে’আমাদের। ‘কে হে তুমি’ বাক্যটা নিজের প্রশ্নত্ব হাঁকাইয়া চলিয়াছে। উহার পিছনে আবার একটা কুঁজওয়ালা সহিস লাগাইবার দরকার নাই। ‘আহা, হিমালয়ের কী অপূর্ব গাম্ভীর্য’-এই বাক্যের পরে আর একখানা ফোঁটা-সওয়ারি দাঁড়ি বা বিস্ময়চিহ্নের প্রয়োগ বৃথা। ভাষাকে বৃথা ঋণী না করাই কবির ধর্ম।
কবি শুদ্ধ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যতিচিহ্ন সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব বানানচিহ্ন সম্বন্ধেও খাটে। প্রশ্ন বা বিস্ময়চিহ্ন যেমন বাংলা ভাষায় মধ্যে মধ্যে অত্যাচার আকারে হাজির হয় দীর্ঘ ঈকারযুক্ত ‘কী’ বানানও তাহার অনুরূপ কিনা রবীন্দ্রনাথের ভাবিবার অবকাশ হয় নাই। আমার ধারণা- না হওয়াতে আমাদের ভাষারই ক্ষতি হইয়াছে। ভাষাকে বৃথা ঋণী করার সকল চেষ্টাই পরিহার করিতে হইবে। না করিলে ভাষা সম্বন্ধে সতর্ক হইবার কর্তব্যে শিথিলতা দেখা দেয়।
রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইহার নজির দেখাইয়াছেন, ‘চিহ্নের উপর বেশি নির্ভর যদি না করি তবে ভাষা সম্বন্ধে অনেকটা সতর্ক হতে হয়। মনে করো কথাটা এই: “তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ।”এখানে বাবুয়ানার উপর ঠেস দিলে কথাটা প্রশ্নসূচক হয়-ওটা একটা ভাঙা প্রশ্ন- পুরিয়ে দিলে দাঁড়ায় এই, “তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ তার মানেটা কী বলো দেখি।” “যে” অব্যয় পদের পরে ঠেস দিলে বিস্ময় প্রকাশ পায়। “তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ”। প্রথমটাতে প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়টাতে বিস্ময়চিহ্ন দিয়ে কাজ সারা যায়। কিন্তু যদি চিহ্ন দুটো না থাকে তা হলে ভাষাটাকেই নিঃসন্দিগ্ধ করে তুলতে হয়। তা হলে বিস্ময়সূচক বাক্যটাকে শুধরিয়ে বলতে হয়-“যে-বাবুয়ানা তুমি শুরু করেছ”। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮৯-৯০)
রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা ভাষার এই শিক্ষাটিই ধরিয়া রাখিতেন তবে তাহাকেও ‘কি’ বানান বদলাইবার প্রাণান্তকর ব্যায়ামটি করিতে হইত না। বানানের খরচ বাঁচিত, প্রয়োজনের বিঘ্ন হইত না।
দুঃখের মধ্যে সমস্যা শুদ্ধ বানানের খরচ লইয়া নহে। ঋণই আসল সমস্যা। ভাষার কাজ শুদ্ধ ভাবের প্রকাশ নহে। ভাষা ভাবের জন্মও দিয়া থাকে। সংস্কারও করে। রবীন্দ্রনাথ- আমার আশঙ্কা- এই কথাটিই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভাবের মাপে ভাষা হইয়া থাকে- এই সংস্কারটাই কবির বাক্যভ্রংশের গোড়ায় বলিয়া আমার ধারণা। মনুষ্যজাতির মধ্যে এহেন অহমিকা আকছার দেখা যায়। মানুষ ভাবিয়া থাকেন তিনি ভাষা তৈয়ার করিয়াছেন। অথচ সত্য তো ইহাও হইতে পারে- ভাষাই মানুষ তৈয়ার করিয়াছে।
মানুষ ভাষার প্রভু নহে- বরং ভাষাই মানুষকে পালন করেন। এই সত্যে যতদিন সন্দেহ থাকিবে ততদিন রবীন্দ্রনাথের মতন আমাদেরও বাক্যভ্রংশ রোগের শিকার হইতেই হইবে। আমি বা আপনি কিয়ৎ পরিমাণে ভাষার স্রষ্টা- এই বিশ্বাসই আমাদের আদিপাপ। আর কে না জানে পাপ বাপকেও ছাড়ে না। কেবল ভাষার অধীন থাকিয়াই মানুষকে ভাষার প্রেম জয় করিতে পারে। যে মানুষ ভাষার অধীনতা সহজে স্বীকার করে তাহাকেই আমাদের দেশের সাধকরা ‘সহজ মানুষ’বলিয়াছেন।
‘কি’সমস্যায়ও আমার এই বক্তব্য। দুই বানানে এক শব্দ লিখিবার এই অসম্ভব বাসনা অভিমানি প্রভুর বিকারগ্রস্ত বাসনা বৈ নহে। ভাষা নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করিতে সক্ষম, বিকাশ করিতে সক্ষম। কারণ ভাষা নিজেই আকাশ। আর ভাষার সকাশেই ভাবের হিসাব-নিকাশ। ভাষা মানে কি মাত্র বানান বা যতিচিহ্ন? কখনই না।
বঙ্কিমচন্দ্র বকলম কমলাকান্ত লিখিলেন, “কে গায় ওই?” তিনি ‘কে’পদে কি বুঝাইলেন? “কে”শব্দে নানা ভাবের প্রকাশ হইতে পারে। প্রশ্ন যদি হইত ‘কে গায়?’- শুদ্ধ ওইটুকুই, তবে জানিতাম উত্তর হইবে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ কি রামপ্রসাদ, কি অন্য কোন একজন। কিন্তু ‘ওই’ শব্দ জোড়া দিয়া বঙ্কিম সেই ভাবের সর্বনাশ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় যদি দৈবক্রমে দীর্ঘ একার বলিয়া কোন স্বরচিহ্ন থাকিতও তাহাতেও শান্তি হইত না। কে গায়? বলা মুশকিল। প্রশ্ন হয়, “গায়” বলিতেও বা কি বুঝাইল?
‘পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ-উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর; -মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাক্যের তন্ত্রীকে অঙ্গুলি স্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?’
কমলাকান্তের ‘উত্তর কি?’
একটা উত্তর এই রকম:
‘ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল- তাই এই সংগীত এত মধুর লাগিল। শুদ্ধ তাই নয়। তখন সংগীত ভাল লাগিত- এখন লাগে না- চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম- সেই সময়ে এই পূর্বস্মৃতিসূচক সংগীত কর্ণে প্রবেশ করিল। তাই এত মধুর বোধ হইল।’
যথার্থ উত্তরণ হইল কি? কমলাকান্ত জানেন, হয় নাই।
‘-কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতিধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সংগীত, তেমনি সংসারের এক সংগীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সংগীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সংগীত আর কি শুনিব না?’
এতক্ষণে বুঝিলাম, ‘কে গায়?’-ওটা একটা কথার কথা মাত্র। গায়কের পরিচয় নিশ্চয় করিয়া জানা জিজ্ঞাসাকর্তার আদত উদ্দেশ্য ছিল না। এই যে কথার কথা-ইহার নামই ভাষার পালনক্ষমতা।
‘শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনিসংমিলিত বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারসংগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই- সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতিধ্বনিতে কর্ণাধার পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী- ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।’ (বঙ্কিম রচনবাবলী, খণ্ড ২, মু. ১৪, পৃ, ৪৫-৪৭)
হ্রস্ব ইকারের অধিকার যেখানে খাস্ বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সেখানে হ্রস্ব ইকারের অধিকার, সুতরাং দীর্ঘ ঈ’র সেখান হইতে ভাসুরের মতো দূরে চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য।’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব , পৃ. ১১২) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ‘বাঙ্গালা বানান সমস্যা’ নামে এক প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলেন বাংলা ১৩৩১ সালে। তাহার পরের বছর মাত্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বকলম প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বাহির হয় রবীন্দ্রনাথের আদেশ- বাংলা ‘কি’ শব্দ দুই বানানে লিখিতে হইবে। শহীদুল্লাহর বিষয় ছিল খানিক ভিন্ন। তিনি বলিতেছিলেন বাংলার সকল শব্দই উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিতে হইবে। তাঁহার বক্তব্য ছিল, শ্রবণ করা অর্থে বাংলায় ‘শোনা’ শব্দ লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু স্বর্ণ অর্থে তাহা কেন ‘শোনা’ লেখা হইবে না? একটা উত্তর- সংস্কৃত স্বর্ণ শব্দে দন্ত্য ‘স’ আছে, তাই ‘সোনা’ লেখাই স্বাভাবিক। তিনি বলিলেন, ‘সোনা’ শব্দের উচ্চারণ তো ‘শোনা’। তাই ‘শোনা’ লেখাই তো উচ্চারণের বিচারে স্বাভাবিক।
তখন আপত্তি উঠিতেছে, ‘স্বর্ণ’ আর ‘শ্রবণ করা’ দুই অর্থ, দুই ভাব। এই ভাবের তফাত বজায় রাখিতে হইলে বানানের তফাত রাখার দরকার আছে। স্বর্ণ অর্থের ব্যঞ্জনা আর ‘শ্রবণ করা’র ব্যঞ্জনা কি এক জিনিস? উভয়ের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক ‘শোনা’শব্দে দুই ভাব প্রকাশ হইবে কি করিয়া? অথবা ‘সোনা’আর ‘শোনা’ দুই বানানই রাখিতে হয়। ইহার জবাবেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিলেন : ‘যদি বল এ কি হইল! স্বর্ণ আর শ্রবণ করা দুই-ই যদি শোনা হয়, তবে মানে বুঝিব কেমন করিয়া?’
“আমি বলিব যদি গায়ের তিলে গাছের তিলে কোন গোল না ঠেকে, যদি গানের তালে আর নাচের তালে ঠোকাঠুকি না ঘটে, তবে স্বর্ণ শোনায় আর শ্রবণ শোনায়ও কোন হাঙ্গামা হইবে না। আসল কথা, ভাষায় অক্ষরের মত শব্দ কখন দল ছাড়া হইয়া একেলা আসে না। অক্ষর থাকে শব্দের সঙ্গে জড়াইয়া আর শব্দ থাকে বাক্যের মধ্যে মিশিয়া। কাজেই মানে যদি আলাদা আলাদা হয়, তবে বানান বা উচ্চারণ এক হইলেও বুঝিবার গোলমাল বড় একটা হয় না।” (ভাষা ও সাহিত্য, স. ৩, পৃ. ৮১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু জায়গায় কবুল করিয়াছেন তিনি ব্যাকরণে কাঁচা। তাঁহার ভাষায়, ‘কী সংস্কৃত ভাষায় কী ইংরেজিতে আমি ব্যাকরণে কাঁচা’। কিন্তু বাংলায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হয় না বাংলা ব্যাকরণ তিনি আর কাঁহারও অপেক্ষা কম জানেন। তবু তাঁহার বিনয়কে অবিশ্বাস করিব না। তিনি জানাইয়াছেন, “ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাত এই- তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোলবিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে-চলা-পথের ভ্রমণকারী।” (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৯) বৈষ্ণব ভাবিয়া বিনয়কে তুচ্ছ করিবেন না।
পায়ে চলা পথের এক জায়গায় শেষ হয়। সে কথা কবির অজানা নয়। পায়ের পথিক ভূগোলে অপটু হইতেই পারেন। তাহাতে দোষ নাই। দোষ অপটুতাকে ধর্মের মর্যাদা দেওয়ায়। ঠাকুর মোটেও নিশ্চিত হইতে পারেন নাই, বাংলা ‘কি’ শব্দটি কি, অর্থাৎ কোন জাতের? তিনি একবার বলিয়াছেন শব্দটি অব্যয়, আর বার বলিয়াছেন সর্বনাম। আগে এই প্রশ্নটির মীমাংসা না করিয়া হাঁটিতে শুরু করা পায়ে চলার কাজ সন্দেহ নাই, ভূগোলবিজ্ঞানীর কাজ এ রকম নহে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শব্দটি বিশেষণ হইয়া যায়। আবার আরো বিশেষ করিয়া দেখিলে ইহাকে ‘ক্রিয়া বিশেষণ’ হিসাবেও দেখা যায়। প্রয়োজনে সে বিশেষ্যের ভূমিকাও লইতে পারে। ক্রিয়ার কাজও কখনো বা সে করিলে বিস্ময়ের থাকিবে না।
এই যে বিভিন্ন প্রয়োগ, বিবিধ ব্যবহার তাহার মধ্যে কি কোনই ঐক্য নাই? সেই ঐক্যের নিয়মের সূত্র যতদূর জানি পহিলা রাজা রামমোহন রায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাবিতে শিহরিয়া উঠি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি সেই আবিষ্কারের খবর লয়েন নাই? না লইবার কোন কারণ তো নাই। তবে আলামত দেখিতেছি। ঠাকুরের লেখায় ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ বলেন :
“প্রশ্নসূচক ‘কি’ শব্দের অনুরূপ আর-একটি ‘কি’ আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম। এ তার প্রকৃত অর্থের প্রয়োজন সেরে মাঝে মাঝে খোঁচা দেবার কাজে লাগে। যেমন : কী তোমার ছিরি, কী যে তোমার বুদ্ধি।” (‘বাংলা ভাষা-পরিচয়’, পৃ. ১১৩)
রামমোহন ভাল করিয়া পড়া থাকিলে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়া লইতেন, বাংলায় ‘কি’ শব্দ একটাই। কারকভেদে (অথবা রামমোহনের ভাষায় ‘পরিণমন’ বা ‘পরিণাম’ ভেদে) ইহার রূপভেদ হয় মাত্র। যেমন ‘কি’ শব্দ কর্তৃকারকে (রামমোহনের ভাষায় ‘অভিহিত’ পদে) যেমন ‘কি’ কর্মকারকেও তেমনি ‘কি’ই। অধিকরণে ‘কিসে’ অথবা ‘কিসেতে’ আর সম্বন্ধে ‘কিসের’। সবগুলিই ‘কি’ শব্দের আত্মীয়রূপ বৈ নহে। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৮)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দেখাইয়াছেন, রামমোহনের ব্যাকরণে একটু অপূর্ণতা আছে। কি, কিসে, কিসেতে, কিসের প্রভৃতি সকল শব্দরূপের গোড়া মাত্র ‘কি’ নহে। ‘কি’ শুদ্ধ সকলেরই গোড়া হইল অন্য একটি রূপ- কাহা (বা কাঁহা)। ইহা ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। জাতিতে সর্বনাম। ইহার সহিত তুলনীয়, সহধর্মিণী আরও সর্বনাম শব্দ আছেন, যথা: তাহা, যাহা, ইহা, উহা ইত্যাদি।
তবে কাহা শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া তাহার রূপের খানিক বিশেষত্ব রহিয়াছে। এই শব্দে বিভক্তির একবচন রূপ কর্তা ও কর্ম দুই কারকেই ‘কি’। বহুবচনে ‘কিসের’। তবে শহীদুল্লাহ লিখিয়াছেন, “কাহা শব্দের ক্লীবলিঙ্গের বহুবচনে প্রয়োগ নাই। কখনও কখনও বহুবচন বুঝাইতে দ্বিরুক্তি হয়। যথা- কি কি হইয়াছে? সে কি কি লইয়াছে?” (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, স. মাওলা ব্রাদার্স, মু. ২, পৃ. ৭৮)
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মোটেও কেমাল পাশা নহেন। তিনিও প্রচলিত ব্যাকরণের মতো বাংলায় ছয় কারকই দেখাইয়াছেন। রামমোহন বলিয়াছেন, বাংলায় দরকারই নাই অত কারকের। তাঁহার বয়ান : “গৌড়ীয় ভাষাতে নামের চারি প্রকার রূপের দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অভিহিত, যেমন রাম, কর্ম্ম, যেমন রামকে; অধিকরণ, যেমন রামে; সম্বন্ধ, যেমন রামের।” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১৩) রামমোহনের কথাই সঠিক বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। আরো মনে করিতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ও রামমোহনের কথানুসারে অমৃত হইয়াছিল।
‘যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার বোধের নিমিত্ত ভাষাতে অভিহিত পদের পরে “দিয়া” শব্দের প্রয়োগ করা যায়, যেমন, ছুরি দিয়া কাটিলেন। আর কখন [কখন] সম্বন্ধ পরিণামের পরে “দ্বারা” শব্দ দিয়া ঐ করণকে কহা যায়; যেমন, ছুরির দ্বারা কাটিলেন।’(পৃ. ১৫) আরো পড়া যাইতেছে : ‘কখন বা অধিকরণ বাচক বিভক্তির দ্বারা করণের জ্ঞান হইয়া থাকে, যদি সেই করণ অপ্রাণি হয়; যেমন, ছুড়িতে কাটিলেন। অতএব করণের নিমিত্ত শব্দের পৃথক রূপ করিবার আবশ্যক দেখি নাই।’ (পৃ. ১৫) শহীদুল্লাহ করিয়াছেন, ‘কি দিয়া, কিসের দ্বারা, কিসে।’ দরকার ছিল কি? (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, মু. ২, পৃ. ৭৭)
একই কারণে রামমোহন বলিলেন, বাংলায় অপাদান কারকেরও প্রয়োজন নাই। পড়া যাইতেছে :
‘কোন এক ক্রিয়ার বক্তব্য স্থলে যখন অন্য বস্তু হইতে এক বস্তুর নিঃসরণ অথবা ত্যাগ বোধ হয়, তখন তাহার জ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রথম বস্তুর নামের পরে যদি সেই প্রথম বস্তু একবচনান্ত হয় তবে “হইতে” এই শব্দের প্রয়োগ করা যায়। আর যদি বহুবচনান্ত হয় তবে বহুবচনান্ত সম্বন্ধীয় পরিণাম পদের পরে “হইতে” ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন গ্রাম হইতে, মন্ত্রিদের হইতে, বেণেদের হইতে, অতএব বঙ্গভাষায় অপাদান কারকের নিমিত্ত শব্দের পৃথক রূপ করিবার আবশ্যক নাই।’ (পৃ. ১৫)
তদ্রূপ “সম্বোধনের নিমিত্তেও শব্দের পৃথক রূপের প্রয়োজনাভাব” বলিয়া রামমোহন তাহার আলাদা প্রকরণ করেন নাই। সম্প্রদান সম্বন্ধেও একই কথা খাটিবে : “ভাষাতে রূপান্তরাভাব, এই হেতুক লিখা গেল না।” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১৪, পাদটীকা ৩)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সহিত পণ্ডিত হরনাথ ঘোষ আর সুকুমার সেনের ব্যাকরণও একমত। ঘোষ ও সেনের বইতে ‘কাহা’ শব্দের সম্ভমসূচক একটা রূপও পাওয়া যাইতেছে- কাঁহা বা সংক্ষেপে কাঁ। (বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ, পৃ. ২৭৫)
এই সকল কিছু না দেখিয়াই, না চিন্তিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, শ্যামাপ্রসাদ, আইন কর। বাংলাভাষার অনেক মহদুপকার রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা তো তাহাকে “কি” শব্দের বানান বদলাইবার অধিকার দেয় নাই। এয়াহুদিপুরানে বলে, সন্তানের গলা কাটিবার অধিকার স্বয়ং ভগবানও এব্রাহিমকে দেন নাই। তিনি তাঁহাকে পরীক্ষা মাত্র করিতেছিলেন। দীপ্তি হউক বলিলেই ভাষায় দীপ্তি হয় না। কোন ভাষাই মাত্র ছয় দিনে তৈরি হয় নাই। রামমোহনে ফিরিয়া চল ‘কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিশেরও জোর।’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৯
রাজা রামমোহন রায় দেখাইয়াছেন ভাষার তাবৎ শব্দ প্রথমত দুই প্রকারে বিভক্ত হয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ। “যে শব্দের অর্থ প্রাধান্যরূপে জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাকে বিশেষ্য কহে; যেমন, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর, ইত্যাদি স্থলে রামের জ্ঞান প্রাধান্যরূপে হয়, এ নিমিত্তে রাম বিশেষ্য।
“আর যাহার অর্থ অপ্রাধান্য রূপে বুদ্ধির বিষয় হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর ইত্যাদি স্থলে যাইতেছেন ও সুন্দর এ দুই শব্দের অর্থ রাম শব্দের অর্থেতে অনুগত হয়, এ কারণ বিশেষণ পদ কহে।” (পৃ. ১১)
রামমোহনের ব্যাকরণে বিশেষ্য নানা প্রকারের হয়। বিশেষ্যকে ‘নাম’ অথবা ‘সংজ্ঞা’ দুইটাই বলিয়াছেন তিনি। এই কাণ্ডজ্ঞান অনুসারে “কাহা” শব্দও একপ্রকার ‘সংজ্ঞা’ বা ‘নাম’ শব্দ। সুতরাং ভাষার প্রথম দুই ভাগ অনুসারে কাহা শব্দের জাতক ‘কি’ শব্দ বিশেষ্য। বিশেষ্য বা সংজ্ঞার মধ্যে ইহা প্রতিসংজ্ঞা বা সর্বনাম জাতীয় হইয়াছে। রামমোহনের সহিত সম্যক পরিচয় থাকিলে ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ বইতে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করিতে হইত না, “প্রশ্নসূচক ‘কি’শব্দের অনুরূপ আর-একটি ‘কি’আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম।” (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ১১৩)
সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় কি শব্দ আদিতে সর্বনাম, তবে অব্যয় হিসাবে তাহার প্রয়োগ আছে। অন্য প্রয়োজনেও তাহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। রামমোহন লিখিয়াছেন : “বিশেষ্য পদকে নাম কহি, অর্থাৎ এ রূপ বস্তুর নাম হয় যাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে। যেমন রাম, মানুষ, ইত্যাদি। অথবা যাহার উপলব্ধি কেবল অন্তরিন্দ্রিয়-দ্বারা হয় তাহাকেও এইরূপ নাম কহেন, যেমন ভয়, প্রত্যাশা, ক্ষুধা ইত্যাদি।”
‘ঐ নামের মধ্যে কতিপয় নাম বিশেষ ব্যক্তির প্রতি নির্ধারিত হয়, তাহাকে ব্যক্তি সংজ্ঞা কহি, যেমন রামচরণ, রামভদ্র, ইত্যাদি। আর কতিপয় নাম এক জাতীয় সমূহ ব্যক্তিকে কহে, তাহাকে সাধারণ সংজ্ঞা কহি, যেমন মনুষ্য, গরু, আম্র, ইত্যাদি। এবং কতক নাম নানাজাতীয় সমূহকে কহে, যাহার প্রত্যেক জাতি অন্য [অন্য] জাতি হইতে বিশেষ [বিশেষ] ধর্ম্মের দ্বারা বিভিন্ন হয়, তাহাকে সর্ব্বসাধারণ বা সামান্য সংজ্ঞা কহি, যেমন ‘পশু’, মনুষ্য, গরু, হস্তি প্রভৃতি নানাবিধ বিজাতীয় পদার্থ সমূহকে কহে। এবং “বৃক্ষ” নানাবিধ বিজাতীয় আম, জাম, কাঁটাল ইত্যাদিকে প্রতিপন্ন করে’।
‘ঐ নামের মধ্যে কতিপয় শব্দ ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হয়, অথচ ঐ সকল শব্দ স্বয়ং স্বতন্ত্র বিশেষ [বিশেষ] ব্যক্তিকে কিম্বা বিশেষ ব্যক্তিসমূহকে নিয়ত অসাধারণরূপে প্রতিপন্ন করে না, ওই সকলকে প্রতিসংজ্ঞা কহি, যেমন আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি।’ (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১১-১২, নিম্নরেখা আমরা যোগাইয়াছি)
একইভাবে রামমোহন রায় বিশেষণ শব্দেরও নানান জাতি নির্ণয় করিয়াছেন। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে যে সকল শব্দকে বিশেষণ বলা হইয়া থাকে, তাহাদের নাম রামমোহন রাখিয়াছেন ‘গুণাত্মক বিশেষণ’। লিখিয়াছেন : ‘বিশেষণ শব্দের মধ্যে যাহারা বস্তুর গুণকে কিম্বা অবস্থাকে কাল সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কহে, সে সকল শব্দকে গুণাত্মক বিশেষণ কহি, যেমন, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি।’(গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১২, নিম্নরেখা আমরা যোগ করিয়াছি)
“আর যাহারা কালের সহিত সম্বন্ধপূর্ব্বক বস্তুর অবস্থাকে কহে, তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, আমি মারি, তুমি মারিবে।” প্রচলিত ব্যাকরণে এই পদের নাম ‘ক্রিয়া’মাত্র। ক্রিয়ার অপর নাম ‘আখ্যাত’পদ। ইহা ভাষায় ব্যবহার্যও হইয়াছে। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ৩২)
গুণাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক ছাড়াও রাজা রামমোহন রায় আরও পাঁচ জাতের বিশেষণ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে, ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ, সম্বন্ধীয় বিশেষণ, সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ এবং অন্তর্ভাব বিশেষণ রহিয়াছে। মনোযোগ করিবার বিষয়, অব্যয়ের জন্য তিনি কোন আলাদা প্রকরণ করেন নাই।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের তারিফ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার এই অব্যয় জাতীয় শব্দের আলাদা প্রকরণ না করার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি শুদ্ধ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন: “রামমোহন ‘সর্বনাম’-কে বলেছেন ‘প্রতিসংজ্ঞা’, এর সঙ্গে তুলনীয় পঞ্জাবীতে ব্যবহৃত নাম ‘পড়নাঊঁ’ (= প্রতিনাম)। নামটি সার্থক, ‘সর্বনাম’এই শব্দের মতো এর ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন থাকে না। ‘প্রতিনাম’শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার জন্যে আমি ‘সর্বনাম’-এর পাশে ‘প্রতিনাম’ শব্দটিও আমার বাঙলা ব্যাকরণে ব্যবহার করেছি।” (মনীষী স্মরণে, পৃ. ৬)
রামমোহন দেখিয়াছেন ভাষায় অব্যয়ের কাজ বিশেষণেরই কাজ। তিনি কাজ দেখিয়া নাম করিয়াছেন, রূপ দেখিয়া ভোলেন নাই। তাই অব্যয় শব্দের আলাদা প্রকরণ করার “প্রয়োজনাভাব” হইয়াছে। কয়েক গুটি উদাহরণ লইলেই আবিষ্কারটি পরিচ্ছন্ন হইবে। মেঘ কাটিয়া যাইবে।
ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণকে ইংরেজিতে বলে ‘পার্টিসিপ্ল্’। ইহা কি পদার্থ? রামমোহন কহেন, “যাহারা অন্য ক্রিয়াগত কালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তুর কাল সংক্রান্ত অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি প্রহার করত বাহিরে গেলেন, ভোজন করিতে [করিতে] কহিয়াছিলেন।” (পৃ. ১২)
আর “যাহারা ক্রিয়া কিংবা গুণাত্মক বিশেষণের অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি শীঘ্র যান, তিনি অত্যন্ত মৃদু হন।” (পৃ. ১২)
প্রচলিত ব্যাকরণের অব্যয়কেও রামমোহন ‘বিশেষণ’রূপেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যথা : “যে সকল শব্দকে পদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিয়মমতে রাখিলে সেই পদের সহিত অন্য পদের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ বুঝায়, সেই শব্দকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি; যেমন রামের প্রতি ক্রোধ হইয়াছে।” (পৃ. ১২) ইংরেজিতে এইসব পদকে প্রিপোজিশন কহে।’
‘রামের’পদ বানাইতে রাম শব্দের সহিত যাহা যোগ করা হইয়াছে (এর), তাহাতে বুঝাইত শুদ্ধ ক্রোধের কর্তা রাম। তবে কিনা ‘প্রতি’শব্দটি বসিয়া রামকে ক্রোধের গৌণকর্ম বানাইয়া সারিয়াছে। এই প্রতিশব্দটি বাংলায় ‘অনুসর্গ’ বলিয়াই কথিত হয়। রামমোহন রায়ের লেখা বাংলা ব্যাকরণের ইংরেজি-সংস্করণে এই জাতের পদকেও ‘প্রিপোজিশন’ বলা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। (নির্মল দাশ, বাংলা ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৪৭)
বিশেষণের চতুর্থ প্রকারের (অব্যয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী) নাম সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ। রামমোহন উল্লেখ করিলেন,
“যাহারা দুই বাক্যের মধ্যে থাকিয়া ঐ দুই বাক্যের অর্থকে পরস্পর সংযোগ কিংবা বিয়োগরূপে বুঝায়, অথবা দুই শব্দের মধ্যে থাকিয়া এক ক্রিয়াতে অন্বয় বোধক হয়, কিন্তু কোন শব্দের বিভক্তির বিপর্য্যয় করে না, সে সকল শব্দকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি : যেমন, তিনি আমাকে অশ্ব দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি লইলাম না; আমি এবং তুমি তথায় যাইব, আমাকে ও তোমাকে দিয়াছেন।”
ইংরেজিতে এইগুলি ‘কনজাংশন নামে চলে’। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১২)
পঞ্চম জাতীয় বিশেষণ (তৃতীয় শ্রেণীর অব্যয়) রামমোহনের বয়ানে এই রকম : “যাহারা অন্য শব্দ সংযোগ বিনাও ঝটিতি উপস্থিত অথবা অন্তকরণের ভাবকে বুঝায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি; যেমন, হা আমি কি কর্ম্ম করিলাম!” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১২-১৩)
এতক্ষণ একটু লম্বা শ্বাস টানিয়া রামমোহন পড়িবার কারণ কি? বাংলা ব্যাকরণে ‘কি’ শব্দ প্রতিসংজ্ঞা জাতীয় [অর্থাৎ বিশেষ্য কুলোদ্ভব] হইলেও বিশেষণকুলে হামেশাই তাহার যাতায়াত আছে- এই কথা প্রমাণ করার আবশ্যক দেখি আজিও ফুরাইল না। অথচ তাহার কুল পরিচয় প্রতিসংজ্ঞাতেই পাওয়া যাইবে। চেহারা দেখিয়া লোকে পরিচয় তারপরও ভুলিয়া যায়। এই কথা এখনও সত্য।
বাংলায় “আমি”, “তুমি”, “সে” প্রভৃতি শব্দের যে জাত “যে” শব্দেরও সেই জাতই। আমিকে “ইতর লোকে” “মুই” কহিয়া থাকে। তুচ্ছতা প্রকাশের নিমিত্ত “তুমি” স্থানে “তুই” হইয়া থাকে। “সে শব্দের প্রয়োগ অপ্রত্যক্ষ বস্তু বা ব্যক্তি যাহার জ্ঞান বা উল্লেখ পূর্বে থাকে তাহার স্থলে হয়, যেমন সে চৌকি, সে ব্যক্তি। “যখন সম্মান তাৎপর্য্য হইবেক তখন সে ইহার স্থানে তিনি কিম্বা তেঁহ আদেশ হয়, আর অন্য তাবৎ পরিনামে [কারকে] প্রথম স্বর সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন, তাঁহাকে, তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের, ইত্যাদি।” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৬)
“সে” শব্দের আরেক রূপ “এ”। বস্তুর কিম্বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ-অভিপ্রেত হইলে “এ”শব্দের প্রয়োগ হয়। সম্মান অভিপ্রেত হইলে “এ”স্থানে “ইনি”আদেশ হয় এবং প্রথম স্বরেরও সানুনাসিক উচ্চারণ হয়। “কিয়দন্তর পরোক্ষ অভিপ্রেত হইলে “ও” শব্দের প্রয়োগ হয়, আর তাহার রূপ “এ” শব্দের মতন হইয়া থাকে। কেবল ওকারের স্থানে “উ”হইয়া থাকে। সম্মান অভিপ্রেত হইলে “ও”স্থানে উনি আদেশ হয়, আর প্রথম স্বরের সানুনাসিক উচ্চারণ হয়।”
“যে” শব্দ আসিয়াছে “যাহা” হইতে। এই শব্দ প্রতিসংজ্ঞা বা সর্বনাম। ইহার রূপও ‘সে’শব্দের ন্যায় হয়। অর্থাৎ সে, তাহাকে, তাহাতে, তাহার ইত্যাদির ন্যায় যে, যাহাকে, যাহাতে, যাহার ইত্যাদি হয়। সম্মান অভিপ্রেত হইলে যিনি, যাঁহাকে, যাঁহাতে, যাঁহার ইত্যাদি রূপে পরিণাম হয়।’ (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৭)
এখন ‘কাহা’ শব্দের রূপ। আবারও রামমোহন হইতে সাক্ষাৎ উদ্ধার করিতেছি:
‘জিজ্ঞাসার বিষয় পদার্থ যদি ব্যক্তি হয় তবে কে, আর যদি বস্তু হয় তবে কি, ইহার প্রয়োগ হয় কিন্তু অধ্যাহৃত কিম্বা উক্ত ক্রিয়া যাহার যোজক হইয়াথাকে, যেমন কে কহিয়াছিল? এ স্থলে বাক্যের অর্থ কে কহিয়াছিল উক্ত হইয়াছে; কি? অর্থাৎ কে বসিয়াছে, বা গিয়াছে। এ স্থলে ক্রিয়া উহ্য হইল, এবং কি কহিতেছে? কি? অর্থাৎ কি হয় ইত্যাদি।’ (পৃ. ২৭; নিম্নরেখার যোগান দিয়াছি, নিরেট লিখনরীতি রামমোহন রায়ের)
‘যাহা’শব্দের যে রূপ, কাহা শব্দেরও সেই রূপই হইয়া থাকে। “প্রভেদ এই যে সম্মান অভিপ্রেত হইলেও বিশেষ নাই।” (পৃ. ২৭) অর্থাৎ ‘যিনি’র ন্যায় ‘কিনি’ হয় না।
যদি সময় জিজ্ঞাস্য হয় তবে, “কবে”আর “কখন”শব্দের প্রয়োগ হয়। ইহাদের রূপান্তর নাই। তবে “ওই দুয়ের প্রভেদ এই যে, কবে, ইহার প্রয়োগ দিন জিজ্ঞাস্য [হইলে]; আর, কখন, ইহার প্রয়োগ সময় জিজ্ঞাস্য হইলে প্রায় হইয়া থাকে, যেমন কবে যাইবে? অর্থাৎ কোন্ দিন যাইবে? কখন যাইবে? অর্থাৎ কোন্ সময়ে যাইবে।” (পৃ. ২৮)
একই নিয়মে অন্যান্য প্রতিসংজ্ঞারও প্রয়োগ হয়। “যখন স্থান জিজ্ঞাস্য হয় তখন “কোথা” কিম্বা “কোথায়” ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কোথা যাইবে, কোথায় যাইবে? অবস্থা কিম্বা প্রকার ইহার জিজ্ঞাস্য হইলে-“কেমন” শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা কেমন আছেন? ইহার রূপান্তর নাই।” (পৃ. ২৮)
রামমোহনের বিভাজন অনুসারে কি শব্দ অব্যয় নয়, কারণ ইহার ব্যয় বা রূপান্তর আছে। শুদ্ধমাত্র অভিহিত পদ আর কর্মকারকেই ইহা একরূপ থাকে। অন্য পক্ষে “নান্ত কোন্ শব্দ”অব্যয়। কে, কি, কবে, কোথা প্রভৃতি শব্দ নান্ত কোন্ শব্দের প্রতিনিধি হয়। যেমন কে- কোন্ জন? কি- কোন্ বস্তু? কবে- কোন্ দিন, কোথা- কোন্ স্থান ইত্যাদি। কিন্তু খোদ “কোন্”শব্দটি অব্যয় পদবাচ্য। “ইহার রূপান্তর হয় না। আর বিশেষণ পদের ন্যায় ব্যবহার হয়।
“কোন্”শব্দের উচ্চারণ যখন “হলন্ত”বা “নান্ত”না হইয়া অকারান্ত বা ওকারান্ত হয়, তখন কোন জাতিবাচক শব্দের অনির্দ্ধারিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হয়, কাহাকেও নির্দিষ্ট ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হয় না। অকারান্ত বা ওকারান্ত ‘কোন’শব্দ বিশেষণের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে; যেমন, কোন মনুষ্য ঘরে আছে? অর্থাৎ মনুষ্যের কোন এক ব্যক্তি ঘরে আছে? কোন পুস্তক পেটরাতে আছে? অর্থাৎ পুস্তকের কোন এক খান পেটরাতে আছে?” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৮)
‘অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হইলে, কেও [কেউ], কিম্বা কেহ, ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কেও ঘরে আছে, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি ঘরে আছে? আর কোন শব্দ ও কেহ শব্দ যখন দ্বিরুক্তি হয় তখন প্রশ্ন অভিপ্রেত না হইয়া অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি সকলকে বুঝায়, যেমন কোন [কোন] ব্রাহ্মণ, কোন [কোন] রাজা ইত্যাদি।’ (পৃ. ২৮, নিম্নরেখা আমরা যোগাইয়াছি)
রামমোহন তাড়াহুড়া করিয়া লিখিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি দেখাইতে পারিতেন এই প্রণালীতে ‘কেন’এবং ‘কিছু’ শব্দও নিষ্পন্ন হইয়াছে। “কেন”মানে কি কারণে, কি হেতু ইত্যাদি। আর “কিছু”শব্দেরই প্রয়োগ হয় অনির্দ্ধারিত কোন বস্তু জিজ্ঞাসাস্য হইলে, যেমন- ঘরে কিছু খাবার আছে? ইহা “কি”শব্দের রূপান্তর। একই সঙ্গে ইহার প্রয়োগ বিশেষণের ন্যায়ও বটে। বিশেষ্যের ন্যায়ও হইতে পারে, যেমন-‘কিছু হইয়াছে?’ ‘কিছু বলিবে?’ ইত্যাদি।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৮৬ সনে জন্ম লইবার পর হইতেই সংস্কার কাজে মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। ২০০৫ সালে তাঁহাদের বানানবিধির পঞ্চম সংস্করণ ছাড়া হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অর্থগত প্রয়োগ ধরিয়া কি ‘কর্মবাচক সর্বনাম’ কি ‘প্রশ্নমূলক সর্বনাম’, কি ‘বিশেষণের বিশেষণ’-সকল ক্ষেত্রেই ‘কি’বানান ‘কী’লেখা হইবে। একই সঙ্গে তাঁহারা বিধান দিয়াছেন ‘বিকল্পাত্মক বিশেষণ’ [যাহাকে কেহ কেহ ‘সমুচ্চয়ার্থক বিশেষণ’ও বলিতে পারেন] হিসাবেও ‘কী’চলিবে।[১২.১] (আকাদেমি বানান অভিধান, স. ৫, পৃ. ৫৫৪)
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন “‘কী’শব্দের করণ কারকের রূপ : কিসে, কিসে ক’রে, কী দিয়ে, কিসের দ্বারা। অধিকরণের রূপও ‘কিসে’যথা: এ লেখাটা কিসে আছে।” (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৯৯)
আর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি লিখিতেছেন : “বিকল্পাত্মক বিশেষণ হিসেবেও কী ব্যবহৃত হবে: কী রাম কী শ্যাম, দুটোই সমান পাজি! এইসঙ্গে সমজাতীয় ব্যাকরণসূত্রে কীসে এবং কীসের দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লেখা উচিত এবং তার প্রচলন বাড়ছে’।” (বিধি ১২.১)
জানি সব শিয়ালের এক রা। প্রভেদ মধ্যে মধ্যে। প্রভেদের মধ্যে ঢাকার বাংলা একাডেমি ‘বিকল্পাত্মক বিশেষণ’কে এখনও অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়া লিখিবার পক্ষে। প্রমাণ : “অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন : তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।” [.০১] (প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম; ৩য় সংস্করণ) ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, স. ২, পৃ. ১২২১) প্রভুর ছলের অভাব নাই “প্রেমনারায়ণ বিরক্ত হইয়া আপন মনের কথা আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন-চাক্রি করা ঝক্মারি- চাকরে কুকুরে সমান- হুকুম করিলে দৌড়িতে হয়। মতে, হলা, গদার জ্বালায় চিরকালটা জ্বলে মরেছি- আমাকে খেতে দেয় নাই- শুতে দেয় নাই- আমার নামে গান বাঁধিত- সর্ব্বদা ক্ষুদে পিঁপড়ার কামড়ের মত ঠাট্টা করিত- আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত ও মধ্যে [মধ্যে] আপনারাও আমার পেছনে হাততালি দিয়া হো হো করিত। এসব সহিয়া কোন ভাল মানুষ টিকিতে পারে? ইহাতে সহজ মানুষ পাগল হয়। আমি যে কলিকাতা ছেড়ে পলাই নাই এই আমার বাহাদুরি- আমার বড় গুরুবল যে অদ্যাপিও সরকারগিরি কর্ম্মটি বজায় আছে। ছোঁড়াদের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এখন জেলে পচে মরুক- আর যেন খালাস হয় না- কিন্তু এ কথা কেবল কথার কথা, আমি নিজেই খালাসের তদ্বিরে যাইতেছি। মনিবওয়ারি কর্ম্ম। চারা কি? মানুষকে পেটের জ্বালায় সব করিতে হয়।” -টেকচাঁদ ঠাকুর (আলালের ঘরের দুলাল, পৃ. ২৩)
বাংলা আকাদেমির দ্বিতীয় অবয়বের নাম উচ্চারণে বল প্রয়োগ বা শ্বাসের আঘাতের বিষয় হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই যুক্তির বয়ান রাজশেখর বসু সহজেই করিয়াছিলেন।
চলন্তিকা অভিধানে রাজশেখর ‘কী’শব্দের অর্থ দিয়াছিলেন : “বেশী জোর দিতে, যথা- কী সুন্দর! তোমার কী হয়েছে?” মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বলিয়াছিলেন, “আরও কোন কোন অভিধানে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে পারিতেছি না।” (বাংলা বানান, পৃ. ৮০)
সত্য বলিতে উল্লেখ করিবার মত সকল বাংলা অভিধানে ইহাই আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষের অভিধানে লেখেন :
‘মৈথিলী বা উত্তরবিহারী ভাষায় ‘কি’ও ‘কী’র প্রভেদ নাই। (Grierson’s Maithili Dialect, Pt. I., Grammar, 2nd edition, pp. 99-101) তার অনুকরণে প্রাচীন বাংলায়ও ‘কি’ ও ‘কী’নির্ব্বিশেষে প্রচলিত হয়।” জ্ঞানেন্দ্রমোহন আরও জ্ঞান দিয়াছেন, কী শব্দটি ‘মধ্য বাংলা সাহিত্যে অপ্রচলিত। অধুনা কোন কোন লেখক কর্ত্তৃক পুনঃপ্রচলিত।’
সুকুমার সেন প্রণীত ‘বুৎপত্তি-সিদ্ধান্ত বাংলা-কোষ’অভিধানেও ‘কী’শব্দের কোন জায়গা হয় নাই। কিন্তু ‘কি’শব্দের পাঁচ রকম অর্থ দেওয়া হইয়াছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে এই অভিধানের ইংরেজি সংস্করণ পহেলা ১৯৭১ সালে বাহির হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণ খোদ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি হইতে বাজারে আসিয়াছে।
‘বুৎপত্তি সিদ্ধান্ত’ অনুসারে, “কি” শব্দ প্রশ্নবাচক, অনির্দেশক সর্বনাম। ইহা শেষ বিচারে সংস্কৃত “কিম্” হইতে আসিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের প্রয়োগ এই অর্থেই : ‘কি লআঁ যাইব ঘর’।
“কি” শব্দের দ্বিতীয় প্রয়োগ প্রশ্নবাচক অব্যয়ে আকারে। সুকুমার সেন দুই দুইটি প্রয়োগ দেখাইতেছেন এই অর্থে। দুইই চর্যাপদ হইতে, ‘দুহিল দুধু কি বেন্টে যামায়’ (চর্যা ৩৩) এবং ‘ভাগ তরঙ্গ কি সোসঈ সাঅর’ (চর্যা ৪২)
“কি” শব্দের তৃতীয় প্রয়োগও অব্যয় আকারে। এই প্রয়োগের অর্থে, সুকুমার সেন যাহাকে বলেন ‘দ্বৈধ’সেই ভাবই বুঝাইতেছে। বাংলা আকাদেমির লোকেরা হয়তো বা বলিবেন ‘বিকল্পাত্মক’, কিংবা “সমুচ্চয়বোধক”। এই প্রয়োগও চর্যাপদ হইতে, “জামে কাম কি কামে জাম’। (চর্যা ২২)
কি শব্দের আরো প্রয়োগ “না” শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ঘটে। দুইপদ যুক্ত হইয়া একই সঙ্গে সংশয় ও প্রশ্ন দুইটাই সূচনা করে।
“কি” আরও অর্থে প্রয়োগ করা চলে। সুকুমার সেনের পাঁচ নম্বর অর্থ বুঝাইতে সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী বিভক্তি আকারে ইহার প্রয়োগ হয়। এই অর্থে ইহা সংস্কৃত “কৃত” শব্দের পরিবর্তন হইতে আসিয়াছে। উদাহরণ : ব্রজবুলি হইতে ‘চাঁদ কি চলনা’, হেমচন্দ্র হইতে, ‘অব বাপ্পকি ডুম্মুড়ি’(= বাবার জমিটুকু)।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি উচ্চারণের যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা এই বাবদ ধন্যবাদ পাইতেছেন। কিন্তু শ্বাসাঘাতের যে যুক্তি তাহারা দ্বিতীয় অবয়বস্বরূপ হাজির করিয়াছেন তাহাও নিতান্ত খোঁড়া যুক্তি। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে প্রেতের বানান বলিয়াছিলেন তাহার পেছনের যুক্তিই নতুন মুখোশ পরিয়া হাজির হইল মাত্র। কিভাবে, দেখাইতেছি। কথায় বলে দুর্বৃত্তের ছলের অভাব নাই।
‘বাঙলা বানানবিধি’পুঁথিযোগে পরেশচন্দ্র মজুমদার যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এই মুখোশের সেলাইরেখা দেখা যাইবে। পরেশচন্দ্র দেখাইতেছেন :
“প্রথমেই মনে রাখা দরকার, সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব/দীর্ঘ ভেদ আছে। বাঙলাতেও আছে। কিন্তু উভয়ের গুণগত পার্থক্য যথেষ্ট। সংস্কৃতে এই গুরু-লঘু ভেদ শব্দের অর্থান্তর ঘটায়, যেমন, দিন : দীন, চির : চীর, কুল : কূল ইত্যাদি। কাজেই সংস্কৃতে হৃস্বদীর্ঘভেদ ধ্বনিমানসূচক (Phonemic)। বাঙলা শব্দের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অবস্থানমূলক অর্থাৎ স্বরের অবস্থান অনুযায়ী এই ভেদ ঘটে; যেমন, ‘তিন, হিম, চিল’ ইত্যাদি শব্দের ই-কার উচ্চারণে দীর্ঘ, কিন্তু রিপু, ভীষণ’ইত্যাদি শব্দে ই-স্বর হ্রস্ব। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ‘প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে স্বর রুদ্ধ (Closed), কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মুক্ত (Open)। কিন্তু লক্ষণীয়, অবস্থান অনুযায়ী বাঙলা স্বরমাত্রার হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ থাকলেও এর বিপর্যয় অর্থান্তর ঘটায় না। কাজই বাংলায় এই ভেদ ধ্বনিমানসূচক (Phonemic) নয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার যথার্থ প্রবণতা হলো হ্রস্ব মাত্রার উচ্চারণ। উচ্চারণে এবং বানানে সমতা আনা উচিত।” (বাঙ্লা বানানবিধি, পৃ. ২৮)
পশ্চিমবঙ্গে “কি” ও “কী” তফাত উপপাদ্যের পাঁচআনি নেতা পবিত্র সরকার। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন : “স্বরচিহ্নের মধ্যে দীর্ঘ ঈকার ও দীর্ঘ ঊকারের উচ্চারণ বাংলায় নেই। অর্থাৎ এই উচ্চারণ ফোনিমিক নয়। এর সহজ অর্থ হল, স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে অর্থ পাল্টাচ্ছে, এমন শব্দের দৃষ্টান্ত বাঙলায় নেই।” (বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃ. ৪৭) এই কারণেই বাংলা বানানের সংস্কারে মনীন্দ্রকুমার ঘোষ যাহাকে বলেন ‘হ্রস্ব-ইকার প্রবণতা’ তাহার জয় হইতেছে। ইহার কৃতিত্ব বহুলাংশে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথা মানিতে হইবে।
পবিত্র সরকারও দেখিয়াছেন সত্য লোকের মধ্যে স্বীকৃতিও পাইতেছে : ‘স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ ফোনিমিক না হওয়ার দরুন আলোচ্য শব্দগুলিকে উচ্চারণ-অনুগ করতে গিয়ে দীর্ঘ ঈকার দীর্ঘ ঊকারের জায়গায় হ্রস্ব ইকার হ্রস্ব উকার লেখা চলছে, এবং এ ধরনের প্রয়োগ ক্রমশ বেশি লোকের কাছে গৃহীত হচ্ছে।’ (বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃ. ৪৭)
এত বাক্য ব্যয় করিবার পরও পায়ে টিকা দিয়া পবিত্র সরকার পুনশ্চ যোগ করিতে ভুলিলেন না, “বাংলা উচ্চারণে ই ও ঈ-র মধ্যে কোনো তফাত নেই।” (বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃ. ১৫১) জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রসিদ্ধ ‘বাংলা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে এই মূলনীতির অবতারণাই করিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও তীব্র ব্যঙ্গে মিশাইয়া কহিয়াছিলেন, “মাকে মা বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই মা বলিতে যাওয়া দোষের হয়। সেইরূপ বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না।” (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ১১২)
পবিত্র সরকার মহাশয়ও রবীন্দ্রনাথের বৃত্তি করিয়া লিখিয়াছেন : “সংসদ বাঙ্গলা অভিধান’-এর সম্পাদক মাঝে মাঝে “বাংলা ঈ” প্রত্যয় জুড়ে শব্দ তৈরি করেছেন, যেমন “অদরকারী”। মনে রাখতে হবে এসব প্রত্যয় তৈরি হয়েছে মুখের ভাষায়, আর মুখের ভাষায় দীর্ঘ ঈ বলে কিছু নেই। সুতরাং ওটা সোজাসুজি ই-প্রত্যয়।” (বাংলা বানান-সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা পৃ. ১৫১)
এতখানি যাঁহার জ্ঞানগরিমা, এতখানি যাঁহার বিচারবুদ্ধি তিনিই পরক্ষণে লিখিতে বসিলেন, ‘তবু “কী” ‘কি’ দুভাবে লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা আমরা সমর্থন করি। ‘কী’ কর্মপদের স্থান নেয়, কিংবা বিশেষণের বিশেষণ (intensifier) হিসাবে কাজ করে। ‘কি’ হ্যাঁ-না প্রশ্নের সূচক। দুটির ভূমিকা ও তাৎপর্য-আলাদা, ধ্বনিগত চরিত্রও আলাদা।’ (পৃ. ১৫১)
এখন আমরা কি করি? কিংকতর্ব্যবিমূঢ় ছাড়া আর কি বা হই!
সারকথা এই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি দুই নম্বর যে অবয়ব দেখাইয়াছেন তাহা আপাদমস্তক স্ববিরোধিতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রলোকের জন্য শিক্ষাপ্রদ হইবে না। পবিত্র সরকার মহোদয়কে বাংলা ভাষা আর কে শিখাইবে? শুদ্ধ ইংরেজি হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিবার ধৃষ্টতা করি।
সরকার মহাশয় যদি রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ ভাল উল্টাইয়া দেখিতেন, খুঁজিয়া পাইতেন ‘কি’শব্দের কর্তৃ (অভিহিত) পদে যে রূপ কর্মপদেও সেই রূপ অপরিবর্তিত থাকে। ইহার রূপ অধিকরণে ‘কিসে’ এবং ‘কিসেতে’, সম্বন্ধপদে ‘কিসের’। রামমোহন রায় বাংলা ভাষায় সম্প্রদান ও অপাদান পরিণাম স্বীকার করেন নাই। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৮)
সুতরাং ‘কর্মপদের স্থান নেয়’এই যুক্তি চলে না। বিশেষণের বিশেষণ হইলেও রূপান্তর হইবার কোন কারণ হয় না। যুক্তি একই। যদি না আপনি ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজশেখর বসুর প্রস্তাবে- অর্থাৎ বেশি জোর দিতে ফিরিয়া না আসেন। সেই যুক্তি তো অচল। তাহা আপনি মানিয়াছেন আর পরেশচন্দ্র মজুমদারও মানিয়াছেন। মানিয়াছেন দুই জনেই।
এক্ষণে ইংরেজিতে আসিতেছি। ইংরেজিতে অনেক ক্রিয়ার সহিত একটি প্রত্যয়ের যোগসাজশ করিয়া বিশেষ্য বা সংজ্ঞা তৈয়ার হয়। যথা- break হইতে breakage। drainage, leakage প্রভৃতিও এইরূপে গড়া হয়।
কতক আছে যাহাতে মূল ক্রিয়া শব্দে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটাইয়া যোগক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যেমন : approval, arrival, refusal। কতকে আবার করিতে হয় না, যেমন : acceptance, appearance, performance, delivery, discovery, recovery, agreement, arrangement, employment, departure, failure। কতকে আবার করিতে হয়, যথা : collision, decision, division, education, organisation, attention, solution, closure ইত্যাদি।
কতক ইংরেজি বিশেষ্য গঠিতে হয় বিশেষণ হইতে, যথা: importance, absence, presence, ability, activity, equality, darkness, happiness, kindness, length, strength, truth ইত্যাদি।
কতক উদাহরণ পাওয়া যায় যাহাতে একই শব্দ উচ্চারণ বা বানান কোনটি না বদলাইয়াই যুগপৎ বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ করা যায়। আবার ক্রিয়ার ভাড়ার হইতেও তাঁহাদের বিয়োগ করা চলে না। উদাহরণের তালিকা দীর্ঘ হইবে, আমি কয়েকটি দিতেছি :
aim, answer, cause, change, doubt, dream, end, fall, guess, hope, influence, interest, joke, laugh, lock, move, note, order, plan, play, quarrel, result, smile, stop, talk, trouble, walk, work ইত্যাদি।
আবার কতক শব্দ আছে যাহাদের প্রয়োগ অনুসারে উচ্চারণ বদলায় কিন্তু বানান আদৌ বদলাইবে না। যখন শব্দটি বিশেষ্য ব্যবহার্য হইবে তখন উহার শেষ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অঘোষ (voiceless) হইবেক। আর ক্রিয়ায় ব্যবহার্য হইলে একই ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সঘোষ (voiced) হইবেক। যথা : abuse শব্দের উচ্চারণ বিশেষ্য অবস্থায় “এবিয়ুস” (abuse/s) আর ক্রিয়া অবস্থায় উচ্চারণ “এবিয়ুজ” (abuse/z)। একই রকম উচ্চারণভেদ হইবে house, excuse, use শব্দে।
কতক শব্দে উচ্চারণভেদে বানানও ভেদ হইয়া থাকে, যেমন advice (বিশেষ্য), advise (ক্রিয়া) ইত্যাদি। কতক শব্দে ইংল্যান্ডের ইংরেজিতে বানানভেদ হইলেও বিশেষ্যে আর ক্রিয়ার উচ্চারণে ভেদ নাই, যেমন practice (বিশেষ্য) practise (ক্রিয়া)। দুই শব্দই শেষ ব্যঞ্জনে অঘোষ থাকে।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি উচ্চারণে বল (stress) প্রয়োগের যুক্তি দেখাইয়াছেন। বাংলায় ‘কি’ ও ‘কী’ উচ্চারণের কোন ভেদ নাই। বলের অভিঘাতের আলাদা করার জায়গা নাই। দুইটার ফলই সোজাসুজি ‘ই’। তাঁহারা লিখিয়াছেন, ‘উচ্চারণে হ্যাঁ-না প্রশ্নের “কি”তে বল (stress) নেই। কিন্তু অন্য “কী”তে আছে। তাতেও এ দুটি পৃথক হয়ে যায়।” (বিধি ১২.২) ধরণী দ্বিধা না হইলেও দুঃখ নাই। কি ও কী দ্বিধা হইবেন।
ইংরেজি ভাষায় বিস্তর শব্দ পাওয়া যায় যাহাদের উচ্চারণকালে শ্বাসাঘাত বা বলের স্থান পরিবর্তন হয় কিন্তু বানানের পরিবর্তন হয় না। যদি বল প্রথম দলে (syllable) প্রযুক্ত হয় তখন শব্দটি বিশেষ্য পদবাচ্য হয়। আর বল দ্বিতীয় ভাগে সরিয়া যায় তো শব্দটি ক্রিয়া হইয়া যায়। উদাহরণ : accent (শ্বাসাঘাত)।
শব্দটি যদি বলি ‘The/accent in this noun falls on the first syllable’ (এই বিশেষ্যটির প্রথম ভাগে শ্বাসাঘাত হইবে) তখন শ্বাসাঘাত পড়িতেছে a অক্ষরের আগে, নির্দেশ করা স্থানে। আর যদি ক্রিয়াবিশ্বাসে বলি ‘We ac/cent this verb on the second syllable’ (এই ক্রিয়াটির দ্বিতীয় ভাগে শ্বাসাঘাত পড়িয়া থাকে) তবে শ্বাসাঘাত পড়িবে দ্বিতীয় c অক্ষরটির আগে, নির্দেশ করা জায়গায়।
এই রকম শব্দের তালিকা নাতিদীর্ঘই হইবে। যেমন : abstract, addict, ally, attribute, combine, compress, concert, conduct, conflict, conscript, contest, contract, contrast, converse, convert, convict, decrease, desert, dictate, digest, discount, discourse, entrance, /envelope (বিশেষ্য), en/velop (ক্রিয়া), escort, essay, exploit, export, extract, import, impress, incense, increase, insult, abject, perfume, permit, present, produce, progress, project, prospect, protest, rebel, record, retail, subject, survey, suspect, torment, transfer, transport ইত্যাদি। (R.A. Close, A Reference Grammar, pp. 107-08)
উচ্চারণের যুক্তিবিচার করিয়া বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি বা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কেহই প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই “কি” শব্দের বানান ক্ষেত্র (বা প্রয়োগ) বিশেষে “কী” কেন লিখিতে হইবে। তাঁহারা জানেন রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছিলেন, ‘আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিশেরও জোর।’ তাই তাঁহারা উপরওয়ালার দ্বারে দ্বারে দস্তক ও পুরস্কার ভিক্ষা করিয়া বল সংগ্রহের পথ ধরিয়াছেন।
বাংলাদেশে সরকারের বিশেষ পুলিশ বাহিনির হেফাজতে বন্দির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিলে মন্ত্রণালয় যে যুক্তি সচরাচর দিয়া থাকেন তাহা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।
তুমি কি জাতি?
‘অনধিকার চর্চায় অব্যবসায়ীর যে বিপদ ঘটে আমারও তাই ঘটিয়াছে।’
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৩২)
‘ভাষার স্বরূপবিচারে একদেশদর্শী সংস্কর্তাদের অভিলাষও যথার্থ দিগ্দর্শনের কাজ করে না। ভাষার সৃষ্টিশীল প্রধান লেখকগণের উৎকৃষ্ট রচনারীতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেই সেই ভাষা-প্রবাহের মৌল প্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে, তার ক্রমবিবর্তনের স্বকীয় ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করতে হবে।’
- মুনীর চৌধুরী, (বাংলা গদ্যরীতি, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩)
এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কি তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়াইবে? গড়াইলে গড়াইবে। কিন্তু বিচার করেন কে? আমরা কমলাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়কে বিচারকর্তা মানিতে প্রস্তুত আছি। কারণ বাংলাদেশের উচ্চ-আদালত বাংলা ভাষার সমজদার নহেন। তাঁহারা এই মামলা শুনিবেন না।
খোসনবীস জুনিয়ার প্রণীত বিবরণীতে দেখা যাইতেছে ওই আফিঙ্গখোর কমলাকান্ত মহাশয় এতদিনে আদালতপাড়ায় হাজির আছেন। তিনি ফরিয়াদি নহেন। চুরিও করেন নাই। দোষের মধ্যে এক আফিঙ্গ। তিনি অন্তত সাক্ষী তো হইবেন।
‘এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার- পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে- সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।
কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল-“হাস কেন?”
কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, “বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?”
চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাঁড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, “তামাসার জায়গা এ নয়- হলফ পড়।”
কমলাকান্ত বলিল, “পড়াও না বাপু।”
একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, “বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ...”।
কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?
মুহুরি। শুনতে পাও না-“পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে!”
কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!
হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “সর্ব্বনাশ কি?”
কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি- এ কথাটা বলতে হবে?”
হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই।
কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম- কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?
হাকিম। এর আর মিথ্যা কি?
কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, “তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?” প্রকাশ্যে বলিল, “ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চশমা নাকে দিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন- কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না- তখন কেমন করিয়া বলি- আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে-”
আমি এক্ষণে কিছু অংশ ছাড়িয়া দিতেছি। উকিল সাহেব চটিলেন বটে তবে হাজার হোক মোয়াক্কেলের স্বার্থ দেখিতে হয়। সাক্ষীকে মনে করাইয়া দিলেন, ‘এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।’অর্থাৎ মিথ্যা বলুন। হাকিমের হস্তক্ষেপে খানিক পর আবার জেরা শুরু হইল।
কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, “বহুৎ খুব।” উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, “তোমার নাম কি?”
কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।
উকীল। তোমার বাপের নাম কি?
কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি?
উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, “হুজুর! এসব Contempt of Court! হুজুর, উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন- বলিলেন, “আপনারই সাক্ষী।” সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, “বল। বলিতে হইবে।”
কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জাতি?”
কমলা। আমি কি একটা জাতি?
উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়।
কমলা। হিন্দু জাতীয়।
উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ?
কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।
উকীল। দূর হোক ছাই। এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে?
কমলা। মারে কে?
হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় কাজ হইবে না। বলিলেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত- তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর?
কমলা। ধর্ম্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা। দেখিতেছেন, আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী- ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?
হাকিম লিখিলেন, “জাতি ব্রাহ্মণ।” তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বয়স কত?”
এজলাসে একটা ক্লক ছিল- তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, “আমার বয়স একান্ন বৎসর, দুই মাস তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট-”
আবার উকিল সাহেবের উষ্মা হইল। আমি খানিক লাফ দিয়া সামনে যাইতেছি। জেরা চলিতেছে।
উকীল। এখন আছ কোথা?
কমলা। কেন এই আদালতে।
উকীল। কাল ছিলে কোথা?
কমলা। একখানা দোকানে।
হাকিম বলিলেন, ‘আর বকাবকিতে কাজ নাই- আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তারপর?’
উকীল। তোমার পেশা কি?
কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে?
উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?
কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি। (বঙ্কিম রচনাবলী, খণ্ড ২, পৃ. ৯০-৯২)
বস্তুত শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে জেরা করা শামলা গায়ের আমলা উকীলের কর্ম্ম নহে। ভাগ্যের মধ্যে বানান সংস্কর্তা আমলারা কি পূর্বে কি পশ্চিমে কমলার মতো সাক্ষীর পাল্লায় এখনও পড়েন নাই। তাই তাঁহারা ধরাকে সরাই ভাবিতেছেন।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই জনকেই উদীয়মান শক্তিরূপে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদের সাক্ষ্য অনুসারে তাঁহারা উভয়েই বঙ্কিমের প্রতিভার অনতিক্রমনীয় প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ৮০ বছর আগের রবীন্দ্র সংবর্ধনা বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, “বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর ফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাঁহার আবির্ভাব একটি যুগদৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথ আজও ক্রমশঃ উর্দ্ধলোকে আরোহণ করিতেছেন।’ আমরা যোগ করিব, আজও এই আরোহণ অব্যাহতই আছে।
সামান্য ‘কি’ শব্দের বানান লইয়া তিনি যে অসামান্য জিদ করিয়াছিলেন, তাহা অবিস্মরণীয়। ভুলিলে চলিবে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাংলা বানানে হ্রস্ব ই-কারের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে কর্ণধারের ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোঃপূত কর্ণধার সুনীতিকুমার করেন নাই। ‘কি’ বানান দীর্ঘ ঈ-কারযোগে লিখিবার জেদাজেদিতে তাঁহার এই কীর্তি খানিক ম্লান হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে কীর্তিনাশা হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কালের যাত্রার ধ্বনি এই জেদ ভুলিতে আমাদের সহায় হইবে।
কোন মহান স্রষ্টার কীর্তি তাহার ছোট কিছু জেদের কাছে কিছুতেই ম্লান হইতে পারে না। ঢাকা ও কলিকাতার দুই বাংলা অনুষ্ঠান যাহা করিতেছেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গৌরব বাড়িতেছে কি?
বাংলা কি শব্দের বানান বদলাইয়া অর্থের তফাত সৃষ্টির চেষ্টা যে চিন্তার উপর দাঁড়াইয়াছে সেই চিন্তা অসার। এই অসারতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। ১৯৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত ও পরে পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী দেখিতেছি আকাদেমির বানানবিধিতে একটি প্রস্তাব ছিল এই উপলব্ধির সাক্ষী: ‘অতৎসম শব্দে হ্রস্ব-ইকার আর দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে বিশেষ্য বিশেষণরূপের স্বাতন্ত্র্য দেখানোর দরকার নেই। অর্থাৎ আমার খুশি/আমি খুশী তৈরি করা/তৈরী বাড়ি এ রকম কোনো প্রভেদ করা নিষ্প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই হ্রস্ব ই-কারের প্রয়োগ চলুক।” [বানানবিধি ৭.২০; মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম, পৃ. ১৭৩-৭৪]
বানানবিধি ৫ম সংস্করণ হইতে ইহা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে ইহাতে ঐ জাতীয় প্রভেদের অনুমোদন করা হইয়াছে বলিয়া ভুল করিবার সম্ভাবনা নাই। কালের অবধি নাই, পৃথিবীও বিপুলা কম নহেন।
ঢাকার বাংলা একাডেমী এই প্রশ্নে কিছু না লিখিলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) গৃহীত বাংলা বানানরীতিতে (১৯৮৮) এই ভুল চিন্তার উৎস কোথায় তাহা আজও দেখা যাইতেছে। বোর্ডের ১০ নং সুপারিশে বলা হইয়াছিল, “অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন, কি (অব্যয়), কী (সর্বনাম); তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ); নিচ (নিু অর্থে) নীচ (হীন অর্থে); কুল (বংশ অর্থে), কূল (তীর অর্থে)।” (আনিসুজ্জামান, পাঠ্যপুস্তকের বানান, পৃ. ১০৬; শফিউল আলম, প্রসঙ্গ: ভাষা বানান শিক্ষা, পৃ. ৭৪)
আনিসুজ্জামান, মাহবুবুল হক প্রভৃতি লেখকের বই পড়িয়া মনে হইতেছে ইঁহারা এখনও সেই অর্থভেদ উপপাদ্যের নিচেই মুখ থুবড়াইয়া আছেন। (আনিসুজ্জামান, পাঠ্যপুস্তকের বানান, পৃ. ৩৩-৩৭; মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম, পৃ. ১৪৩-১৪৪)
এই অসার যুক্তি বা জেদের প্রকোপে রবীন্দ্রনাথও একদা “নীচ” ও “নিচ” শব্দে ভেদ করিতে তাগাদা দিয়াছিলেন। নীতিশাস্ত্রের বিচারে কেহ মন্দ বিবেচিত হইলে দীর্ঘ ঈকারযোগে “নীচ” আর পদার্থশাস্ত্রের অর্থে কেহ নিম্নে পতিত হইলে “নিচ” হইবেন। ইহাই ছিল ঠাকুরের ধারণা। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯০) এই ধারণার সমাধি বহু আগেই হওয়া উচিত ছিল। বাংলা ভাষায় ইকারের প্রবণতা অনুসারে উভয় অর্থেই শব্দটির বানান “নিচ” হইতে পারে। সংস্কৃত বাদিপক্ষের বিচারে হয়তো উভয় অর্থেই শব্দটি “নীচ”ই ছিল। (মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাংলা বানান, পৃ. ৭৬-৭৮) তাহাতে কিছু আসে যায় না। (দিনেন ভট্টাচার্য, বানানের রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৬০-৬১)
এইখানে আমাদের স্থলাভাব হইয়াছে। তাই মাত্র সংক্ষেপে, ইঙ্গিতে লিখিতেছি। যে বানানেই লিখিবেন না কেন, বাংলায় নীতিশাস্ত্র ও পদার্থশাস্ত্র দুই শাস্ত্রেই এক বানানে “নিচ” কথাটা লেখা যাইবে। কারণ “নিচ” শব্দের যথার্থ অর্থ ভূমিতে “নিম্নস্থল” নৈতিক অর্থে “নিম্নমর্যাদা” তাহার ব্যঞ্জনা মাত্র। দুর্ভাগ্যের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ ইহা ধরিতেই পারেন নাই। তাই তাঁহার জেদাজেদি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় কবি সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এক ধরনের বাক্যভ্রংশ বা এফেসিয়া (aphasia) হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহা কুলসঞ্চারিরোগ কিনা জানি না। (‘যে রোগ পিতামাতা হইতে পুত্রপৌত্রে যায়’ তাহাকে আয়ুর্বেদে “সঞ্চারিরোগ” বলে।’ -বিজয়চন্দ্র মজুমদার।) অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্মৃতিভ্রংশ’ রোগটা ধরনে ছিল রোমান এয়াকবসন কথিত সামঞ্জস্য-বৈকল্য (similarity disorder) বা ব্যঞ্জনালোপ ব্যাধির মতন। ঢাকা ও কলিকাতার সরকারি পণ্ডিতদের মাথায় তাহা কুলসঞ্চারি (hereditary) বিমারস্বরূপ বর্তাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। (R. Jakobson, ‘Two Aspects,’ pp. 54-82)
ইহাদের উদ্দেশে আমার আজিকার শেষ আবেদন, ভাবিয়া দেখুন। স্বয়ং কবিরই যেখানে চিকিৎসা দরকার সেখানে আপনারা রোগ নির্ণয়ই করেন নাই। উপরন্তু গোটা বাংলা ভাষাকেই রোগদোষে দুষিত করিতেছেন। কবি যদি কোন বিষয় বুঝিতে না পারিয়াও থাকেন আমাদের কি উচিত হইবে তাঁহার এই অগৌরবের দিকে সারাক্ষণ তাক লাগাইয়া চাহিয়া থাকা? কবিকে সম্মান জানাইবার ইহাই কি শ্রেষ্ঠ পন্থা?
যে মানুষের একটি চোখ নষ্ট হইয়াছে তাহাকে কানা বলে কেন? চোখের ব্যবহার সীমারেখায় পৌঁছিলে কানের ব্যবহার বাড়িয়া যায়। এই লোকসংস্কার সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক এক চোখা লোককে কানা বলাই তাই রীতি। আপনারাও কি কানা হইলেন না? শুদ্ধ কানকথায় কান দিলেন, চোখের দেখা দেখিলেন না?
পণ্ডিত কৃষ্ণপদ গোস্বামীও দুর্ভাগ্যক্রমে মনে করিতেন অর্থভেদের জন্য “কি” ও “কী” আলাদা করা যাইতে পারে। তবে তিনিও খেয়াল করেন নাই শব্দের ব্যঞ্জনা আসে তাহার বানান হইতে নহে। ব্যবহার হইতে। ব্যবহারই ব্যঞ্জনা নহে, কিন্তু ব্যবহারেই ব্যঞ্জনা।
যদি না হইত তবে গোস্বামী নিজেই কি লিখিতেন এই কথাগুলি? ‘বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস’ গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, “অকল্যাণকর বা কুৎসিত অর্থবাচক কোন শব্দকে ভদ্রভাবে প্রকাশ করিবার সময় অনেক সময় সুভাষণ অলঙ্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়। চাউল বা ভাত না থাকিলে স্ত্রীলোকেরা ‘চাল বাড়ন্ত’, ‘ভাত বাড়ন্ত’ ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে। উত্তর ভারতে পাচক ব্রাহ্মণকে বলা হয় মহারাজ, বাংলায় বলা হয় ঠাকুর।” (পৃ. ১০৮)
পাচক শব্দের উৎপত্তি অনুসারে জাতি যৌগিক। পচ্ ধাতুর সহিত অক প্রত্যয় লাগাইয়া বাংলায় পাচক হইয়াছে। কিন্তু ‘পচেগা’মানে হিন্দিতে ‘পরিপাক হইবে’ বুঝাইলেও বাংলায় বুঝাইতেছে ‘পচিয়া যাইবে’। এক ধাতু হইতে বহু শব্দ ও বহু অর্থ হয়। ‘অক’প্রত্যয়ের অর্থ কর্তৃত্ব ধরিলে পাচক মানে পচনের উপর যাহার কর্তৃত্ব আছে বোঝায়। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র। তিনি লিখিয়াছেন, অনেক সময় বুৎপত্তি ভিন্ন হইলেও ধ্বনি বিচারের দিক দিয়া এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় মিলিয়া যাইতেছে দেখা যায়, কোন রূপভেদ হয় না ; ‘কিন্তু ভাষাভেদে অর্থভেদ ঘটে’। (বাংলাভাষা, পৃ. ২৯৪-৯৫)
সংস্কৃতে তীর অর্থ কূল বা পাড়, ফারসিতে তীর অর্থ শর বা বাণ। বানান বদলাইয়া কূল পাইবেন না। বাংলায় দুই তীরই সমান তীরন্দাজ। এক তীর হইতে তীর ছুড়িয়া অন্য তীরে নিতুই যাইতে পারেন।
রবীন্দ্রনাথ প্রাজ্ঞ বয়সে (পৌষ ১৩২৬) একবার স্বীকার করিয়াছিলেন, ‘অনধিকার চর্চায় অব্যসায়ীর যে বিপদ ঘটে আমারও তাই ঘটিয়াছে।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৩২)
যাহার বিপদ ঘটে এবং যিনি সেই বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া বয়ান করেন- দুইজন কি একই ব্যক্তি। যদি তাহারা দুইজনই হইয়া থাকেন, তাহাদের কি কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়? দোহাই ১. আকাদেমি বানান উপসমিতি (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ) সম্পাদিত, আকাদেমি বানান অভিধান, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫)।
২. আনিসুজ্জামান, পাঠ্য বইয়ের বানান, সংশোধিত ও পরিমার্জিত (জিয়াউল হাসান) সংস্করণ, (ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০০৫)।
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ২য় খণ্ড,তীর্থপতি দত্ত সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা : তুলি-কলম, ২০০১)।
৪. কৃষ্ণপদ গোস্বামী, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ২য় (পরিবর্ধিত) সংস্করণ, (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০০১)।
৫. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯২২-২১ মার্চ ১৯৩২, ১ম খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩)।
৬. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ২য় (পরিবর্ধিত) সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯)।
৭. টেকচাঁদ ঠাকুর, আলালের ঘরের দুলাল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ৮ম (পরিষৎ) সংস্করণ (কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪০৫)।
৮. দিনেন ভট্টাচার্য, বানানের রবীন্দ্রনাথ (কলকাতা : ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৪১০)।
৯. নির্মল দাশ, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ (কলকাতা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭)।
১০. নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, বানান বিতর্ক, ৩য় (পরিবর্ধিত, পবিত্র সরকার) সংস্করণ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭)।
১১. নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ২য় (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত) সংস্করণ, (কলকাতা : নব চলন্তিকা, ২০০১)।
১২. পবিত্র সরকার, বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, (কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৭)।
১৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙ্লা বানানবিধি, পরিবর্ধিত সংস্করণ (কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৮)।
১৪. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, বাংলাভাষা, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা : জিজ্ঞাসা এজেন্সিস, ১৯৯৮)।
১৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, ১৪শ মুদ্রণ (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৪০৯)।
১৬. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি, ২য় মুদ্রণ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪)।
১৭. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাংলা বানান, ৪র্থ (দে’জ) সংস্করণ (কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৪০৯)।
১৮. মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম, ৭ম মুদ্রণ (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮)।
১৯. মিতালী ভট্টাচার্য, বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন (কলকাতা : পারুল প্রকাশনী, ২০০৭)।
২০. মুনীর চৌধুরী, বাঙ্লা গদ্যরীতি, ২য় সংস্করণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৮৩)।
২১. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৪০৭)।
২২. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ভাষা ও সাহিত্য, ৩য় (সংশোধিত) সংস্করণ (ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ১৯৪৯)।
২৩. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা ব্যাকরণ, নতুন সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮)।
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলাভাষা পরিচয়, পুনর্মুদ্রণ (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৭৫)।
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা শব্দতত্ত্ব, ৩য় (স্বতন্ত্র) সংস্করণ (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯১)।
২৬. রমাপ্রসাদ চন্দ, ‘কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম’, বসুমতী, ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪৪।
২৭. রামমোহন রায়, ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’, রামমোহন গ্রন্থাবলী, ৭ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ (কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৮০)।
২৮. সলিমুল্লাহ খান, ‘বাংলা বানানের যম ও নিয়ম’, নতুনধারা, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭।
২৯. সুকুমার সেন, বুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩)।
৩০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মনীষী স্মরণে, দ্বিতীয় প্রকাশ (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা এজেন্সিস, ১৩৯৬)।
৩১. শফিউল আলম, প্রসঙ্গ : ভাষা বানান শিক্ষা (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০০২)।
৩২. হরনাথ ঘোষ ও সুকুমার সেন, বাঙ্লা ভাষার ব্যাকরণ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (কলিকাতা : ভিক্টোরিয়া বুক ডিপো, ১৩৫৬)।
৩৩. R.A. Close, A Reference Grammar for Students of English, 15th ed. (Burnt Mill, Harlow: Longman, 1990).
৩৪. G. A. Grierson, Maithili Dialect, Part 1, Grammar, 2nd ed., cited in জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯)।
৩৫. Roman Jakobson, ‘Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances,’ in R. Jakobson and M. Halle, Fundamentals of Language, pp. 54-82 (Leiden: Mouton, 1956). প্রথম প্রকাশ : শিল্পসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা ‘নতুনধারা’, ৮ম সংখ্যা, ১ আষাঢ় ১৪১৭/১৫ জুন ২০১০, সম্পাদক : নাঈমুল ইসলাম খান।
বাংলা বানানে হ্রস্ব ইকার
সলিমুল্লাহ খান
‘আজ ৮০-৯০ বছর পর্যন্ত বাংলা বানানে হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ নিয়ে যত আলোচনা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, এত আর কোনো বানান নিয়ে হয়নি।’
-মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (বাংলা বানান, দে’জ ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৫) আমার ‘বাংলা বানানের যম ও নিয়ম’প্রবন্ধ (নতুনধারা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭) বাহির হইবার পর দাতা হিতৈষী ও পরোপকারী বন্ধুরা বলিয়াছেন, ‘তুমি উষ্ণ হইয়াছ যে? এই বয়সে মানুষের শোণিত তো শীতল হইবার কথা, কথা শীতল হইবার কথা।’ আপনারা আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। জানিবেন রক্তে বসন্তরোগের শিকার আমি একা হই নাই। এই বিষয়ে আমার উত্তমর্ণ আছেন।
“যে পণ্ডিতমূর্খেরা ‘গভর্ণমেন্ট’ বানান প্রচার করতে লজ্জা পাননি তাঁদেরই প্রেতাত্মার দল আজও বাংলা বানানকে শাসন করছেন- এই প্রেতের বিভীষিকা ঘুচবে কবে? কান হলো সজীব বানান, আর কাণ হলো প্রেতের বানান এ কথা মানবেন তো?’
-কে লিখিয়াছিলেন এই সকল কথা? আর কেহ নয়, স্বয়ং মহাত্মা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯৮-৯৯) বাংলা বানানের রাষ্ট্রে ‘বিপ্লব’আনিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার তুলনা তিনি নিজেই। একান্ত কাঁহারও সহিত তাঁহার তুলনা করিতেই হয়- তো আমি শুদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ বিদ্যাসাগরের নাম লইব। ১৮৫৫ ইংরেজি [সংবৎ ১৯১২] সালে বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ছাপা হয়। প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা স্বাক্ষরের উপরে যাহা লেখা গিয়াছিল তাহাতে এসায়ি উনিশ শতকের বিপ্লব চরমে দেখা যায়। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ লিপিকালে এই বিপ্লব সম্পন্ন হয়।
‘বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋকার [রিকার] ও দীর্ঘ ৯ কারের [লিকারের] প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য, ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর, চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এ জন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে’ (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১২৪৯)
অন্যূন কুড়ি বছরের ভিতর বর্ণপরিচয়ের কমসে কম ষাটটি সংস্করণ হইয়াছিল। ষাটি সংস্করণের বিজ্ঞাপনেও সেই ঘটমান বর্তমানের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন: ‘প্রায় সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ, এই দুই বর্ণস্থলে স্বরের অ, স্বরের আ, বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা, সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ, এইরূপ বলে, তদ্রুপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।’ (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১২৫০)
প্রসঙ্গ যখন উঠিলই বলা অবিধেয় হয় না, আমার- মানে এই গরিব লেখকের- জন্ম বর্ণপরিচয়ের একশত কয়েক বছর পর। কিন্তু আমাকে সেই সদুপদেশ কেহ দেন নাই। আমিও স্বরের অ, স্বরের আ-ই বলিয়া থাকিব। সন্দেহ কি? যাহা বাছুরকে দেওয়া হয় নাই তাহা ষাড়ে দিয়া কোন লাভের মুখ দেখা যায় না। তথাপি বিদ্যাসাগরের গৌরব ম্লান হইতেছে না। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হইতেছে। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা লিখিয়াছেন :
‘যে সকল শব্দের অন্ত্য বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত, উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত-কর, খল, ঘট, জল, পথ, রস, বন ইত্যাদি। অকারান্ত- ছোট, বড়, ভাল, ঘৃত, তৃণ, মৃগ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ শব্দ মাত্রেই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে।’(বিদ্যাসাগর রচনাবলী, খ. ২, পৃ. ১২৫০)
মনে পড়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩০৫ ও ১৩০৮ সালে রাজা রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ ধরিয়া তাঁহার সহিত এই হলন্ত ও অকারান্ত উচ্চারণ বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ৫৫, ৯১) দশ বছর পরও তিনি রামমোহনের উল্লেখ করিয়া একই কথা সামান্য ঘুরাইয়া লিখিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরের উল্লেখই করিলেন না। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ১৩৮)
শুদ্ধ কি তাহাই? তাঁহার আয়ু যখন ৭৭ বছরে পড়িয়াছে তখনও রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি ছাড়েন নাই। তখনও তিনি তত্ত্ব করিলেন, বাংলা ভাষায় দুই অক্ষরবিশিষ্ট বিশেষণ পদ প্রায়ই স্বরান্ত হইয়া থাকে। ঠাকুর লিখিলেন, “তার কোনো ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় অতি অল্প।”(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭১)
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কোথাও বিদ্যাসাগরের ঋণ স্বীকার করিলেন না, যদিও একেলা ‘বাংলা শব্দতত্ত্ব’গ্রন্থেই পাঁচ জায়গায় বিদ্যাসাগরের উল্লেখ প্রসঙ্গত পাওয়া যাইবে। ভাবিতেছিলাম, শুদ্ধ স্বদেশে কেন স্বকালেও যোগী মাঝে মাঝে ভিখ্ পাইবেন না।
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপর সংযোজন, বাংলা তকারের ত ও ৎ এই দ্বিবিধ কলেবর। দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড তকার। ‘ঈষৎ, জগৎ, প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময়, খণ্ড তকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে তকারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।’ (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, খ.২, পৃ. ১২৪৯-৫০)
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরোপকারবৃত্তি স্বীকার করুন আর নাই করুন রবীন্দ্রনাথের নিজের সৎকর্মের তালিকাও কিন্তু হ্রস্ব নহে। তাঁহার দেওয়া অনেক। তাঁহার বাংলা সম্পত্তির মধ্যে বানান সংস্কারও পড়িবে। ঠাকুরের খ্যাতি জগৎ জুড়িয়া। কিন্তু আমরা যাঁহারা নিতান্ত গৃহকোণজীবী তাঁহাদের কাছে তিনি আরো। বাংলা ভাষার দশ স্রষ্টার একজন। আর দশ শব্দের কথা ছাড়িয়াও যদি দিই খোদ “বাংলা”শব্দটির বানান তো আর ছাড়িতে পারি না। বানানটি ব্যবহার প্রথম করিয়াছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৫৭)
এই বিষয়ে ঠাকুরের জবাবদিহি শুনিবার মতন: ‘আমার প্রদেশের নাম আমি লিখি বাংলা। হসন্ত ঙ-র চিহ্ন ং। যেমন হসন্ত ত-য়ের চিহ্ন ৎ। “বাঙ্গলা”মুখে বলি নে লিখতেও চাই নে। যুক্তবর্ণ ঙ্গ-এ হসন্ত চিহ্ন নিরর্থক। ঙ-র সঙ্গে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া চলে, কিন্তু দরকার কী, হসন্ত চিহ্ন যুক্ত ঙ-র স্বকীয়রূপ তো বর্ণমালায় আছে- সেই অনুস্বরকে আমি মেনে নিয়ে থাকি।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯৭)
বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়ে? পড়ে বটে। তিনিও তো ‘বাঙ্গালা’-ই লিখিয়াছিলেন। সত্যের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কবিতার ব্যবসায়ী হয়েন নাই। আর রবীন্দ্রনাথ শেষ বিচারে কবিই। কিন্তু তিনি হাল ছাড়িয়া দিবার মত, কবিজনোচিত ধাতুদৌর্বল্যে ভুগিবার মত অস্থিরমতি ছিলেন না। তাই রক্ষা।
এখনও অনেকের মনে দুঃখ। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ ‘বাংলা’বানান তাঁহারা এখনও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা লেখেন “বাঙ্লা”। ঘটনা কি? মণীন্দ্রকুমার ঘোষ পূর্ব বাঙালির দুঃখ খানিক ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। মাত্র ১৯৭৬ সালেও তিনি লিখিয়াছেন :
‘উচ্চারণের খাতিরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি মাত্র শব্দে ‘ঙ্গ’থেকে ‘গ’বিচ্ছিন্ন করে ‘ঙ’কে স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন বটে কিন্তু সেসব শব্দ ছিল তদ্ভব- তৎসম শব্দে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নি। ‘বঙ্গ’শব্দ থেকে ‘বাঙ্গালা’‘বাঙ্গলা’-আমরা দুই বানানেরই সাক্ষাৎ পাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। রবীন্দ্রনাথ ‘বাঙ্গলা’না লিখে প্রথমে লিখলেন ‘বাঙ্লা’, পরে ‘বাংলা’। ‘বাঙ্গালী, কাঙ্গালী, ভাঙ্গা, রাঙ্গা’রবীন্দ্রনাথের হাতে হল ‘বাঙালি, কাঙালি, ভাঙা, রাঙা’। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে ‘গ’লোপ পেয়েছে ঠিকই, তবে পূর্ববঙ্গের কণ্ঠ থেকে কিন্তু অদ্যাপি ‘ঙ্গ’ধ্বনির কোনো বর্ণ স্খলিত হয় নি।” (বাংলা বানান, পৃ. ৩২)
এই তো মাত্র শুরু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন দানকে বাংলাদেশ (ভারতের কথা বলিতে পারিব না) অস্বীকার করিবে? ১৯৩১ সনে রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭০ বছর পূরা হইয়াছিল। তাঁহাকে বাড়াইয়া লইবার জন্য বাংলাদেশের সাধুব্যক্তিরা ৮ মে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়ায় জনসভা ডাকিয়াছিলেন। মূলসভা নহে, পরামর্শ সভা। সভায় সভাপতির পাট লইয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিলেন আমাদের মনের কথাটাই :
‘সাহিত্য-জগতের এমন কোন বিভাগ নাই যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেন নাই, কিন্তু গীতিকাব্য জগতে তিনি যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ত অপরিমেয়। তাঁহার রচনাবলী জীবন্ত তাঁহার বিদ্রুপ তীক্ষ্ণ এবং তাঁহার ব্যঙ্গ তীব্র হইয়াছে। তিনি প্রাচীন কবিদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহার ব্যাকরণ জ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞান আমাদের অধিকাংশকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।’(চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, খণ্ড ১, পৃ. ২৩)
ঠাকুরের জগজ্জোড়া খ্যাতি বাংলা বানান সংস্কার আন্দোলনে তাঁহার সহায়ও হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা হইতেও তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ‘বহু দূরের স্কান্ডিনেভিয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দেশবাসী তাঁহার জন্য কি করিয়াছেন?’- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তর তাঁহার ৮ মে তারিখের বক্তৃতাতেই আছে: ‘আমরা যদি তাঁহার প্রতিভা-প্রসূত দানসমূহকে গ্রহণ ও উপলব্ধি করি, তাহাতেই তাঁহার প্রতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে।’ ব্যাকরণিয়া রবীন্দ্রনাথ ‘প্রাকৃত বাংলায় যা শুচি, সংস্কৃত ভাষায় তাই অশুচি।’
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮২)
বানান সংস্কার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে ‘কর্ণধার’মনে (বৃথা যদিও) করিয়াছিলেন সেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ই তাঁহাকে ‘ব্যাকরণিয়া’উপাধি দিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক পুঁথির মধ্যে এক পুঁথির নাম ‘মনীষী স্মরণে’। সেখানে রামমোহন রায়ের উপাধি হইয়াছে ‘ব্যাকরণকার’আর রবীন্দ্রনাথের হইয়াছে ‘ব্যাকরণিয়া’। ‘বৈয়াকরণ’কথাটি সুনীতিকুমার কাঁহারও ভাগেই বরাদ্দ করেন নাই।
রামমোহন পুরাদস্তুর একখানা ব্যাকরণ বই লিখিয়াছিলেন, যথাক্রমে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ তাহা না করিলেও এই বিষয়ে তাঁহার মোট লেখা কম নহে। বিশেষ, শেষের দিকে লেখা ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’প্রবন্ধের লেখককে তাঁহার ধাঁচায় ‘ব্যাকরণিয়া’বলা অবৈধ হইতেছে না। তিনি যদি কোনদিন এই কথা বলিয়া থাকেন, ‘বাংলাদেশকে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়ে চিরজীবন আমি সেবা করে এসেছি,’ তবে তিনি অনেক কম দাবি করিয়াছেন ধরিতে হইবে।
বাংলা ব্যাকরণে বা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ যাহা দিয়াছেন তাহার সারাংশ লেখাও শক্ত। কতর্ব্যরে দোহাই দিয়া বলিব- সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন অর্থাৎ নিয়মের নিগড় হইতে বাংলা ব্যাকরণের মুক্তি প্রার্থনা তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্তি। জীবনের উপান্তে পৌঁছিয়া ঠাকুর লিখিয়াছেন, ‘এতকাল ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য না নিয়ে যে বহুকোটি বাঙালি প্রতিদিন মাতৃভাষা ব্যবহার করে এসেছে এতকাল পরে আজ তাদের সেই ভাষাই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। এই জন্য তাদের সেই খাঁটি বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮১)
একই জায়গায় তিনি দাবি করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষা না জানিলে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা যাইবে না এমত দাবি অস্বাভাবিক এবং অত্যাচারের শামিল। যত শীঘ্র পারা যায় এই কঠোর বন্ধন, ‘পাণ্ডিত্যাভিমানী বাঙালির’এই নূতন কীর্তি, শিথিল করিয়া দেওয়া উচিত। তাঁহার ভাষায়, ‘বস্তুত একেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮১)
তিনি অনেক দূর গিয়াছেন। সবটুকু যাইতে পারেন নাই বলিয়া তাহার যতটুকু কৃতিত্ব তাহা তো অস্বীকার করা যাইবে না। রাজশেখর বসুকে ১৯৩১ সাল নাগাদ তিনি লিখিয়াছিলেন,
‘ভেবে দেখলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই। যাকে তৎসম শব্দ বলি উচ্চারণের বিকারে তাও অপভ্রংশ পদবীতে পড়ে। সংস্কৃত নিয়মে লিখি সত্য কিন্তু বলি শোত্তো। মন শব্দ যে কেবল বিসর্গ বিসর্জন করেছে তা নয় তার ধ্বনিরূপ বদলে সে হয়েছে মোন্। এই যুক্তি অনুসারে বাংলা বানানকে আগাগোড়া ধ্বনি-অনুসারী করব এমন সাহস আমার নেই- যদি বাংলায় কেমাল পাশার পদ পেতুম তা হলে হয়তো এই কীর্তি করতুম- এবং সেই পুণ্যে ভাবীকালের অগণ্য শিশুদের কৃতজ্ঞতাভাজন হতুম। অন্তত তদ্ভব শব্দে যিনি সাহস দেখিয়ে ষত্বণত্ব ও দীর্ঘহ্রস্বের পণ্ডপাণ্ডিত্য ঘুচিয়ে শব্দের ধ্বনিস্বরূপকে শ্রদ্ধা করতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর আমি জয়জয়কার করব।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯৮)
মনে করিবার কারণ ঘটে নাই, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতের মর্যাদা কমাইয়া দেখিয়াছেন। তিনি রুই মাছের অমর্যাদা করেন নাই, শুদ্ধমাত্র পুঁটি মাছের জন্য দুঃখ পাইয়াছেন। রুই মাছ অগাধ জলে বিহার করে। তাহার বিকার নাই। পুঁটি গণ্ডুষমাত্র জলে ফরফর করিয়া বেড়ায়।
বাংলার উপর সংস্কৃতের চাপ বা প্রভাব বলিয়া একটা কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ জানিয়াছেন এই চাপ প্রাচীনকালের নয়। নিতান্ত আধুনিক যুগের ঘটনা। যে যুগে ভারতবর্ষের নানান এলেকায় নানা প্রকার প্রাকৃত অর্থাৎ মৌখিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল তখন সেই সকল ভাষা লেখার সময় সংস্কৃত ভাষার নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই। মুখের ভাষাকেই লিখিত ভাষার আদর্শ ধরা হইয়াছিল। সর্বসাধারণের মধ্যে নতুন ধর্মের বাণী ছড়াইয়া দিতে হইলে তাহাই ছিল কার্যকর পন্থা। এই কার্যবুদ্ধি ও ন্যায়পরতা সমান হইয়াছিল সেই যুগে।
বর্তমান যুগের আদর্শ কেন তাহা হইবে না? প্রাচীন পণ্ডিতদের তিনি শ্রদ্ধা করিয়াছেন। ঠাকুর লিখিয়াছেন: ‘যাঁরা সমাধান করেছিলেন তাঁরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁরা বোঝার মতো চাপিয়ে যান নি জনসাধারণের ’পরে। যে অসংখ্য পাঠক ও লেখক পণ্ডিত নয় তাদের পথ তাঁরা অকৃত্রিম সত্যপন্থায় সরল করেই দিয়েছিলেন।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮১)
এ কালের পণ্ডিতরা, কবির নালিশ, সেই ধর্ম ভুলিয়াছেন। ‘তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯৩) রবীন্দ্রনাথ বাংলা বানান সংস্কারে বাদী হইয়াছিলেন এই দুঃখেই। তিনি জানিতেন, ‘বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুলপরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্ভাবিত বলিয়া বাংলা বানান, এমন-কি, বাংলা পদাবিন্যাস প্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৬) কামনা করিয়াছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ইহাতে হাত দিন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান সংস্কার সমিতির বিধানকর্তা হইবার মতো জোর আছে। রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধমাত্র যুক্তির জোরে নহে, সেই জোরের জোরেও আস্থা রাখিতেন।
সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় চিত্তের যে আভিজাত্য, যে তপস্যা আছে তাকে বাংলা ভাষায় পুরাপুরি গ্রহণ করিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ। যদি না করি তবে আশঙ্কা, ‘আমাদের সাহিত্য ক্ষীণপ্রয়ণ ও ঐশ্বর্যভ্রষ্ট’ হইবে। শুদ্ধ ভাবের দিক হইতেই নহে, ‘শব্দের দিক’ হইতেও ‘বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কাছে নিরন্তর আনুকূল্যের অপেক্ষা না করে’ থাকিতে পারে না। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৪২)
রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধমাত্র বাংলার স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা পাইবে এই প্রার্থনা করিয়াছেন। ১৩৩৮ সালে সংস্কৃত কলেজ কবিকে ‘কবি সার্বভৌম’উপাধি দেন। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষাতত্ত্ব নতুন করিয়া বয়ান করিলেন। বলিলেন, ‘একদিন ছিল ভারতবর্ষে ভাষা-বোধের একটা প্রতিভা। ভারতবর্ষ পানিনির জন্মভূমি।’ তিনি আরো বলিলেন :
‘তখনকার দিনে প্রাকৃতকে যাঁরা বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন পরম পণ্ডিত। অথচ প্রাকৃতের প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা ছিল না। সংস্কৃত ব্যাকরণের চাপে তাঁরা প্রাকৃতকে লুপ্ত-প্রায় করেন নি। তার কারণ ভাষা সম্বন্ধে তাঁদের ছিল সহজ বোধশক্তি। আমরা আজকাল সংস্কৃত শিখে ভুলে যাই যে বাংলার একটি স্বকীয়তা আছে। অবশ্য সংস্কৃত থেকেই সে শব্দ-সম্পদ পাবে, কিন্তু তার নিজের দৈহিক প্রকৃতি সংস্কৃত দ্বারা আচ্ছন্ন করবার চেষ্টা অসংগত। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কখনো সে চেষ্টা করেন নি।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৪১)
রবীন্দ্রনাথকে কেহ কেহ বসন্তরোগে পাইয়াছে কিনা সন্দেহ করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি শীতলা মায়ের পূজা বিশেষ দিয়াছিলেন বলিয়া জানি না। তিনি কোন কোন ‘আধুনিক’পণ্ডিতকে ‘পণ্ডিতমূর্খ’কেন বলিয়াছিলেন, এখন বোঝা যাইতেছে। কারণ তাঁহারাই তো গভর্ণমেন্ট, কাণ, বানান প্রভৃতি বানান লিখিতেন। কবির উষ্মার কারণ এই সংস্কৃতের চাপে বাংলাকে লুপ্তপ্রায় করনেওয়ালারা অর্বাচীন। তাহাদের দোষ পশ্চিমের দোষ মাত্র।
‘যারা মনে করেছেন বাইরে থেকে বাংলাকে সংস্কৃতের অনুগামী করে শুদ্ধিদান করবেন, তাঁরা সেই দোষ করেছেন যা ভারতে ছিল না। এ দোষ পশ্চিমের। ইংরেজিতে শব্দ ধ্বনির অনুযায়ী নয়। ল্যাটিন ও গ্রীক থেকে উদ্ভূত শব্দে বানানের সঙ্গে ধ্বনির বিরোধ হলেও তাঁরা মূল বানান রক্ষা করেন।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৪১)
কেহ কেহ বলিতে কসুর করেন নাই, রবীন্দ্রনাথের ‘অনুগত’ পণ্ডিতগণ সমভিব্যবহারে বানান সংস্কার সমিতি গঠিয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেই কমিটি বিচারের উপরে উঠে নাই-একথা সত্য। পুরাতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দ কহিয়াছিলেন, ‘বাঙ্গালা ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান।’ (‘কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম,’ মাসিক বসুমতী ১৩৪৪) তদুপরি, কমিটির অন্যতম সভ্য বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের কথানুসারে, ‘সে সময়ে বাংলাদেশে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মন কষাকষির ভাব চলিতেছিল।’শুদ্ধ তাহাই নহে, ‘অনেক মুসলমান লেখক বাংলা ভাষায় নূতন নূতন আরবী ফারসী শব্দ এবং অপূর্ব-প্রচলিত বাগভঙ্গী আমদানী করিয়া বাংলা ভাষার ‘সংস্কার’-এ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।’ আর রবীন্দ্রনাথ ‘ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন’। (বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি, মুদ্রণ ২, পৃ. ৩৭-৩৮)
কি শোচনীয় এই দেশ! যে দেশের শতে পঞ্চাশের বেশি লোক সেই বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেই মুসলমান হইয়া গিয়াছে, যে দেশের বাদবাকির শতকরা ৮০ জনই তপশিলি হিন্দু তাঁহাদের একজন প্রতিনিধিও বাংলা বানান সংস্কার কমিটিতে দেখা যায় নাই। ইহা কেমন ন্যায়বিচার? কেমন কাণ্ডজ্ঞান? কোন কোন লোকের ধারণা বানান কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান এবং প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও ছিলেন। (নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, পৃ. ৩৪)
প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার ধারণা মার্ক টোয়েনের মৃত্যু সংবাদের মতো সামান্য অতিরঞ্জিত হইয়াছে। এই যা। রসিকতার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছিলেন, ‘নব্য বানান-বিধাতাদের মধ্যে তিন জন বড় বড় ভট্টাচার্যবংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৬)
সমিতির সাধারণ সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকেও যদি হিসাবে লওয়া অবৈধ না হয় তবে আমি তো ভট্টাচার্য পাইতেছি চারিজন- বাকি তিনের মধ্যে বিধুশেখর, দুর্গামোহন ও বিজনবিহারী রহিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি, পৃ. ২১-২২)
এই বানান সমিতিও কবির কথা ষোলো আনা রাখেন নাই। কান, সোনা, কোরান, গভর্নর প্রভৃতি শব্দও যাহাতে কবির ইচ্ছানুযায়ী বামুন, গিন্নী, শোনা, করেন, করুন প্রভৃতির মতন দন্ত্য ন দিয়া লেখা হয় তাঁহার আদেশ হইল। দুঃখের মধ্যে, প্রতিবিধানও একই সঙ্গে রহিল। ‘ “রাণী”বানান অনেকেই রাখিতে চান, এ জন্য এই শব্দে বিকল্প বিহিত হইয়াছে’-সমিতি বলিলেন তাহাই সই। (নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, বানান বিতর্ক, পৃ. ৩১৪)
বিধানকর্তারা নিতান্ত অবিবেচক নহেন। সবার উপরে রবীন্দ্রনাথও বুঝিলেন, ‘তাঁহাদের মনেও ভয় ডর আছে, প্রমাণ পাওয়া যায়।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৫) প্রমাণ- সমিতি লিখিয়াছেন-‘বিকল্প বাঞ্ছনীয় নয়, তথাপি যেখানে দুই প্রকার বানানের পক্ষেই প্রবল অভিমত পাওয়া গিয়াছে সেখানে বিকল্পের বিধান করিতে হইয়াছে।’(বানান বিতর্ক, পৃ. ৩১৩)
একপ্রস্ত উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝান যাইতে পারে। ‘বাংলা বানানের নিয়ম’দ্বিতীয় সংস্করণে (সেপ্টেম্বর ১৯৩৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার সমিতি বিধান দিয়াছিলেন, ঢাকি, ঢুলি, বাঙ্গালি, ইংরেজি, হিন্দি, রেশমি, পশমি, মাটি, ওকালতি, একটি, দুটি প্রভৃতি তদ্ভব, স্ত্রীলিঙ্গ ও অন্য শব্দে কেবল হ্রস্ব-ই বা হ্রস্ব-উ হইবে। (বিধি ৭)
তৃতীয় সংস্করণে পুনরাদেশ হইল: ‘স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা-“কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী”। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা: “ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চল্তি”। “পিসী, মাসী”স্থানে বিকল্পে ‘‘পিসি, মাসি’’ লেখা চলিবে।’ (বিধি ৫)
তৃতীয় সংস্করণের পায়ে পায়ে প্রকাশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, ‘সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন’এ দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়।’ (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৮৬)
‘গৃহবিচ্ছেদের আশংকা’আছে বলে রবীন্দ্রনাথও সমিতির অনেক সিদ্ধান্ত কষ্টে মানিয়া লইয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালের ২ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে ‘বিশ্বভারতীয় কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রচিত বাঙ্গালা শব্দের নূতন বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি এবং বাঙ্গালা পরিভাষা গ্রহণ করিয়াছেন।’ (রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, খ. ২, পৃ. ১৫৫)
মণীন্দ্রকুমার দারুণ বলিয়াছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল হ্রস্ব-ইকারের দিকে, সুনীতিকুমারের আসক্তি দীর্ঘ-ঈকারের প্রতি।’রবীন্দ্রনাথ ‘জরাজনিত মনোযোগের দুর্বলতা’ হেতু ‘দায়ী’কে ‘দায়ি’ লিখিতেন আর সুনীতিকুমার ‘খেয়াল ছিল না’ বলিয়া রিপোর্টকে ‘রীপোর্ট’লিখিতেন। মণীন্দ্রকুমার লিখিতেছেন, ‘অর্থাৎ খেয়াল না থাকলে রবীন্দ্রনাথের কলমে আসে হ্রস্ব ই-কার, সুনীতিকুমারের আসে দীর্ঘ-ঈকার।’ (বাংলা বানান, পৃ. ৩৫-৩৬) কথাপ্রসঙ্গে সুনীতিকুমার নাকি একদিন বলেওছিলেন ‘দীর্ঘ-ঈকার (ী) লেখা সোজা।’ মণীন্দ্রকুমারের মন্তব্যও তাঁহার অনুকূলই: ‘বাস্তবিকই বাংলা বর্ণবিন্যাসে স্বরচিহ্নের মধ্যে হ্রস্ব-ইকার (ি) লেখাই সর্বাধিক কষ্টদায়ক।’(বাংলা বানান, পৃ. ৩৬)
রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ‘ভাষাচার্য’ উপাধি দান করিয়া যে পুঁথিটি তাঁহার করকমলে তুলিয়া দিলেন, তাহাতেই দেখি লেখা আছে,
‘খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যাভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ই-কারকে মানব। ‘ইংরেজি’ বা ‘মুসলমানি’ শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই- অসংকোচে হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্-ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্ দিন কোনো পণ্ডিতাভিমানী লেখক ‘মুসলমানিনী’কায়দা বা ‘ইংরেজিনী’রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশংকা থেকে যায়।’(বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৮৬-৭; নিুরেখা যোগ করা হইয়াছে, বানান রবীন্দ্রনাথের)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তো রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য প্রকাশের এক যুগ আগেই তাঁহার সমর্থনসূচক কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার বিচারে তদ্ভব ও দেশজ বাংলা শব্দে সবখানেই হ্রস্ব ই এবং হ্রস্ব উ হওয়াই নিয়ম। দীর্ঘস্বরের জন্য বাংলা ভাষায় আলাদা হরফেরই দরকার নাই। দীর্ঘস্বর বুঝাইবার জন্য আদৌ কোন চিহ্নও দরকার হইবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে শহীদুল্লাহ বাংলা ১৩৩১ সালে জানাইয়াছিলেন,
‘যেমন সংস্কৃত ইত্যাদির রোমান অক্ষরে অনুলেখনে (Transliteration) স্বরবর্ণের উপর দীর্ঘ চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালায় তাহার কোন দরকার নাই। বাঙ্গালা উচ্চারণের নিয়মেই হ্রস্ব দীর্ঘ ধরা পড়ে- যেমন হসন্ত বর্ণের আগের স্বর দীর্ঘ হয়। বাস্তবিক সেখানে আমরা সংস্কৃতের অনুকরণে হ্রস্বদীর্ঘ লিখি, বাঙ্গালা উচ্চারণ অনেক জায়গায় তাহার বিপরীত, যেমন “সীতা” এবং “মিতা”। এখানে “সী” ও “মি” উভয়েরই উচ্চারণ হ্রস্ব। “মীন” “দিন” এখানে “মী” ও “দি” উভয়েরই উচ্চারণ দীর্ঘ। কাজেই “শিতা” “মিন” লিখিলে বাঙ্গালা উচ্চারণ দস্তুরমত বুঝা যাইবে।’ (ভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৮৬)
মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁহার ‘ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’ নামক প্রসিদ্ধ পুঁথিযোগে আরো অধিক গিয়াছেন। তাঁহার মতে দেশজ, বিদেশি, সংস্কৃত ও সংস্কৃতভব সকল বাংলা শব্দেই হ্রস্ব ই আর হ্রস্ব উ ব্যবহার করাই সংগত। যথা: গাভি, বুদ্ধিজিবি, নিড়, অনুসারি, অনুরূপ, ইত্যাদি। কেবল বিদেশি শব্দ বাংলা অক্ষরে লিপিকালে ইহার অন্যথা হইতে পারে। (পৃ. ৬৪৬; পরেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙলা বানানবিধি, পৃ. ২৮)
বাংলা শব্দের, স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয় একদা “ন্” ছিল, যেমন: নাতিন, মিতিন, ঠাকুরন ইত্যাদি, পরেশচন্দ্র মজুমদার এ কথা মানেন। কিন্তু তাঁহার মতে, ‘সংস্কৃত প্রভাবেই তা ক্রমে ক্রমে –নী (অর্থাৎ ন+ঈ) প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে।’ (বাঙলা বানানবিধি, পৃ. ২৩) এই যুক্তিতে তিনি বাদী হইলেন, বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে দীর্ঘ ঈকারযুক্ত প্রত্যয় রাখিতে হইবে। তাঁহার ধারণা সংস্কৃতের চাপ এখনও আছে। যেখানে তৎসম শব্দের বেলায় যথারীতি ঈ/নী প্রত্যয় থাকিতেছে সেখানে বাংলা শব্দের বেলায় ই/নি চালু করা হইলে ‘দ্বৈধ প্রবণতার সংগ্রাম’ সূচিত হইবে।
ইহার বাহিরেও কথা আছে। ওড়িয়া, ভোজপুরি, অহমিয়া, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় তদ্ভব শব্দের বানানে এখনও সংস্কার করা হয় নাই। সেখানে এখনও ঈ/নী চলিতেছে। তাই বাংলায় বিচ্ছিন্ন সংস্কার করা উচিত হইবে কিনা তিনি নিশ্চিত হইতে পারিতেছেন না। (বাঙলা বানানবিধি, পৃ. ২৩) দুই বানানের আবদার ‘পণ্ডিত বলেন, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে তুমি ঈ ছাড়িয়া হ্রস্ব ই ধরিলে যে? আমি বলিব ছাড়িলাম আর কই। একতলাতেই যাহার বাস তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, নীচে নামিলে যে, সে বলিবে, নামিলাম আর কই- নীচেই তো আছি। ঘোটকীর দীর্ঘ-ঈতে দাবি আছে; সে ব্যাকরণের প্রাচীন সনন্দ দেখাইতে পারে- কিন্তু ঘুড়ির তাহা নাই। প্রাচীন ভাষা তাহাকে এই অধিকার দেয় নাই। কারণ, তখন তাহার জন্ম হয় নাই। তাহার পরে জন্মাবধি সে তাহার ইকারের পৈতৃক দীর্ঘতা খোয়াইয়া বসিয়াছে।
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ১১২)
পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি পণ্ডিতের আপত্তি যেন রবীন্দ্রনাথ আগে হইতেই আন্দাজ করিয়া থাকিবেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, ‘একটা বিষয়ে বাংলাকে বাহাদুরি দিতে হবে। য়ুরোপীয় অনেক ভাষায়, তা ছাড়া হিন্দি হিন্দুস্থানি গুজরাটি মারাঠিতে, কাল্পনিক খেয়ালে বা স্বরবর্ণের বিশেষত্ব নিয়ে লিঙ্গভেদপ্রথা চলেছে। ভাষার এই অসংগত ব্যবহার বিদেশীদের পক্ষে বিষম সংকটের। বাংলা এ সম্বন্ধে বাস্তবকে মানে। বাংলায় কোনোদিন ঘুড়ি উড্ডীয়মানা হবে না, কিংবা বিজ্ঞাপনে নির্মলা চিনির পাকে সুমধুরা রসগোল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে না। কিংবা শুশ্রূষার কাজে দারুণা মাথাধরায় বরফশীতল জলপটির প্রয়োগ সম্ভাবনা নেই।’ (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৮৬)
তাহা ছাড়াও ‘খাপছাড়াভাবে সংস্কৃতের নী ও ঈ প্রত্যয়ের যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাবার রীতি বাংলায় আছে, কিন্তু তাকে নিয়ম বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণেও মেনে চলবার অভ্যেস তার নেই। সংস্কৃতে ব্যাঘ্রের স্ত্রী ‘ব্যাঘ্রী’, বাংলায় সে ‘বাঘিনী’। সংস্কৃতে ‘সিংহী’ই স্ত্রীজাতীয় সিংহ, বাংলায় সে ‘সিংহিনী’।’(বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৮৪)
শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথেরই জয় হইল। ১৯৮০ সালের দশক হইতে বাংলাদেশে এবং ভারতে বাংলা ভাষার বানান, লিপি ও লেখনরীতির সংস্কার আন্দোলন শুরু হইবার পর ভাষায় হ্রস্ব ইকারের অধিকার বেশি করিয়া স্বীকার করা হইতেছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমি যে সকল সংস্কার প্রস্তাব পাস করাইতে সমর্থ হইয়াছেন সেইগুলিতে হ্রস্ব ইকার প্রবণতারই জয় হইয়াছে। সাধারণভাবে এই সত্যে সন্দেহ করিবার কোন স্থান নাই। তবে ইহাও মিথ্যা নহে যে সংস্কৃতের চাপ কোথাও কোথাও এখনও রহিয়া গিয়াছে।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ব্যাপক সমতার জন্য সিদ্ধান্ত লইয়াছেন স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানোর ক্ষেত্রে হ্রস্ব ইকার/নিকারের ব্যবহার হইবে। (বানানবিধি, স. ৫, বিধি ১১.৪)
‘তাই লেখা হবে কাকি(-মা) কামারনি খান্ডারনি খুকি খুড়ি খেঁদি গয়লানি’ চাকরানি চাচি ছুঁড়ি ছুকরি জেঠি (-মা) ঝি ঠাকুরানি দিদি (-মা) নেকি পাগলি পিসি (-মা) পেঁচি বাঘিনি বামনি বেটি ভেড়ি মামি (-মা) মাসি (-মা) মুদিনি মেথরানি রানি সাপিনি সোহাগিনি স্যাঙাতনি ইত্যাদি।’
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির তুলনায় বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি খানিক পিছনে আছেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদের ‘প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ‘তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার দেওয়া যেতে পারে। যেমন : রানী, পরী, গাভী।’ (নিয়ম ২.০১) ভারতের বাংলা আকাদেমিও কম যাইবেন কেন? তাঁহারাও ব্যতিক্রম অনুমোদন করিয়াছেন। বিধান হইল :
‘সংস্কৃত-ঈয় প্রত্যয় যদি বিশেষণার্থে বিদেশি শব্দ বা অ-তৎসম শব্দ বা শব্দাংশের সঙ্গে যুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার বজায় রাখতে হবে। যেমন : অস্ট্রেলীয় আর্টেজীয় আলজেরীয় ইউরোপীয় ইতালীয় এশীয় কানাডীয় ক্যারিবীয় ক্যালাডোনীয় জর্জীয় পোলিনেশীয় লাইবিরীয় সাইবেরীয় ইত্যাদি।’ (বিধি ১১.৮)
কোন যুক্তিতে এই ব্যতিক্রম? যুক্তি আর যাহাই হোক বিশেষ্য-বিশেষণ উচ্চারণ ভেদের যুক্তি হইতে পারে না। বাংলা ও সংস্কৃতের ভেদই শুরু হইয়াছে উচ্চারণ ভেদ হইতেই। রবীন্দ্রনাথ সে সত্যে সম্পূর্ণ সজাগ : ‘বাংলা ভাষা শব্দ সংগ্রহ করে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু ধ্বনিটা তার স্বকীয়। ধ্বনিবিকারেই অপভ্রংশের উৎপত্তি।’
এই সত্যটাই চাপা দেওয়ার সুবিধা জোগায় বাংলা শব্দের বানান। রবীন্দ্রনাথের মতে এই বানান ব্যবসায়ের জোরেই বাংলা আপন অপভ্রংশত্ব চাপা দিতে চাহে। ‘এই কারণে বাংলা ভাষার অধিকাংশ বানানই নিজের ধ্বনিবিদ্রোহী ভুল বানান।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৬৪)
একই কথাটা উল্টা দিক হইতে দেখিলে কি দাঁড়ায়? পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ‘ধ্বনিবিদ্রোহী ভুল বানান’কেও ‘মান্যতা’ দিতে আগ্রহী। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ‘বাংলা ব্যাকরণসম্মত প্রত্যয়-ব্যবহারে, সমাস-ব্যবহারে বা সন্ধি-সূত্রানুসারে কোনো কোনো বানান বাংলায় দীর্ঘকাল যাবৎ ঈষৎ স্বতন্ত্রতা লাভ করেছে। সেগুলিকেও তৎসম শব্দানুরূপ মান্যতা দেওয়া যেতে পারে।’(বিধি ৩.২, নিুরেখা আমরা দিয়াছি)
রবীন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ‘যদি প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম। প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণের কেমাল পাশা হবার দুরাশা আমার নেই কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ। উক্ত পাশা এ দেশেও দেহান্তর গ্রহণ করতে পারেন।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৫)
বলি, ঠাকুরের আত্মা শান্তিতে থাকিবেন। আপনার পাশা এখনও এই দেশে দেহান্তর গ্রহণ করেন নাই। বোধ হয় তিনি বিশ্রামে আছেন। তবিয়তে বহাল আছেন অসত্য বানান। মান্যতা পাইয়াছেন নতুন করিয়া। কোন কোন বাংলা বানানকে তৎসম শব্দস্বরূপ মান্যতা দিবার দৃষ্টান্ত: অধিকারী অধিবাসী অভিমুখী আততায়ী একাকী কৃতী গুণী জ্ঞানী তন্ত্রী দ্বেষী ধনী পক্ষী মন্ত্রী রোগী শশী সহযোগী ইত্যাদি।
আবার এগুলি বাংলায় আসিলেও সংস্কৃতের পোঁ ছাড়ে নাই। তাই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মেই পরিবর্তিত হইবে। যথা: গুণিজন, পক্ষিকুল মন্ত্রিসভা শশিভূষণ বা একাকিত্ব সহযোগিতা প্রভৃতি। সঙ্গে সঙ্গে আবার ব্যতিক্রমও স্বীকার করা কর্তব্য হইয়াছে। তাই পাইবেন দীর্ঘ ঈকারওয়ালা শব্দভাণ্ডার। যেমন : আগামীকাল আততায়ীদ্বয় ধনীসমাজ পরবর্তীকাল প্রাণীবিদ্যা যন্ত্রীদল হস্তীদল ইত্যাদি। (বিধি ৪.২)
এই রকম আরও চিত্তরঞ্জিনী বিধির প্রদর্শনী আছে। বাংলা বানানে আমোদ নামে নতুন প্রবন্ধ কেহ লিখিলে মন্দ হইবে না। এই প্রসঙ্গে জানাইয়া রাখি একালের সংস্কারবাদী কর্তারাও রবীন্দ্রনাথের সেই দেহান্তর লওয়া কেমাল পাশা মোটেই নহেন। তাঁহাদিগকে বড় জোর খলিফা আবদুল হামিদ উপাধি দেওয়া যাইতে পারে।
মজার কথা এই- ঢাকা ও কলিকাতার সংস্কর্তারা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ বা প্রেরণা অমান্য করিয়াই এখনও সংস্কৃত ব্যাকরণের দাসত্ব করিতেছেন। শুদ্ধমাত্র বাংলায় চলিত ‘সংস্কৃতসম’শব্দেই নহে, এই দাসত্বের শিকলি তাহারা ‘সংস্কৃতভব’শব্দেও ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে লাগাইয়া রাখিয়াছেন।
আবার এই সংস্কর্তারাই কারণে অকারণে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যত্রতত্র দীর্ঘ-ঈকার বসাইয়া ‘কী’লিখিয়া উল্লাস করিবার সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই নজির হাজির করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া দেবপ্রসাদ ঘোষ ১৯৩৭ সনে একবার বলিয়াছিলেন, ‘আপনি অদ্বিতীয় সাহিত্য-স্রষ্টা, কিয়ৎ পরিমাণে ভাষাস্রষ্টাও বটেন, কিন্তু বিশ্লেষণ বিষয়ে আপনার যেন কিঞ্চিৎ অপাটব লক্ষ্য করিতেছি। বোধ করি সৃষ্টি এবং বিশ্লেষণে বিভিন্ন প্রকার প্রতিভার আবশ্যক হয়।’ (বানান বিতর্ক, স. ৩, পৃ. ১৪৬)
আমাদের আশংকা দেবপ্রসাদের এই নির্দেশ হয়তো বা অমূলক নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার একাধিক পত্রিকা ব্যবহারে ও ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’প্রবন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করিয়া দীর্ঘ-ঈকারযোগে ‘কী’লিখিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেই তো স্থানে স্থানে, অজ্ঞানে খণ্ডন করিয়াছেন। আমাদের তাহা খণ্ডন করিবার প্রয়োজন হইতেছে না।
রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলিয়াছেন, ‘কি শব্দের সর্বনাম প্রয়োগ ও অব্যয় প্রয়োগে বানানভেদ করিলে অর্থাৎ একটাতে হ্রস্ব ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ ঈ দিলে উভয়ের ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝাবার সুবিধা হয়।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯০)
আরেক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, ‘তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমন-কি প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দূর হয় না।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮৪)
ঠাকুরের এই ধারণাটাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি ১৯৩৬ সনে (২য় সংস্করণে) গ্রহণ করিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন, “অব্যয় হইলে ‘কি’, সর্বনাম হইলে বিকল্পে ‘কী’বা ‘কি’হইবে, যথা : ‘তুমি কি যাইবে? তুমি কী (কি) খাইবে বল’। (নিয়ম ৭) অর্থাৎ সর্বত্র ‘কি’লিখিলেও অন্যায় হইবে না।
ব্যাখ্যাচ্ছলে জানানো হইয়াছিল, ‘অর্থপ্রকাশের সুবিধার নিমিত্ত ‘কি’ও ‘কী’র ভেদ বিকল্পে বিহিত হইল। অন্যত্র ঈ ই প্রয়োগের হেতু দেখা যায় না, কেবল ই উ লিখিলে বানান সরল হইবে।’(নিয়ম ৭) ইহা কি প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথের আবদার যুগপৎ প্রত্যাখ্যান ও অনুমোদন দুইটাই ছিল না? ইহাতেই তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আগে তিনি পালন করিয়া চলিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। তাই না? আমরা ইহার অর্থ করিতে পারি কেহ ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজনে ‘কী’লিখিতে পারিবেন, তবে অন্যদের লিখিতে বাধ্য করা যাইবে না। এতদিনে আমাদের বাধ্য করা হইতেছে, ইচ্ছা এখন অধিকারকে হটাইয়াছে।
ইতিহাসের অনুরোধে স্মরণ করিতেছি এই দীর্ঘ ঈকারযুক্ত কী বানানের দাবি প্রথম তুলিয়াছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁহাদের ‘চ’ল্তি ভাষার বানান’ নামক প্রবন্ধে জানানো হইয়াছিল
‘সাধুভাষা ও চল্তি ভাষা দুয়েতেই প্রশ্নসূচক অব্যয় কি [হ্রস্ব] ই-কার দিয়ে লেখা হবে। নির্দেশক সর্ব্বনাম “কী” [দীর্ঘ] ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: তুমি কি খাবে? [অব্যয়], তুমি কী খাবে? [সর্ব্বনাম], তুমি কী কী খাবে [সর্ব্বনাম]।’সঙ্গে আরো জানান হইয়াছিল, ‘পুরানো বাঙলা পুঁথীতে “কী”বানান অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।’ (বানান বিতর্ক’, পৃ. ৩০৯-৩১০)
বানানের তফাত না থাকিলে ভাবের তফাত নিশ্চিত করা যাইবে না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ‘কি’বানান হইতে ‘কী’বানান আলাদা করিতে চাহেন। ‘তুমি কি জানো?’ এই প্রশ্নে দুই দুইটা ভাব প্রকাশ হইতে পারে। একটা ভাবে প্রশ্ন করা হয় শ্রোতা জানেন কি জানেন না। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম রাখিয়াছেন ‘জানা সম্বন্ধে’প্রশ্ন। দ্বিতীয় ভাবে একটা সন্দেহ করা হয় মাত্র। সন্দেহের বিষয় শ্রোতা জানেন কি জানেন না এই বিকল্প নহে। বিষয় তিনি কতখানি জানেন তাহাতেই সীমিত। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম রাখিলেন ‘জানার প্রকৃতি বা পরিমাণ সম্বন্ধে’প্রশ্ন। ভাবের এই তফাত নিশ্চিতরূপে আন্দাজ করিতে হইলে বানানের তফাত করিতে হয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব। দেবপ্রসাদ ঘোষের কাছে লেখা দ্বিতীয় পত্রিকায় ঠাকুরের প্রতিপাদ্য ইহাই। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮৪-৮৫)
ছয় বছর আগের- জীবনময় রায়কে লিখিত-চিঠিতে পরিমার্জিত রূপও বাংলা শব্দতত্ত্ব বইয়ে পাওয়া যায়। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ব্যাকরণের ‘পদ’অর্থেও জাতি শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন। বলিয়াছেন ‘কি’শব্দ অব্যয় হইলে এক জাতি, সর্বনাম হইলে অন্য জাতি। জাতির মতন অর্থেরও ভেদ হয়। এই ভিন্ন জাতিধর্ম আর ভিন্ন অর্থধর্ম বুঝবার সুবিধা হয় বলিয়াই তিনি বানানের তফাত দরকার বোধ করেন। তাঁহার আশঙ্কা, ‘এক বানানে দুই প্রয়োজন সারতে গেলে বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের বিঘ্ন ঘটানো হবে।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯০)
এক্ষণে কবির উদাহরণ ‘কি রাঁধছ?’ অথবা “কী রাঁধিছ?”- এই প্রশ্নেও দুই অর্থ প্রকাশ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “বলা বাহুল্য এ দুটো বাক্যের ব্যঞ্জনা স্বতন্ত্র।” বাক্যের এক ব্যঞ্জনা- শ্রোতা রাঁধিতেছেন কি রাঁধিতেছেন না সেই দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় ব্যঞ্জনা, তিনি রাঁধিতেছেন নিশ্চিত তবে জানার ইচ্ছা হইতেছে কোন ব্যঞ্জন রাঁধিতেছেন। এই দুই ব্যঞ্জনার তফাত করিতে হইলে বানানের তফাতে সাহায্য হইবে। ইহার একটি বিকল্পও রবীন্দ্রনাথের মনে আসিয়াছিল: “যদি দুই ‘কি’-এর জন্যে দুই ইকারের বরাদ্দ করতে নিতান্তই নারাজ থাক তা হলে হাইফেন ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত: ‘তুমি কি রাঁধ্ছ’ এবং ‘তুমি কি-রাঁধ্ছ’।” (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ, ২৯০)
দুর্ভাগ্যবশত এই বিকল্পটি প্রয়োগের কথা তিনি বেশিদিন মনে রাখেন নাই। অর্থের প্রভেদ করার সমস্ত দায় তিনি বানানের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বিচার করিয়া দেখিতে হয়, এই দায় সত্য সত্যই বহন করা বানানের ক্ষমতায় কুলাইবে কিনা।
জীবনময় রায়কে লিখিত ১৯৩১ সালের পত্রিকায় তিনি আরো একটি পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কবি বলিতেছিলেন ভাষায় অতিরিক্ত যতিচিহ্ন ব্যবহার করার দরকার নাই। তাঁহার কথায়, “চিহ্নগুলো ভাষার বাইরের জিনিশ।”এইগুলি অগত্যা ব্যবহার করিতে হয় মাত্র। ভাষার গতি হইলে করিতে হয় না: “সেগুলোকে অগত্যার বাইরে ব্যবহার করলে ভাষায় অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়।” কবি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, “প্রাচীন পুঁথিতে দাঁড়ি ছাড়া আর-কোনো উপসর্গ ছিল না। ভাষা নিজেরই বাক্যগত ভঙ্গিদ্বারাই নিজের সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধি করত।”(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮৮)
কবি বলিতেছিলেন প্রশ্নবোধক আর বিস্ময়চিহ্নের তো প্রয়োজনই নাই। ‘কে, কি, কেন, কার, কিসে, কিসের, কত প্রভৃতি এক ঝাঁক অব্যয় শব্দ তো আছেই তবে চিহ্নের খোশামুদি করা কেন।’কবি বলিলেন, ‘তুমি তো আচ্ছা লোক’-এই বাক্যে তো শব্দই যাহা বলিবার বলিতেছে। তাহার পর আর বিস্ময়চিহ্ন বা প্রশ্নচিহ্ন যোগ করা বাহুল্য মাত্র। কবির ভাষায়, ‘ইঙ্গিতের পিছনে আরো একটা চিহ্নের ধাক্কা দিয়ে পাঠককে ডব্ল চমক খাওয়ানোর দরকার আছে কি। পাঠক কি আফিমখোর।’
আরো উদাহরণ দিয়াছেন তিনি। ‘রোজ রোজ যে দেরি করি আসো’-এই বাক্যের বিন্যাসেই নালিশের যথেষ্ট জোর আছে। বিস্ময়বোধক চিহ্ন বসাইবার কাজটিই বরং কবির বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। তিনি বাতলাইয়াছেন, ‘যদি মনে কর অর্থটা স্পষ্ট হল না তা হলে শব্দযোগে অভাব পূরণ’কর। ‘করলে ভাষাকে বৃথা ঋণী করা হয় না-যথা, ‘রোজ রোজ বড়ো-যে দেরি করে আস’।’ (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮৯)
বাংলা ভাষার এই দোষ নতুন, পশ্চিমের দোষ। পরাধীনতার কুফল। রবীন্দ্রনাথের হাতের ভাষায় এই ‘হাকিমী সাহেবিয়ানায় পেয়ে বসেছে’আমাদের। ‘কে হে তুমি’ বাক্যটা নিজের প্রশ্নত্ব হাঁকাইয়া চলিয়াছে। উহার পিছনে আবার একটা কুঁজওয়ালা সহিস লাগাইবার দরকার নাই। ‘আহা, হিমালয়ের কী অপূর্ব গাম্ভীর্য’-এই বাক্যের পরে আর একখানা ফোঁটা-সওয়ারি দাঁড়ি বা বিস্ময়চিহ্নের প্রয়োগ বৃথা। ভাষাকে বৃথা ঋণী না করাই কবির ধর্ম।
কবি শুদ্ধ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যতিচিহ্ন সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব বানানচিহ্ন সম্বন্ধেও খাটে। প্রশ্ন বা বিস্ময়চিহ্ন যেমন বাংলা ভাষায় মধ্যে মধ্যে অত্যাচার আকারে হাজির হয় দীর্ঘ ঈকারযুক্ত ‘কী’ বানানও তাহার অনুরূপ কিনা রবীন্দ্রনাথের ভাবিবার অবকাশ হয় নাই। আমার ধারণা- না হওয়াতে আমাদের ভাষারই ক্ষতি হইয়াছে। ভাষাকে বৃথা ঋণী করার সকল চেষ্টাই পরিহার করিতে হইবে। না করিলে ভাষা সম্বন্ধে সতর্ক হইবার কর্তব্যে শিথিলতা দেখা দেয়।
রবীন্দ্রনাথ নিজেই ইহার নজির দেখাইয়াছেন, ‘চিহ্নের উপর বেশি নির্ভর যদি না করি তবে ভাষা সম্বন্ধে অনেকটা সতর্ক হতে হয়। মনে করো কথাটা এই: “তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ।”এখানে বাবুয়ানার উপর ঠেস দিলে কথাটা প্রশ্নসূচক হয়-ওটা একটা ভাঙা প্রশ্ন- পুরিয়ে দিলে দাঁড়ায় এই, “তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ তার মানেটা কী বলো দেখি।” “যে” অব্যয় পদের পরে ঠেস দিলে বিস্ময় প্রকাশ পায়। “তুমি যে বাবুয়ানা শুরু করেছ”। প্রথমটাতে প্রশ্ন এবং দ্বিতীয়টাতে বিস্ময়চিহ্ন দিয়ে কাজ সারা যায়। কিন্তু যদি চিহ্ন দুটো না থাকে তা হলে ভাষাটাকেই নিঃসন্দিগ্ধ করে তুলতে হয়। তা হলে বিস্ময়সূচক বাক্যটাকে শুধরিয়ে বলতে হয়-“যে-বাবুয়ানা তুমি শুরু করেছ”। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৮৯-৯০)
রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা ভাষার এই শিক্ষাটিই ধরিয়া রাখিতেন তবে তাহাকেও ‘কি’ বানান বদলাইবার প্রাণান্তকর ব্যায়ামটি করিতে হইত না। বানানের খরচ বাঁচিত, প্রয়োজনের বিঘ্ন হইত না।
দুঃখের মধ্যে সমস্যা শুদ্ধ বানানের খরচ লইয়া নহে। ঋণই আসল সমস্যা। ভাষার কাজ শুদ্ধ ভাবের প্রকাশ নহে। ভাষা ভাবের জন্মও দিয়া থাকে। সংস্কারও করে। রবীন্দ্রনাথ- আমার আশঙ্কা- এই কথাটিই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভাবের মাপে ভাষা হইয়া থাকে- এই সংস্কারটাই কবির বাক্যভ্রংশের গোড়ায় বলিয়া আমার ধারণা। মনুষ্যজাতির মধ্যে এহেন অহমিকা আকছার দেখা যায়। মানুষ ভাবিয়া থাকেন তিনি ভাষা তৈয়ার করিয়াছেন। অথচ সত্য তো ইহাও হইতে পারে- ভাষাই মানুষ তৈয়ার করিয়াছে।
মানুষ ভাষার প্রভু নহে- বরং ভাষাই মানুষকে পালন করেন। এই সত্যে যতদিন সন্দেহ থাকিবে ততদিন রবীন্দ্রনাথের মতন আমাদেরও বাক্যভ্রংশ রোগের শিকার হইতেই হইবে। আমি বা আপনি কিয়ৎ পরিমাণে ভাষার স্রষ্টা- এই বিশ্বাসই আমাদের আদিপাপ। আর কে না জানে পাপ বাপকেও ছাড়ে না। কেবল ভাষার অধীন থাকিয়াই মানুষকে ভাষার প্রেম জয় করিতে পারে। যে মানুষ ভাষার অধীনতা সহজে স্বীকার করে তাহাকেই আমাদের দেশের সাধকরা ‘সহজ মানুষ’বলিয়াছেন।
‘কি’সমস্যায়ও আমার এই বক্তব্য। দুই বানানে এক শব্দ লিখিবার এই অসম্ভব বাসনা অভিমানি প্রভুর বিকারগ্রস্ত বাসনা বৈ নহে। ভাষা নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করিতে সক্ষম, বিকাশ করিতে সক্ষম। কারণ ভাষা নিজেই আকাশ। আর ভাষার সকাশেই ভাবের হিসাব-নিকাশ। ভাষা মানে কি মাত্র বানান বা যতিচিহ্ন? কখনই না।
বঙ্কিমচন্দ্র বকলম কমলাকান্ত লিখিলেন, “কে গায় ওই?” তিনি ‘কে’পদে কি বুঝাইলেন? “কে”শব্দে নানা ভাবের প্রকাশ হইতে পারে। প্রশ্ন যদি হইত ‘কে গায়?’- শুদ্ধ ওইটুকুই, তবে জানিতাম উত্তর হইবে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ কি রামপ্রসাদ, কি অন্য কোন একজন। কিন্তু ‘ওই’ শব্দ জোড়া দিয়া বঙ্কিম সেই ভাবের সর্বনাশ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় যদি দৈবক্রমে দীর্ঘ একার বলিয়া কোন স্বরচিহ্ন থাকিতও তাহাতেও শান্তি হইত না। কে গায়? বলা মুশকিল। প্রশ্ন হয়, “গায়” বলিতেও বা কি বুঝাইল?
‘পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ-উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর; -মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাক্যের তন্ত্রীকে অঙ্গুলি স্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?’
কমলাকান্তের ‘উত্তর কি?’
একটা উত্তর এই রকম:
‘ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল- তাই এই সংগীত এত মধুর লাগিল। শুদ্ধ তাই নয়। তখন সংগীত ভাল লাগিত- এখন লাগে না- চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম- সেই সময়ে এই পূর্বস্মৃতিসূচক সংগীত কর্ণে প্রবেশ করিল। তাই এত মধুর বোধ হইল।’
যথার্থ উত্তরণ হইল কি? কমলাকান্ত জানেন, হয় নাই।
‘-কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতিধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সংগীত, তেমনি সংসারের এক সংগীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সংগীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সংগীত আর কি শুনিব না?’
এতক্ষণে বুঝিলাম, ‘কে গায়?’-ওটা একটা কথার কথা মাত্র। গায়কের পরিচয় নিশ্চয় করিয়া জানা জিজ্ঞাসাকর্তার আদত উদ্দেশ্য ছিল না। এই যে কথার কথা-ইহার নামই ভাষার পালনক্ষমতা।
‘শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনিসংমিলিত বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারসংগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই- সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতিধ্বনিতে কর্ণাধার পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী- ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।’ (বঙ্কিম রচনবাবলী, খণ্ড ২, মু. ১৪, পৃ, ৪৫-৪৭)
হ্রস্ব ইকারের অধিকার যেখানে খাস্ বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সেখানে হ্রস্ব ইকারের অধিকার, সুতরাং দীর্ঘ ঈ’র সেখান হইতে ভাসুরের মতো দূরে চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য।’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব , পৃ. ১১২) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ‘বাঙ্গালা বানান সমস্যা’ নামে এক প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলেন বাংলা ১৩৩১ সালে। তাহার পরের বছর মাত্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বকলম প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বাহির হয় রবীন্দ্রনাথের আদেশ- বাংলা ‘কি’ শব্দ দুই বানানে লিখিতে হইবে। শহীদুল্লাহর বিষয় ছিল খানিক ভিন্ন। তিনি বলিতেছিলেন বাংলার সকল শব্দই উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিতে হইবে। তাঁহার বক্তব্য ছিল, শ্রবণ করা অর্থে বাংলায় ‘শোনা’ শব্দ লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু স্বর্ণ অর্থে তাহা কেন ‘শোনা’ লেখা হইবে না? একটা উত্তর- সংস্কৃত স্বর্ণ শব্দে দন্ত্য ‘স’ আছে, তাই ‘সোনা’ লেখাই স্বাভাবিক। তিনি বলিলেন, ‘সোনা’ শব্দের উচ্চারণ তো ‘শোনা’। তাই ‘শোনা’ লেখাই তো উচ্চারণের বিচারে স্বাভাবিক।
তখন আপত্তি উঠিতেছে, ‘স্বর্ণ’ আর ‘শ্রবণ করা’ দুই অর্থ, দুই ভাব। এই ভাবের তফাত বজায় রাখিতে হইলে বানানের তফাত রাখার দরকার আছে। স্বর্ণ অর্থের ব্যঞ্জনা আর ‘শ্রবণ করা’র ব্যঞ্জনা কি এক জিনিস? উভয়ের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক ‘শোনা’শব্দে দুই ভাব প্রকাশ হইবে কি করিয়া? অথবা ‘সোনা’আর ‘শোনা’ দুই বানানই রাখিতে হয়। ইহার জবাবেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিলেন : ‘যদি বল এ কি হইল! স্বর্ণ আর শ্রবণ করা দুই-ই যদি শোনা হয়, তবে মানে বুঝিব কেমন করিয়া?’
“আমি বলিব যদি গায়ের তিলে গাছের তিলে কোন গোল না ঠেকে, যদি গানের তালে আর নাচের তালে ঠোকাঠুকি না ঘটে, তবে স্বর্ণ শোনায় আর শ্রবণ শোনায়ও কোন হাঙ্গামা হইবে না। আসল কথা, ভাষায় অক্ষরের মত শব্দ কখন দল ছাড়া হইয়া একেলা আসে না। অক্ষর থাকে শব্দের সঙ্গে জড়াইয়া আর শব্দ থাকে বাক্যের মধ্যে মিশিয়া। কাজেই মানে যদি আলাদা আলাদা হয়, তবে বানান বা উচ্চারণ এক হইলেও বুঝিবার গোলমাল বড় একটা হয় না।” (ভাষা ও সাহিত্য, স. ৩, পৃ. ৮১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু জায়গায় কবুল করিয়াছেন তিনি ব্যাকরণে কাঁচা। তাঁহার ভাষায়, ‘কী সংস্কৃত ভাষায় কী ইংরেজিতে আমি ব্যাকরণে কাঁচা’। কিন্তু বাংলায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হয় না বাংলা ব্যাকরণ তিনি আর কাঁহারও অপেক্ষা কম জানেন। তবু তাঁহার বিনয়কে অবিশ্বাস করিব না। তিনি জানাইয়াছেন, “ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাত এই- তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোলবিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে-চলা-পথের ভ্রমণকারী।” (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৯) বৈষ্ণব ভাবিয়া বিনয়কে তুচ্ছ করিবেন না।
পায়ে চলা পথের এক জায়গায় শেষ হয়। সে কথা কবির অজানা নয়। পায়ের পথিক ভূগোলে অপটু হইতেই পারেন। তাহাতে দোষ নাই। দোষ অপটুতাকে ধর্মের মর্যাদা দেওয়ায়। ঠাকুর মোটেও নিশ্চিত হইতে পারেন নাই, বাংলা ‘কি’ শব্দটি কি, অর্থাৎ কোন জাতের? তিনি একবার বলিয়াছেন শব্দটি অব্যয়, আর বার বলিয়াছেন সর্বনাম। আগে এই প্রশ্নটির মীমাংসা না করিয়া হাঁটিতে শুরু করা পায়ে চলার কাজ সন্দেহ নাই, ভূগোলবিজ্ঞানীর কাজ এ রকম নহে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শব্দটি বিশেষণ হইয়া যায়। আবার আরো বিশেষ করিয়া দেখিলে ইহাকে ‘ক্রিয়া বিশেষণ’ হিসাবেও দেখা যায়। প্রয়োজনে সে বিশেষ্যের ভূমিকাও লইতে পারে। ক্রিয়ার কাজও কখনো বা সে করিলে বিস্ময়ের থাকিবে না।
এই যে বিভিন্ন প্রয়োগ, বিবিধ ব্যবহার তাহার মধ্যে কি কোনই ঐক্য নাই? সেই ঐক্যের নিয়মের সূত্র যতদূর জানি পহিলা রাজা রামমোহন রায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাবিতে শিহরিয়া উঠি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি সেই আবিষ্কারের খবর লয়েন নাই? না লইবার কোন কারণ তো নাই। তবে আলামত দেখিতেছি। ঠাকুরের লেখায় ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ বলেন :
“প্রশ্নসূচক ‘কি’ শব্দের অনুরূপ আর-একটি ‘কি’ আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম। এ তার প্রকৃত অর্থের প্রয়োজন সেরে মাঝে মাঝে খোঁচা দেবার কাজে লাগে। যেমন : কী তোমার ছিরি, কী যে তোমার বুদ্ধি।” (‘বাংলা ভাষা-পরিচয়’, পৃ. ১১৩)
রামমোহন ভাল করিয়া পড়া থাকিলে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়া লইতেন, বাংলায় ‘কি’ শব্দ একটাই। কারকভেদে (অথবা রামমোহনের ভাষায় ‘পরিণমন’ বা ‘পরিণাম’ ভেদে) ইহার রূপভেদ হয় মাত্র। যেমন ‘কি’ শব্দ কর্তৃকারকে (রামমোহনের ভাষায় ‘অভিহিত’ পদে) যেমন ‘কি’ কর্মকারকেও তেমনি ‘কি’ই। অধিকরণে ‘কিসে’ অথবা ‘কিসেতে’ আর সম্বন্ধে ‘কিসের’। সবগুলিই ‘কি’ শব্দের আত্মীয়রূপ বৈ নহে। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৮)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দেখাইয়াছেন, রামমোহনের ব্যাকরণে একটু অপূর্ণতা আছে। কি, কিসে, কিসেতে, কিসের প্রভৃতি সকল শব্দরূপের গোড়া মাত্র ‘কি’ নহে। ‘কি’ শুদ্ধ সকলেরই গোড়া হইল অন্য একটি রূপ- কাহা (বা কাঁহা)। ইহা ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। জাতিতে সর্বনাম। ইহার সহিত তুলনীয়, সহধর্মিণী আরও সর্বনাম শব্দ আছেন, যথা: তাহা, যাহা, ইহা, উহা ইত্যাদি।
তবে কাহা শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া তাহার রূপের খানিক বিশেষত্ব রহিয়াছে। এই শব্দে বিভক্তির একবচন রূপ কর্তা ও কর্ম দুই কারকেই ‘কি’। বহুবচনে ‘কিসের’। তবে শহীদুল্লাহ লিখিয়াছেন, “কাহা শব্দের ক্লীবলিঙ্গের বহুবচনে প্রয়োগ নাই। কখনও কখনও বহুবচন বুঝাইতে দ্বিরুক্তি হয়। যথা- কি কি হইয়াছে? সে কি কি লইয়াছে?” (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, স. মাওলা ব্রাদার্স, মু. ২, পৃ. ৭৮)
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মোটেও কেমাল পাশা নহেন। তিনিও প্রচলিত ব্যাকরণের মতো বাংলায় ছয় কারকই দেখাইয়াছেন। রামমোহন বলিয়াছেন, বাংলায় দরকারই নাই অত কারকের। তাঁহার বয়ান : “গৌড়ীয় ভাষাতে নামের চারি প্রকার রূপের দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অভিহিত, যেমন রাম, কর্ম্ম, যেমন রামকে; অধিকরণ, যেমন রামে; সম্বন্ধ, যেমন রামের।” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১৩) রামমোহনের কথাই সঠিক বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। আরো মনে করিতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ও রামমোহনের কথানুসারে অমৃত হইয়াছিল।
‘যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার বোধের নিমিত্ত ভাষাতে অভিহিত পদের পরে “দিয়া” শব্দের প্রয়োগ করা যায়, যেমন, ছুরি দিয়া কাটিলেন। আর কখন [কখন] সম্বন্ধ পরিণামের পরে “দ্বারা” শব্দ দিয়া ঐ করণকে কহা যায়; যেমন, ছুরির দ্বারা কাটিলেন।’(পৃ. ১৫) আরো পড়া যাইতেছে : ‘কখন বা অধিকরণ বাচক বিভক্তির দ্বারা করণের জ্ঞান হইয়া থাকে, যদি সেই করণ অপ্রাণি হয়; যেমন, ছুড়িতে কাটিলেন। অতএব করণের নিমিত্ত শব্দের পৃথক রূপ করিবার আবশ্যক দেখি নাই।’ (পৃ. ১৫) শহীদুল্লাহ করিয়াছেন, ‘কি দিয়া, কিসের দ্বারা, কিসে।’ দরকার ছিল কি? (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, মু. ২, পৃ. ৭৭)
একই কারণে রামমোহন বলিলেন, বাংলায় অপাদান কারকেরও প্রয়োজন নাই। পড়া যাইতেছে :
‘কোন এক ক্রিয়ার বক্তব্য স্থলে যখন অন্য বস্তু হইতে এক বস্তুর নিঃসরণ অথবা ত্যাগ বোধ হয়, তখন তাহার জ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রথম বস্তুর নামের পরে যদি সেই প্রথম বস্তু একবচনান্ত হয় তবে “হইতে” এই শব্দের প্রয়োগ করা যায়। আর যদি বহুবচনান্ত হয় তবে বহুবচনান্ত সম্বন্ধীয় পরিণাম পদের পরে “হইতে” ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন গ্রাম হইতে, মন্ত্রিদের হইতে, বেণেদের হইতে, অতএব বঙ্গভাষায় অপাদান কারকের নিমিত্ত শব্দের পৃথক রূপ করিবার আবশ্যক নাই।’ (পৃ. ১৫)
তদ্রূপ “সম্বোধনের নিমিত্তেও শব্দের পৃথক রূপের প্রয়োজনাভাব” বলিয়া রামমোহন তাহার আলাদা প্রকরণ করেন নাই। সম্প্রদান সম্বন্ধেও একই কথা খাটিবে : “ভাষাতে রূপান্তরাভাব, এই হেতুক লিখা গেল না।” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১৪, পাদটীকা ৩)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সহিত পণ্ডিত হরনাথ ঘোষ আর সুকুমার সেনের ব্যাকরণও একমত। ঘোষ ও সেনের বইতে ‘কাহা’ শব্দের সম্ভমসূচক একটা রূপও পাওয়া যাইতেছে- কাঁহা বা সংক্ষেপে কাঁ। (বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ, পৃ. ২৭৫)
এই সকল কিছু না দেখিয়াই, না চিন্তিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, শ্যামাপ্রসাদ, আইন কর। বাংলাভাষার অনেক মহদুপকার রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা তো তাহাকে “কি” শব্দের বানান বদলাইবার অধিকার দেয় নাই। এয়াহুদিপুরানে বলে, সন্তানের গলা কাটিবার অধিকার স্বয়ং ভগবানও এব্রাহিমকে দেন নাই। তিনি তাঁহাকে পরীক্ষা মাত্র করিতেছিলেন। দীপ্তি হউক বলিলেই ভাষায় দীপ্তি হয় না। কোন ভাষাই মাত্র ছয় দিনে তৈরি হয় নাই। রামমোহনে ফিরিয়া চল ‘কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিশেরও জোর।’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৯
রাজা রামমোহন রায় দেখাইয়াছেন ভাষার তাবৎ শব্দ প্রথমত দুই প্রকারে বিভক্ত হয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ। “যে শব্দের অর্থ প্রাধান্যরূপে জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাকে বিশেষ্য কহে; যেমন, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর, ইত্যাদি স্থলে রামের জ্ঞান প্রাধান্যরূপে হয়, এ নিমিত্তে রাম বিশেষ্য।
“আর যাহার অর্থ অপ্রাধান্য রূপে বুদ্ধির বিষয় হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর ইত্যাদি স্থলে যাইতেছেন ও সুন্দর এ দুই শব্দের অর্থ রাম শব্দের অর্থেতে অনুগত হয়, এ কারণ বিশেষণ পদ কহে।” (পৃ. ১১)
রামমোহনের ব্যাকরণে বিশেষ্য নানা প্রকারের হয়। বিশেষ্যকে ‘নাম’ অথবা ‘সংজ্ঞা’ দুইটাই বলিয়াছেন তিনি। এই কাণ্ডজ্ঞান অনুসারে “কাহা” শব্দও একপ্রকার ‘সংজ্ঞা’ বা ‘নাম’ শব্দ। সুতরাং ভাষার প্রথম দুই ভাগ অনুসারে কাহা শব্দের জাতক ‘কি’ শব্দ বিশেষ্য। বিশেষ্য বা সংজ্ঞার মধ্যে ইহা প্রতিসংজ্ঞা বা সর্বনাম জাতীয় হইয়াছে। রামমোহনের সহিত সম্যক পরিচয় থাকিলে ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ বইতে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করিতে হইত না, “প্রশ্নসূচক ‘কি’শব্দের অনুরূপ আর-একটি ‘কি’আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম।” (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ১১৩)
সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় কি শব্দ আদিতে সর্বনাম, তবে অব্যয় হিসাবে তাহার প্রয়োগ আছে। অন্য প্রয়োজনেও তাহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। রামমোহন লিখিয়াছেন : “বিশেষ্য পদকে নাম কহি, অর্থাৎ এ রূপ বস্তুর নাম হয় যাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে। যেমন রাম, মানুষ, ইত্যাদি। অথবা যাহার উপলব্ধি কেবল অন্তরিন্দ্রিয়-দ্বারা হয় তাহাকেও এইরূপ নাম কহেন, যেমন ভয়, প্রত্যাশা, ক্ষুধা ইত্যাদি।”
‘ঐ নামের মধ্যে কতিপয় নাম বিশেষ ব্যক্তির প্রতি নির্ধারিত হয়, তাহাকে ব্যক্তি সংজ্ঞা কহি, যেমন রামচরণ, রামভদ্র, ইত্যাদি। আর কতিপয় নাম এক জাতীয় সমূহ ব্যক্তিকে কহে, তাহাকে সাধারণ সংজ্ঞা কহি, যেমন মনুষ্য, গরু, আম্র, ইত্যাদি। এবং কতক নাম নানাজাতীয় সমূহকে কহে, যাহার প্রত্যেক জাতি অন্য [অন্য] জাতি হইতে বিশেষ [বিশেষ] ধর্ম্মের দ্বারা বিভিন্ন হয়, তাহাকে সর্ব্বসাধারণ বা সামান্য সংজ্ঞা কহি, যেমন ‘পশু’, মনুষ্য, গরু, হস্তি প্রভৃতি নানাবিধ বিজাতীয় পদার্থ সমূহকে কহে। এবং “বৃক্ষ” নানাবিধ বিজাতীয় আম, জাম, কাঁটাল ইত্যাদিকে প্রতিপন্ন করে’।
‘ঐ নামের মধ্যে কতিপয় শব্দ ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হয়, অথচ ঐ সকল শব্দ স্বয়ং স্বতন্ত্র বিশেষ [বিশেষ] ব্যক্তিকে কিম্বা বিশেষ ব্যক্তিসমূহকে নিয়ত অসাধারণরূপে প্রতিপন্ন করে না, ওই সকলকে প্রতিসংজ্ঞা কহি, যেমন আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি।’ (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১১-১২, নিম্নরেখা আমরা যোগাইয়াছি)
একইভাবে রামমোহন রায় বিশেষণ শব্দেরও নানান জাতি নির্ণয় করিয়াছেন। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে যে সকল শব্দকে বিশেষণ বলা হইয়া থাকে, তাহাদের নাম রামমোহন রাখিয়াছেন ‘গুণাত্মক বিশেষণ’। লিখিয়াছেন : ‘বিশেষণ শব্দের মধ্যে যাহারা বস্তুর গুণকে কিম্বা অবস্থাকে কাল সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কহে, সে সকল শব্দকে গুণাত্মক বিশেষণ কহি, যেমন, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি।’(গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১২, নিম্নরেখা আমরা যোগ করিয়াছি)
“আর যাহারা কালের সহিত সম্বন্ধপূর্ব্বক বস্তুর অবস্থাকে কহে, তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, আমি মারি, তুমি মারিবে।” প্রচলিত ব্যাকরণে এই পদের নাম ‘ক্রিয়া’মাত্র। ক্রিয়ার অপর নাম ‘আখ্যাত’পদ। ইহা ভাষায় ব্যবহার্যও হইয়াছে। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ৩২)
গুণাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক ছাড়াও রাজা রামমোহন রায় আরও পাঁচ জাতের বিশেষণ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে, ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ, সম্বন্ধীয় বিশেষণ, সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ এবং অন্তর্ভাব বিশেষণ রহিয়াছে। মনোযোগ করিবার বিষয়, অব্যয়ের জন্য তিনি কোন আলাদা প্রকরণ করেন নাই।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের তারিফ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার এই অব্যয় জাতীয় শব্দের আলাদা প্রকরণ না করার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি শুদ্ধ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন: “রামমোহন ‘সর্বনাম’-কে বলেছেন ‘প্রতিসংজ্ঞা’, এর সঙ্গে তুলনীয় পঞ্জাবীতে ব্যবহৃত নাম ‘পড়নাঊঁ’ (= প্রতিনাম)। নামটি সার্থক, ‘সর্বনাম’এই শব্দের মতো এর ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন থাকে না। ‘প্রতিনাম’শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার জন্যে আমি ‘সর্বনাম’-এর পাশে ‘প্রতিনাম’ শব্দটিও আমার বাঙলা ব্যাকরণে ব্যবহার করেছি।” (মনীষী স্মরণে, পৃ. ৬)
রামমোহন দেখিয়াছেন ভাষায় অব্যয়ের কাজ বিশেষণেরই কাজ। তিনি কাজ দেখিয়া নাম করিয়াছেন, রূপ দেখিয়া ভোলেন নাই। তাই অব্যয় শব্দের আলাদা প্রকরণ করার “প্রয়োজনাভাব” হইয়াছে। কয়েক গুটি উদাহরণ লইলেই আবিষ্কারটি পরিচ্ছন্ন হইবে। মেঘ কাটিয়া যাইবে।
ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণকে ইংরেজিতে বলে ‘পার্টিসিপ্ল্’। ইহা কি পদার্থ? রামমোহন কহেন, “যাহারা অন্য ক্রিয়াগত কালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তুর কাল সংক্রান্ত অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি প্রহার করত বাহিরে গেলেন, ভোজন করিতে [করিতে] কহিয়াছিলেন।” (পৃ. ১২)
আর “যাহারা ক্রিয়া কিংবা গুণাত্মক বিশেষণের অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি শীঘ্র যান, তিনি অত্যন্ত মৃদু হন।” (পৃ. ১২)
প্রচলিত ব্যাকরণের অব্যয়কেও রামমোহন ‘বিশেষণ’রূপেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যথা : “যে সকল শব্দকে পদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিয়মমতে রাখিলে সেই পদের সহিত অন্য পদের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ বুঝায়, সেই শব্দকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি; যেমন রামের প্রতি ক্রোধ হইয়াছে।” (পৃ. ১২) ইংরেজিতে এইসব পদকে প্রিপোজিশন কহে।’
‘রামের’পদ বানাইতে রাম শব্দের সহিত যাহা যোগ করা হইয়াছে (এর), তাহাতে বুঝাইত শুদ্ধ ক্রোধের কর্তা রাম। তবে কিনা ‘প্রতি’শব্দটি বসিয়া রামকে ক্রোধের গৌণকর্ম বানাইয়া সারিয়াছে। এই প্রতিশব্দটি বাংলায় ‘অনুসর্গ’ বলিয়াই কথিত হয়। রামমোহন রায়ের লেখা বাংলা ব্যাকরণের ইংরেজি-সংস্করণে এই জাতের পদকেও ‘প্রিপোজিশন’ বলা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। (নির্মল দাশ, বাংলা ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৪৭)
বিশেষণের চতুর্থ প্রকারের (অব্যয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী) নাম সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ। রামমোহন উল্লেখ করিলেন,
“যাহারা দুই বাক্যের মধ্যে থাকিয়া ঐ দুই বাক্যের অর্থকে পরস্পর সংযোগ কিংবা বিয়োগরূপে বুঝায়, অথবা দুই শব্দের মধ্যে থাকিয়া এক ক্রিয়াতে অন্বয় বোধক হয়, কিন্তু কোন শব্দের বিভক্তির বিপর্য্যয় করে না, সে সকল শব্দকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি : যেমন, তিনি আমাকে অশ্ব দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি লইলাম না; আমি এবং তুমি তথায় যাইব, আমাকে ও তোমাকে দিয়াছেন।”
ইংরেজিতে এইগুলি ‘কনজাংশন নামে চলে’। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১২)
পঞ্চম জাতীয় বিশেষণ (তৃতীয় শ্রেণীর অব্যয়) রামমোহনের বয়ানে এই রকম : “যাহারা অন্য শব্দ সংযোগ বিনাও ঝটিতি উপস্থিত অথবা অন্তকরণের ভাবকে বুঝায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি; যেমন, হা আমি কি কর্ম্ম করিলাম!” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১২-১৩)
এতক্ষণ একটু লম্বা শ্বাস টানিয়া রামমোহন পড়িবার কারণ কি? বাংলা ব্যাকরণে ‘কি’ শব্দ প্রতিসংজ্ঞা জাতীয় [অর্থাৎ বিশেষ্য কুলোদ্ভব] হইলেও বিশেষণকুলে হামেশাই তাহার যাতায়াত আছে- এই কথা প্রমাণ করার আবশ্যক দেখি আজিও ফুরাইল না। অথচ তাহার কুল পরিচয় প্রতিসংজ্ঞাতেই পাওয়া যাইবে। চেহারা দেখিয়া লোকে পরিচয় তারপরও ভুলিয়া যায়। এই কথা এখনও সত্য।
বাংলায় “আমি”, “তুমি”, “সে” প্রভৃতি শব্দের যে জাত “যে” শব্দেরও সেই জাতই। আমিকে “ইতর লোকে” “মুই” কহিয়া থাকে। তুচ্ছতা প্রকাশের নিমিত্ত “তুমি” স্থানে “তুই” হইয়া থাকে। “সে শব্দের প্রয়োগ অপ্রত্যক্ষ বস্তু বা ব্যক্তি যাহার জ্ঞান বা উল্লেখ পূর্বে থাকে তাহার স্থলে হয়, যেমন সে চৌকি, সে ব্যক্তি। “যখন সম্মান তাৎপর্য্য হইবেক তখন সে ইহার স্থানে তিনি কিম্বা তেঁহ আদেশ হয়, আর অন্য তাবৎ পরিনামে [কারকে] প্রথম স্বর সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন, তাঁহাকে, তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের, ইত্যাদি।” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৬)
“সে” শব্দের আরেক রূপ “এ”। বস্তুর কিম্বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ-অভিপ্রেত হইলে “এ”শব্দের প্রয়োগ হয়। সম্মান অভিপ্রেত হইলে “এ”স্থানে “ইনি”আদেশ হয় এবং প্রথম স্বরেরও সানুনাসিক উচ্চারণ হয়। “কিয়দন্তর পরোক্ষ অভিপ্রেত হইলে “ও” শব্দের প্রয়োগ হয়, আর তাহার রূপ “এ” শব্দের মতন হইয়া থাকে। কেবল ওকারের স্থানে “উ”হইয়া থাকে। সম্মান অভিপ্রেত হইলে “ও”স্থানে উনি আদেশ হয়, আর প্রথম স্বরের সানুনাসিক উচ্চারণ হয়।”
“যে” শব্দ আসিয়াছে “যাহা” হইতে। এই শব্দ প্রতিসংজ্ঞা বা সর্বনাম। ইহার রূপও ‘সে’শব্দের ন্যায় হয়। অর্থাৎ সে, তাহাকে, তাহাতে, তাহার ইত্যাদির ন্যায় যে, যাহাকে, যাহাতে, যাহার ইত্যাদি হয়। সম্মান অভিপ্রেত হইলে যিনি, যাঁহাকে, যাঁহাতে, যাঁহার ইত্যাদি রূপে পরিণাম হয়।’ (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৭)
এখন ‘কাহা’ শব্দের রূপ। আবারও রামমোহন হইতে সাক্ষাৎ উদ্ধার করিতেছি:
‘জিজ্ঞাসার বিষয় পদার্থ যদি ব্যক্তি হয় তবে কে, আর যদি বস্তু হয় তবে কি, ইহার প্রয়োগ হয় কিন্তু অধ্যাহৃত কিম্বা উক্ত ক্রিয়া যাহার যোজক হইয়াথাকে, যেমন কে কহিয়াছিল? এ স্থলে বাক্যের অর্থ কে কহিয়াছিল উক্ত হইয়াছে; কি? অর্থাৎ কে বসিয়াছে, বা গিয়াছে। এ স্থলে ক্রিয়া উহ্য হইল, এবং কি কহিতেছে? কি? অর্থাৎ কি হয় ইত্যাদি।’ (পৃ. ২৭; নিম্নরেখার যোগান দিয়াছি, নিরেট লিখনরীতি রামমোহন রায়ের)
‘যাহা’শব্দের যে রূপ, কাহা শব্দেরও সেই রূপই হইয়া থাকে। “প্রভেদ এই যে সম্মান অভিপ্রেত হইলেও বিশেষ নাই।” (পৃ. ২৭) অর্থাৎ ‘যিনি’র ন্যায় ‘কিনি’ হয় না।
যদি সময় জিজ্ঞাস্য হয় তবে, “কবে”আর “কখন”শব্দের প্রয়োগ হয়। ইহাদের রূপান্তর নাই। তবে “ওই দুয়ের প্রভেদ এই যে, কবে, ইহার প্রয়োগ দিন জিজ্ঞাস্য [হইলে]; আর, কখন, ইহার প্রয়োগ সময় জিজ্ঞাস্য হইলে প্রায় হইয়া থাকে, যেমন কবে যাইবে? অর্থাৎ কোন্ দিন যাইবে? কখন যাইবে? অর্থাৎ কোন্ সময়ে যাইবে।” (পৃ. ২৮)
একই নিয়মে অন্যান্য প্রতিসংজ্ঞারও প্রয়োগ হয়। “যখন স্থান জিজ্ঞাস্য হয় তখন “কোথা” কিম্বা “কোথায়” ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কোথা যাইবে, কোথায় যাইবে? অবস্থা কিম্বা প্রকার ইহার জিজ্ঞাস্য হইলে-“কেমন” শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা কেমন আছেন? ইহার রূপান্তর নাই।” (পৃ. ২৮)
রামমোহনের বিভাজন অনুসারে কি শব্দ অব্যয় নয়, কারণ ইহার ব্যয় বা রূপান্তর আছে। শুদ্ধমাত্র অভিহিত পদ আর কর্মকারকেই ইহা একরূপ থাকে। অন্য পক্ষে “নান্ত কোন্ শব্দ”অব্যয়। কে, কি, কবে, কোথা প্রভৃতি শব্দ নান্ত কোন্ শব্দের প্রতিনিধি হয়। যেমন কে- কোন্ জন? কি- কোন্ বস্তু? কবে- কোন্ দিন, কোথা- কোন্ স্থান ইত্যাদি। কিন্তু খোদ “কোন্”শব্দটি অব্যয় পদবাচ্য। “ইহার রূপান্তর হয় না। আর বিশেষণ পদের ন্যায় ব্যবহার হয়।
“কোন্”শব্দের উচ্চারণ যখন “হলন্ত”বা “নান্ত”না হইয়া অকারান্ত বা ওকারান্ত হয়, তখন কোন জাতিবাচক শব্দের অনির্দ্ধারিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হয়, কাহাকেও নির্দিষ্ট ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হয় না। অকারান্ত বা ওকারান্ত ‘কোন’শব্দ বিশেষণের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে; যেমন, কোন মনুষ্য ঘরে আছে? অর্থাৎ মনুষ্যের কোন এক ব্যক্তি ঘরে আছে? কোন পুস্তক পেটরাতে আছে? অর্থাৎ পুস্তকের কোন এক খান পেটরাতে আছে?” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৮)
‘অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হইলে, কেও [কেউ], কিম্বা কেহ, ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কেও ঘরে আছে, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি ঘরে আছে? আর কোন শব্দ ও কেহ শব্দ যখন দ্বিরুক্তি হয় তখন প্রশ্ন অভিপ্রেত না হইয়া অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি সকলকে বুঝায়, যেমন কোন [কোন] ব্রাহ্মণ, কোন [কোন] রাজা ইত্যাদি।’ (পৃ. ২৮, নিম্নরেখা আমরা যোগাইয়াছি)
রামমোহন তাড়াহুড়া করিয়া লিখিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি দেখাইতে পারিতেন এই প্রণালীতে ‘কেন’এবং ‘কিছু’ শব্দও নিষ্পন্ন হইয়াছে। “কেন”মানে কি কারণে, কি হেতু ইত্যাদি। আর “কিছু”শব্দেরই প্রয়োগ হয় অনির্দ্ধারিত কোন বস্তু জিজ্ঞাসাস্য হইলে, যেমন- ঘরে কিছু খাবার আছে? ইহা “কি”শব্দের রূপান্তর। একই সঙ্গে ইহার প্রয়োগ বিশেষণের ন্যায়ও বটে। বিশেষ্যের ন্যায়ও হইতে পারে, যেমন-‘কিছু হইয়াছে?’ ‘কিছু বলিবে?’ ইত্যাদি।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৮৬ সনে জন্ম লইবার পর হইতেই সংস্কার কাজে মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। ২০০৫ সালে তাঁহাদের বানানবিধির পঞ্চম সংস্করণ ছাড়া হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অর্থগত প্রয়োগ ধরিয়া কি ‘কর্মবাচক সর্বনাম’ কি ‘প্রশ্নমূলক সর্বনাম’, কি ‘বিশেষণের বিশেষণ’-সকল ক্ষেত্রেই ‘কি’বানান ‘কী’লেখা হইবে। একই সঙ্গে তাঁহারা বিধান দিয়াছেন ‘বিকল্পাত্মক বিশেষণ’ [যাহাকে কেহ কেহ ‘সমুচ্চয়ার্থক বিশেষণ’ও বলিতে পারেন] হিসাবেও ‘কী’চলিবে।[১২.১] (আকাদেমি বানান অভিধান, স. ৫, পৃ. ৫৫৪)
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন “‘কী’শব্দের করণ কারকের রূপ : কিসে, কিসে ক’রে, কী দিয়ে, কিসের দ্বারা। অধিকরণের রূপও ‘কিসে’যথা: এ লেখাটা কিসে আছে।” (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৯৯)
আর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি লিখিতেছেন : “বিকল্পাত্মক বিশেষণ হিসেবেও কী ব্যবহৃত হবে: কী রাম কী শ্যাম, দুটোই সমান পাজি! এইসঙ্গে সমজাতীয় ব্যাকরণসূত্রে কীসে এবং কীসের দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লেখা উচিত এবং তার প্রচলন বাড়ছে’।” (বিধি ১২.১)
জানি সব শিয়ালের এক রা। প্রভেদ মধ্যে মধ্যে। প্রভেদের মধ্যে ঢাকার বাংলা একাডেমি ‘বিকল্পাত্মক বিশেষণ’কে এখনও অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়া লিখিবার পক্ষে। প্রমাণ : “অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন : তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।” [.০১] (প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম; ৩য় সংস্করণ) ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, স. ২, পৃ. ১২২১) প্রভুর ছলের অভাব নাই “প্রেমনারায়ণ বিরক্ত হইয়া আপন মনের কথা আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন-চাক্রি করা ঝক্মারি- চাকরে কুকুরে সমান- হুকুম করিলে দৌড়িতে হয়। মতে, হলা, গদার জ্বালায় চিরকালটা জ্বলে মরেছি- আমাকে খেতে দেয় নাই- শুতে দেয় নাই- আমার নামে গান বাঁধিত- সর্ব্বদা ক্ষুদে পিঁপড়ার কামড়ের মত ঠাট্টা করিত- আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত ও মধ্যে [মধ্যে] আপনারাও আমার পেছনে হাততালি দিয়া হো হো করিত। এসব সহিয়া কোন ভাল মানুষ টিকিতে পারে? ইহাতে সহজ মানুষ পাগল হয়। আমি যে কলিকাতা ছেড়ে পলাই নাই এই আমার বাহাদুরি- আমার বড় গুরুবল যে অদ্যাপিও সরকারগিরি কর্ম্মটি বজায় আছে। ছোঁড়াদের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এখন জেলে পচে মরুক- আর যেন খালাস হয় না- কিন্তু এ কথা কেবল কথার কথা, আমি নিজেই খালাসের তদ্বিরে যাইতেছি। মনিবওয়ারি কর্ম্ম। চারা কি? মানুষকে পেটের জ্বালায় সব করিতে হয়।” -টেকচাঁদ ঠাকুর (আলালের ঘরের দুলাল, পৃ. ২৩)
বাংলা আকাদেমির দ্বিতীয় অবয়বের নাম উচ্চারণে বল প্রয়োগ বা শ্বাসের আঘাতের বিষয় হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই যুক্তির বয়ান রাজশেখর বসু সহজেই করিয়াছিলেন।
চলন্তিকা অভিধানে রাজশেখর ‘কী’শব্দের অর্থ দিয়াছিলেন : “বেশী জোর দিতে, যথা- কী সুন্দর! তোমার কী হয়েছে?” মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বলিয়াছিলেন, “আরও কোন কোন অভিধানে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে পারিতেছি না।” (বাংলা বানান, পৃ. ৮০)
সত্য বলিতে উল্লেখ করিবার মত সকল বাংলা অভিধানে ইহাই আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষের অভিধানে লেখেন :
‘মৈথিলী বা উত্তরবিহারী ভাষায় ‘কি’ও ‘কী’র প্রভেদ নাই। (Grierson’s Maithili Dialect, Pt. I., Grammar, 2nd edition, pp. 99-101) তার অনুকরণে প্রাচীন বাংলায়ও ‘কি’ ও ‘কী’নির্ব্বিশেষে প্রচলিত হয়।” জ্ঞানেন্দ্রমোহন আরও জ্ঞান দিয়াছেন, কী শব্দটি ‘মধ্য বাংলা সাহিত্যে অপ্রচলিত। অধুনা কোন কোন লেখক কর্ত্তৃক পুনঃপ্রচলিত।’
সুকুমার সেন প্রণীত ‘বুৎপত্তি-সিদ্ধান্ত বাংলা-কোষ’অভিধানেও ‘কী’শব্দের কোন জায়গা হয় নাই। কিন্তু ‘কি’শব্দের পাঁচ রকম অর্থ দেওয়া হইয়াছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে এই অভিধানের ইংরেজি সংস্করণ পহেলা ১৯৭১ সালে বাহির হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণ খোদ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি হইতে বাজারে আসিয়াছে।
‘বুৎপত্তি সিদ্ধান্ত’ অনুসারে, “কি” শব্দ প্রশ্নবাচক, অনির্দেশক সর্বনাম। ইহা শেষ বিচারে সংস্কৃত “কিম্” হইতে আসিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের প্রয়োগ এই অর্থেই : ‘কি লআঁ যাইব ঘর’।
“কি” শব্দের দ্বিতীয় প্রয়োগ প্রশ্নবাচক অব্যয়ে আকারে। সুকুমার সেন দুই দুইটি প্রয়োগ দেখাইতেছেন এই অর্থে। দুইই চর্যাপদ হইতে, ‘দুহিল দুধু কি বেন্টে যামায়’ (চর্যা ৩৩) এবং ‘ভাগ তরঙ্গ কি সোসঈ সাঅর’ (চর্যা ৪২)
“কি” শব্দের তৃতীয় প্রয়োগও অব্যয় আকারে। এই প্রয়োগের অর্থে, সুকুমার সেন যাহাকে বলেন ‘দ্বৈধ’সেই ভাবই বুঝাইতেছে। বাংলা আকাদেমির লোকেরা হয়তো বা বলিবেন ‘বিকল্পাত্মক’, কিংবা “সমুচ্চয়বোধক”। এই প্রয়োগও চর্যাপদ হইতে, “জামে কাম কি কামে জাম’। (চর্যা ২২)
কি শব্দের আরো প্রয়োগ “না” শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ঘটে। দুইপদ যুক্ত হইয়া একই সঙ্গে সংশয় ও প্রশ্ন দুইটাই সূচনা করে।
“কি” আরও অর্থে প্রয়োগ করা চলে। সুকুমার সেনের পাঁচ নম্বর অর্থ বুঝাইতে সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী বিভক্তি আকারে ইহার প্রয়োগ হয়। এই অর্থে ইহা সংস্কৃত “কৃত” শব্দের পরিবর্তন হইতে আসিয়াছে। উদাহরণ : ব্রজবুলি হইতে ‘চাঁদ কি চলনা’, হেমচন্দ্র হইতে, ‘অব বাপ্পকি ডুম্মুড়ি’(= বাবার জমিটুকু)।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি উচ্চারণের যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা এই বাবদ ধন্যবাদ পাইতেছেন। কিন্তু শ্বাসাঘাতের যে যুক্তি তাহারা দ্বিতীয় অবয়বস্বরূপ হাজির করিয়াছেন তাহাও নিতান্ত খোঁড়া যুক্তি। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে প্রেতের বানান বলিয়াছিলেন তাহার পেছনের যুক্তিই নতুন মুখোশ পরিয়া হাজির হইল মাত্র। কিভাবে, দেখাইতেছি। কথায় বলে দুর্বৃত্তের ছলের অভাব নাই।
‘বাঙলা বানানবিধি’পুঁথিযোগে পরেশচন্দ্র মজুমদার যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এই মুখোশের সেলাইরেখা দেখা যাইবে। পরেশচন্দ্র দেখাইতেছেন :
“প্রথমেই মনে রাখা দরকার, সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব/দীর্ঘ ভেদ আছে। বাঙলাতেও আছে। কিন্তু উভয়ের গুণগত পার্থক্য যথেষ্ট। সংস্কৃতে এই গুরু-লঘু ভেদ শব্দের অর্থান্তর ঘটায়, যেমন, দিন : দীন, চির : চীর, কুল : কূল ইত্যাদি। কাজেই সংস্কৃতে হৃস্বদীর্ঘভেদ ধ্বনিমানসূচক (Phonemic)। বাঙলা শব্দের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অবস্থানমূলক অর্থাৎ স্বরের অবস্থান অনুযায়ী এই ভেদ ঘটে; যেমন, ‘তিন, হিম, চিল’ ইত্যাদি শব্দের ই-কার উচ্চারণে দীর্ঘ, কিন্তু রিপু, ভীষণ’ইত্যাদি শব্দে ই-স্বর হ্রস্ব। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ‘প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে স্বর রুদ্ধ (Closed), কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মুক্ত (Open)। কিন্তু লক্ষণীয়, অবস্থান অনুযায়ী বাঙলা স্বরমাত্রার হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ থাকলেও এর বিপর্যয় অর্থান্তর ঘটায় না। কাজই বাংলায় এই ভেদ ধ্বনিমানসূচক (Phonemic) নয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার যথার্থ প্রবণতা হলো হ্রস্ব মাত্রার উচ্চারণ। উচ্চারণে এবং বানানে সমতা আনা উচিত।” (বাঙ্লা বানানবিধি, পৃ. ২৮)
পশ্চিমবঙ্গে “কি” ও “কী” তফাত উপপাদ্যের পাঁচআনি নেতা পবিত্র সরকার। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন : “স্বরচিহ্নের মধ্যে দীর্ঘ ঈকার ও দীর্ঘ ঊকারের উচ্চারণ বাংলায় নেই। অর্থাৎ এই উচ্চারণ ফোনিমিক নয়। এর সহজ অর্থ হল, স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে অর্থ পাল্টাচ্ছে, এমন শব্দের দৃষ্টান্ত বাঙলায় নেই।” (বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃ. ৪৭) এই কারণেই বাংলা বানানের সংস্কারে মনীন্দ্রকুমার ঘোষ যাহাকে বলেন ‘হ্রস্ব-ইকার প্রবণতা’ তাহার জয় হইতেছে। ইহার কৃতিত্ব বহুলাংশে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথা মানিতে হইবে।
পবিত্র সরকারও দেখিয়াছেন সত্য লোকের মধ্যে স্বীকৃতিও পাইতেছে : ‘স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ ফোনিমিক না হওয়ার দরুন আলোচ্য শব্দগুলিকে উচ্চারণ-অনুগ করতে গিয়ে দীর্ঘ ঈকার দীর্ঘ ঊকারের জায়গায় হ্রস্ব ইকার হ্রস্ব উকার লেখা চলছে, এবং এ ধরনের প্রয়োগ ক্রমশ বেশি লোকের কাছে গৃহীত হচ্ছে।’ (বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃ. ৪৭)
এত বাক্য ব্যয় করিবার পরও পায়ে টিকা দিয়া পবিত্র সরকার পুনশ্চ যোগ করিতে ভুলিলেন না, “বাংলা উচ্চারণে ই ও ঈ-র মধ্যে কোনো তফাত নেই।” (বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃ. ১৫১) জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রসিদ্ধ ‘বাংলা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে এই মূলনীতির অবতারণাই করিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও তীব্র ব্যঙ্গে মিশাইয়া কহিয়াছিলেন, “মাকে মা বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই মা বলিতে যাওয়া দোষের হয়। সেইরূপ বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না।” (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ১১২)
পবিত্র সরকার মহাশয়ও রবীন্দ্রনাথের বৃত্তি করিয়া লিখিয়াছেন : “সংসদ বাঙ্গলা অভিধান’-এর সম্পাদক মাঝে মাঝে “বাংলা ঈ” প্রত্যয় জুড়ে শব্দ তৈরি করেছেন, যেমন “অদরকারী”। মনে রাখতে হবে এসব প্রত্যয় তৈরি হয়েছে মুখের ভাষায়, আর মুখের ভাষায় দীর্ঘ ঈ বলে কিছু নেই। সুতরাং ওটা সোজাসুজি ই-প্রত্যয়।” (বাংলা বানান-সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা পৃ. ১৫১)
এতখানি যাঁহার জ্ঞানগরিমা, এতখানি যাঁহার বিচারবুদ্ধি তিনিই পরক্ষণে লিখিতে বসিলেন, ‘তবু “কী” ‘কি’ দুভাবে লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা আমরা সমর্থন করি। ‘কী’ কর্মপদের স্থান নেয়, কিংবা বিশেষণের বিশেষণ (intensifier) হিসাবে কাজ করে। ‘কি’ হ্যাঁ-না প্রশ্নের সূচক। দুটির ভূমিকা ও তাৎপর্য-আলাদা, ধ্বনিগত চরিত্রও আলাদা।’ (পৃ. ১৫১)
এখন আমরা কি করি? কিংকতর্ব্যবিমূঢ় ছাড়া আর কি বা হই!
সারকথা এই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি দুই নম্বর যে অবয়ব দেখাইয়াছেন তাহা আপাদমস্তক স্ববিরোধিতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রলোকের জন্য শিক্ষাপ্রদ হইবে না। পবিত্র সরকার মহোদয়কে বাংলা ভাষা আর কে শিখাইবে? শুদ্ধ ইংরেজি হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিবার ধৃষ্টতা করি।
সরকার মহাশয় যদি রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ ভাল উল্টাইয়া দেখিতেন, খুঁজিয়া পাইতেন ‘কি’শব্দের কর্তৃ (অভিহিত) পদে যে রূপ কর্মপদেও সেই রূপ অপরিবর্তিত থাকে। ইহার রূপ অধিকরণে ‘কিসে’ এবং ‘কিসেতে’, সম্বন্ধপদে ‘কিসের’। রামমোহন রায় বাংলা ভাষায় সম্প্রদান ও অপাদান পরিণাম স্বীকার করেন নাই। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৮)
সুতরাং ‘কর্মপদের স্থান নেয়’এই যুক্তি চলে না। বিশেষণের বিশেষণ হইলেও রূপান্তর হইবার কোন কারণ হয় না। যুক্তি একই। যদি না আপনি ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজশেখর বসুর প্রস্তাবে- অর্থাৎ বেশি জোর দিতে ফিরিয়া না আসেন। সেই যুক্তি তো অচল। তাহা আপনি মানিয়াছেন আর পরেশচন্দ্র মজুমদারও মানিয়াছেন। মানিয়াছেন দুই জনেই।
এক্ষণে ইংরেজিতে আসিতেছি। ইংরেজিতে অনেক ক্রিয়ার সহিত একটি প্রত্যয়ের যোগসাজশ করিয়া বিশেষ্য বা সংজ্ঞা তৈয়ার হয়। যথা- break হইতে breakage। drainage, leakage প্রভৃতিও এইরূপে গড়া হয়।
কতক আছে যাহাতে মূল ক্রিয়া শব্দে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটাইয়া যোগক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যেমন : approval, arrival, refusal। কতকে আবার করিতে হয় না, যেমন : acceptance, appearance, performance, delivery, discovery, recovery, agreement, arrangement, employment, departure, failure। কতকে আবার করিতে হয়, যথা : collision, decision, division, education, organisation, attention, solution, closure ইত্যাদি।
কতক ইংরেজি বিশেষ্য গঠিতে হয় বিশেষণ হইতে, যথা: importance, absence, presence, ability, activity, equality, darkness, happiness, kindness, length, strength, truth ইত্যাদি।
কতক উদাহরণ পাওয়া যায় যাহাতে একই শব্দ উচ্চারণ বা বানান কোনটি না বদলাইয়াই যুগপৎ বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ করা যায়। আবার ক্রিয়ার ভাড়ার হইতেও তাঁহাদের বিয়োগ করা চলে না। উদাহরণের তালিকা দীর্ঘ হইবে, আমি কয়েকটি দিতেছি :
aim, answer, cause, change, doubt, dream, end, fall, guess, hope, influence, interest, joke, laugh, lock, move, note, order, plan, play, quarrel, result, smile, stop, talk, trouble, walk, work ইত্যাদি।
আবার কতক শব্দ আছে যাহাদের প্রয়োগ অনুসারে উচ্চারণ বদলায় কিন্তু বানান আদৌ বদলাইবে না। যখন শব্দটি বিশেষ্য ব্যবহার্য হইবে তখন উহার শেষ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অঘোষ (voiceless) হইবেক। আর ক্রিয়ায় ব্যবহার্য হইলে একই ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সঘোষ (voiced) হইবেক। যথা : abuse শব্দের উচ্চারণ বিশেষ্য অবস্থায় “এবিয়ুস” (abuse/s) আর ক্রিয়া অবস্থায় উচ্চারণ “এবিয়ুজ” (abuse/z)। একই রকম উচ্চারণভেদ হইবে house, excuse, use শব্দে।
কতক শব্দে উচ্চারণভেদে বানানও ভেদ হইয়া থাকে, যেমন advice (বিশেষ্য), advise (ক্রিয়া) ইত্যাদি। কতক শব্দে ইংল্যান্ডের ইংরেজিতে বানানভেদ হইলেও বিশেষ্যে আর ক্রিয়ার উচ্চারণে ভেদ নাই, যেমন practice (বিশেষ্য) practise (ক্রিয়া)। দুই শব্দই শেষ ব্যঞ্জনে অঘোষ থাকে।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি উচ্চারণে বল (stress) প্রয়োগের যুক্তি দেখাইয়াছেন। বাংলায় ‘কি’ ও ‘কী’ উচ্চারণের কোন ভেদ নাই। বলের অভিঘাতের আলাদা করার জায়গা নাই। দুইটার ফলই সোজাসুজি ‘ই’। তাঁহারা লিখিয়াছেন, ‘উচ্চারণে হ্যাঁ-না প্রশ্নের “কি”তে বল (stress) নেই। কিন্তু অন্য “কী”তে আছে। তাতেও এ দুটি পৃথক হয়ে যায়।” (বিধি ১২.২) ধরণী দ্বিধা না হইলেও দুঃখ নাই। কি ও কী দ্বিধা হইবেন।
ইংরেজি ভাষায় বিস্তর শব্দ পাওয়া যায় যাহাদের উচ্চারণকালে শ্বাসাঘাত বা বলের স্থান পরিবর্তন হয় কিন্তু বানানের পরিবর্তন হয় না। যদি বল প্রথম দলে (syllable) প্রযুক্ত হয় তখন শব্দটি বিশেষ্য পদবাচ্য হয়। আর বল দ্বিতীয় ভাগে সরিয়া যায় তো শব্দটি ক্রিয়া হইয়া যায়। উদাহরণ : accent (শ্বাসাঘাত)।
শব্দটি যদি বলি ‘The/accent in this noun falls on the first syllable’ (এই বিশেষ্যটির প্রথম ভাগে শ্বাসাঘাত হইবে) তখন শ্বাসাঘাত পড়িতেছে a অক্ষরের আগে, নির্দেশ করা স্থানে। আর যদি ক্রিয়াবিশ্বাসে বলি ‘We ac/cent this verb on the second syllable’ (এই ক্রিয়াটির দ্বিতীয় ভাগে শ্বাসাঘাত পড়িয়া থাকে) তবে শ্বাসাঘাত পড়িবে দ্বিতীয় c অক্ষরটির আগে, নির্দেশ করা জায়গায়।
এই রকম শব্দের তালিকা নাতিদীর্ঘই হইবে। যেমন : abstract, addict, ally, attribute, combine, compress, concert, conduct, conflict, conscript, contest, contract, contrast, converse, convert, convict, decrease, desert, dictate, digest, discount, discourse, entrance, /envelope (বিশেষ্য), en/velop (ক্রিয়া), escort, essay, exploit, export, extract, import, impress, incense, increase, insult, abject, perfume, permit, present, produce, progress, project, prospect, protest, rebel, record, retail, subject, survey, suspect, torment, transfer, transport ইত্যাদি। (R.A. Close, A Reference Grammar, pp. 107-08)
উচ্চারণের যুক্তিবিচার করিয়া বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি বা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কেহই প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই “কি” শব্দের বানান ক্ষেত্র (বা প্রয়োগ) বিশেষে “কী” কেন লিখিতে হইবে। তাঁহারা জানেন রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছিলেন, ‘আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিশেরও জোর।’ তাই তাঁহারা উপরওয়ালার দ্বারে দ্বারে দস্তক ও পুরস্কার ভিক্ষা করিয়া বল সংগ্রহের পথ ধরিয়াছেন।
বাংলাদেশে সরকারের বিশেষ পুলিশ বাহিনির হেফাজতে বন্দির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিলে মন্ত্রণালয় যে যুক্তি সচরাচর দিয়া থাকেন তাহা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।
তুমি কি জাতি?
‘অনধিকার চর্চায় অব্যবসায়ীর যে বিপদ ঘটে আমারও তাই ঘটিয়াছে।’
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৩২)
‘ভাষার স্বরূপবিচারে একদেশদর্শী সংস্কর্তাদের অভিলাষও যথার্থ দিগ্দর্শনের কাজ করে না। ভাষার সৃষ্টিশীল প্রধান লেখকগণের উৎকৃষ্ট রচনারীতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেই সেই ভাষা-প্রবাহের মৌল প্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে, তার ক্রমবিবর্তনের স্বকীয় ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করতে হবে।’
- মুনীর চৌধুরী, (বাংলা গদ্যরীতি, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩)
এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কি তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়াইবে? গড়াইলে গড়াইবে। কিন্তু বিচার করেন কে? আমরা কমলাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়কে বিচারকর্তা মানিতে প্রস্তুত আছি। কারণ বাংলাদেশের উচ্চ-আদালত বাংলা ভাষার সমজদার নহেন। তাঁহারা এই মামলা শুনিবেন না।
খোসনবীস জুনিয়ার প্রণীত বিবরণীতে দেখা যাইতেছে ওই আফিঙ্গখোর কমলাকান্ত মহাশয় এতদিনে আদালতপাড়ায় হাজির আছেন। তিনি ফরিয়াদি নহেন। চুরিও করেন নাই। দোষের মধ্যে এক আফিঙ্গ। তিনি অন্তত সাক্ষী তো হইবেন।
‘এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার- পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে- সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।
কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল-“হাস কেন?”
কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, “বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?”
চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাঁড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, “তামাসার জায়গা এ নয়- হলফ পড়।”
কমলাকান্ত বলিল, “পড়াও না বাপু।”
একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, “বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ...”।
কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?
মুহুরি। শুনতে পাও না-“পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে!”
কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!
হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “সর্ব্বনাশ কি?”
কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি- এ কথাটা বলতে হবে?”
হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই।
কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম- কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?
হাকিম। এর আর মিথ্যা কি?
কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, “তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?” প্রকাশ্যে বলিল, “ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চশমা নাকে দিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন- কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না- তখন কেমন করিয়া বলি- আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে-”
আমি এক্ষণে কিছু অংশ ছাড়িয়া দিতেছি। উকিল সাহেব চটিলেন বটে তবে হাজার হোক মোয়াক্কেলের স্বার্থ দেখিতে হয়। সাক্ষীকে মনে করাইয়া দিলেন, ‘এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।’অর্থাৎ মিথ্যা বলুন। হাকিমের হস্তক্ষেপে খানিক পর আবার জেরা শুরু হইল।
কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, “বহুৎ খুব।” উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, “তোমার নাম কি?”
কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।
উকীল। তোমার বাপের নাম কি?
কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি?
উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, “হুজুর! এসব Contempt of Court! হুজুর, উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন- বলিলেন, “আপনারই সাক্ষী।” সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, “বল। বলিতে হইবে।”
কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জাতি?”
কমলা। আমি কি একটা জাতি?
উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়।
কমলা। হিন্দু জাতীয়।
উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ?
কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।
উকীল। দূর হোক ছাই। এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে?
কমলা। মারে কে?
হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় কাজ হইবে না। বলিলেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত- তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর?
কমলা। ধর্ম্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা। দেখিতেছেন, আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী- ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?
হাকিম লিখিলেন, “জাতি ব্রাহ্মণ।” তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বয়স কত?”
এজলাসে একটা ক্লক ছিল- তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, “আমার বয়স একান্ন বৎসর, দুই মাস তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট-”
আবার উকিল সাহেবের উষ্মা হইল। আমি খানিক লাফ দিয়া সামনে যাইতেছি। জেরা চলিতেছে।
উকীল। এখন আছ কোথা?
কমলা। কেন এই আদালতে।
উকীল। কাল ছিলে কোথা?
কমলা। একখানা দোকানে।
হাকিম বলিলেন, ‘আর বকাবকিতে কাজ নাই- আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তারপর?’
উকীল। তোমার পেশা কি?
কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে?
উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?
কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি। (বঙ্কিম রচনাবলী, খণ্ড ২, পৃ. ৯০-৯২)
বস্তুত শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে জেরা করা শামলা গায়ের আমলা উকীলের কর্ম্ম নহে। ভাগ্যের মধ্যে বানান সংস্কর্তা আমলারা কি পূর্বে কি পশ্চিমে কমলার মতো সাক্ষীর পাল্লায় এখনও পড়েন নাই। তাই তাঁহারা ধরাকে সরাই ভাবিতেছেন।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই জনকেই উদীয়মান শক্তিরূপে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদের সাক্ষ্য অনুসারে তাঁহারা উভয়েই বঙ্কিমের প্রতিভার অনতিক্রমনীয় প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ৮০ বছর আগের রবীন্দ্র সংবর্ধনা বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, “বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর ফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাঁহার আবির্ভাব একটি যুগদৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথ আজও ক্রমশঃ উর্দ্ধলোকে আরোহণ করিতেছেন।’ আমরা যোগ করিব, আজও এই আরোহণ অব্যাহতই আছে।
সামান্য ‘কি’ শব্দের বানান লইয়া তিনি যে অসামান্য জিদ করিয়াছিলেন, তাহা অবিস্মরণীয়। ভুলিলে চলিবে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাংলা বানানে হ্রস্ব ই-কারের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে কর্ণধারের ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোঃপূত কর্ণধার সুনীতিকুমার করেন নাই। ‘কি’ বানান দীর্ঘ ঈ-কারযোগে লিখিবার জেদাজেদিতে তাঁহার এই কীর্তি খানিক ম্লান হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে কীর্তিনাশা হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কালের যাত্রার ধ্বনি এই জেদ ভুলিতে আমাদের সহায় হইবে।
কোন মহান স্রষ্টার কীর্তি তাহার ছোট কিছু জেদের কাছে কিছুতেই ম্লান হইতে পারে না। ঢাকা ও কলিকাতার দুই বাংলা অনুষ্ঠান যাহা করিতেছেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গৌরব বাড়িতেছে কি?
বাংলা কি শব্দের বানান বদলাইয়া অর্থের তফাত সৃষ্টির চেষ্টা যে চিন্তার উপর দাঁড়াইয়াছে সেই চিন্তা অসার। এই অসারতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। ১৯৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত ও পরে পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী দেখিতেছি আকাদেমির বানানবিধিতে একটি প্রস্তাব ছিল এই উপলব্ধির সাক্ষী: ‘অতৎসম শব্দে হ্রস্ব-ইকার আর দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে বিশেষ্য বিশেষণরূপের স্বাতন্ত্র্য দেখানোর দরকার নেই। অর্থাৎ আমার খুশি/আমি খুশী তৈরি করা/তৈরী বাড়ি এ রকম কোনো প্রভেদ করা নিষ্প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই হ্রস্ব ই-কারের প্রয়োগ চলুক।” [বানানবিধি ৭.২০; মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম, পৃ. ১৭৩-৭৪]
বানানবিধি ৫ম সংস্করণ হইতে ইহা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে ইহাতে ঐ জাতীয় প্রভেদের অনুমোদন করা হইয়াছে বলিয়া ভুল করিবার সম্ভাবনা নাই। কালের অবধি নাই, পৃথিবীও বিপুলা কম নহেন।
ঢাকার বাংলা একাডেমী এই প্রশ্নে কিছু না লিখিলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) গৃহীত বাংলা বানানরীতিতে (১৯৮৮) এই ভুল চিন্তার উৎস কোথায় তাহা আজও দেখা যাইতেছে। বোর্ডের ১০ নং সুপারিশে বলা হইয়াছিল, “অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন, কি (অব্যয়), কী (সর্বনাম); তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ); নিচ (নিু অর্থে) নীচ (হীন অর্থে); কুল (বংশ অর্থে), কূল (তীর অর্থে)।” (আনিসুজ্জামান, পাঠ্যপুস্তকের বানান, পৃ. ১০৬; শফিউল আলম, প্রসঙ্গ: ভাষা বানান শিক্ষা, পৃ. ৭৪)
আনিসুজ্জামান, মাহবুবুল হক প্রভৃতি লেখকের বই পড়িয়া মনে হইতেছে ইঁহারা এখনও সেই অর্থভেদ উপপাদ্যের নিচেই মুখ থুবড়াইয়া আছেন। (আনিসুজ্জামান, পাঠ্যপুস্তকের বানান, পৃ. ৩৩-৩৭; মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম, পৃ. ১৪৩-১৪৪)
এই অসার যুক্তি বা জেদের প্রকোপে রবীন্দ্রনাথও একদা “নীচ” ও “নিচ” শব্দে ভেদ করিতে তাগাদা দিয়াছিলেন। নীতিশাস্ত্রের বিচারে কেহ মন্দ বিবেচিত হইলে দীর্ঘ ঈকারযোগে “নীচ” আর পদার্থশাস্ত্রের অর্থে কেহ নিম্নে পতিত হইলে “নিচ” হইবেন। ইহাই ছিল ঠাকুরের ধারণা। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯০) এই ধারণার সমাধি বহু আগেই হওয়া উচিত ছিল। বাংলা ভাষায় ইকারের প্রবণতা অনুসারে উভয় অর্থেই শব্দটির বানান “নিচ” হইতে পারে। সংস্কৃত বাদিপক্ষের বিচারে হয়তো উভয় অর্থেই শব্দটি “নীচ”ই ছিল। (মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাংলা বানান, পৃ. ৭৬-৭৮) তাহাতে কিছু আসে যায় না। (দিনেন ভট্টাচার্য, বানানের রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৬০-৬১)
এইখানে আমাদের স্থলাভাব হইয়াছে। তাই মাত্র সংক্ষেপে, ইঙ্গিতে লিখিতেছি। যে বানানেই লিখিবেন না কেন, বাংলায় নীতিশাস্ত্র ও পদার্থশাস্ত্র দুই শাস্ত্রেই এক বানানে “নিচ” কথাটা লেখা যাইবে। কারণ “নিচ” শব্দের যথার্থ অর্থ ভূমিতে “নিম্নস্থল” নৈতিক অর্থে “নিম্নমর্যাদা” তাহার ব্যঞ্জনা মাত্র। দুর্ভাগ্যের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ ইহা ধরিতেই পারেন নাই। তাই তাঁহার জেদাজেদি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় কবি সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এক ধরনের বাক্যভ্রংশ বা এফেসিয়া (aphasia) হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহা কুলসঞ্চারিরোগ কিনা জানি না। (‘যে রোগ পিতামাতা হইতে পুত্রপৌত্রে যায়’ তাহাকে আয়ুর্বেদে “সঞ্চারিরোগ” বলে।’ -বিজয়চন্দ্র মজুমদার।) অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্মৃতিভ্রংশ’ রোগটা ধরনে ছিল রোমান এয়াকবসন কথিত সামঞ্জস্য-বৈকল্য (similarity disorder) বা ব্যঞ্জনালোপ ব্যাধির মতন। ঢাকা ও কলিকাতার সরকারি পণ্ডিতদের মাথায় তাহা কুলসঞ্চারি (hereditary) বিমারস্বরূপ বর্তাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। (R. Jakobson, ‘Two Aspects,’ pp. 54-82)
ইহাদের উদ্দেশে আমার আজিকার শেষ আবেদন, ভাবিয়া দেখুন। স্বয়ং কবিরই যেখানে চিকিৎসা দরকার সেখানে আপনারা রোগ নির্ণয়ই করেন নাই। উপরন্তু গোটা বাংলা ভাষাকেই রোগদোষে দুষিত করিতেছেন। কবি যদি কোন বিষয় বুঝিতে না পারিয়াও থাকেন আমাদের কি উচিত হইবে তাঁহার এই অগৌরবের দিকে সারাক্ষণ তাক লাগাইয়া চাহিয়া থাকা? কবিকে সম্মান জানাইবার ইহাই কি শ্রেষ্ঠ পন্থা?
যে মানুষের একটি চোখ নষ্ট হইয়াছে তাহাকে কানা বলে কেন? চোখের ব্যবহার সীমারেখায় পৌঁছিলে কানের ব্যবহার বাড়িয়া যায়। এই লোকসংস্কার সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক এক চোখা লোককে কানা বলাই তাই রীতি। আপনারাও কি কানা হইলেন না? শুদ্ধ কানকথায় কান দিলেন, চোখের দেখা দেখিলেন না?
পণ্ডিত কৃষ্ণপদ গোস্বামীও দুর্ভাগ্যক্রমে মনে করিতেন অর্থভেদের জন্য “কি” ও “কী” আলাদা করা যাইতে পারে। তবে তিনিও খেয়াল করেন নাই শব্দের ব্যঞ্জনা আসে তাহার বানান হইতে নহে। ব্যবহার হইতে। ব্যবহারই ব্যঞ্জনা নহে, কিন্তু ব্যবহারেই ব্যঞ্জনা।
যদি না হইত তবে গোস্বামী নিজেই কি লিখিতেন এই কথাগুলি? ‘বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস’ গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, “অকল্যাণকর বা কুৎসিত অর্থবাচক কোন শব্দকে ভদ্রভাবে প্রকাশ করিবার সময় অনেক সময় সুভাষণ অলঙ্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়। চাউল বা ভাত না থাকিলে স্ত্রীলোকেরা ‘চাল বাড়ন্ত’, ‘ভাত বাড়ন্ত’ ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে। উত্তর ভারতে পাচক ব্রাহ্মণকে বলা হয় মহারাজ, বাংলায় বলা হয় ঠাকুর।” (পৃ. ১০৮)
পাচক শব্দের উৎপত্তি অনুসারে জাতি যৌগিক। পচ্ ধাতুর সহিত অক প্রত্যয় লাগাইয়া বাংলায় পাচক হইয়াছে। কিন্তু ‘পচেগা’মানে হিন্দিতে ‘পরিপাক হইবে’ বুঝাইলেও বাংলায় বুঝাইতেছে ‘পচিয়া যাইবে’। এক ধাতু হইতে বহু শব্দ ও বহু অর্থ হয়। ‘অক’প্রত্যয়ের অর্থ কর্তৃত্ব ধরিলে পাচক মানে পচনের উপর যাহার কর্তৃত্ব আছে বোঝায়। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র। তিনি লিখিয়াছেন, অনেক সময় বুৎপত্তি ভিন্ন হইলেও ধ্বনি বিচারের দিক দিয়া এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় মিলিয়া যাইতেছে দেখা যায়, কোন রূপভেদ হয় না ; ‘কিন্তু ভাষাভেদে অর্থভেদ ঘটে’। (বাংলাভাষা, পৃ. ২৯৪-৯৫)
সংস্কৃতে তীর অর্থ কূল বা পাড়, ফারসিতে তীর অর্থ শর বা বাণ। বানান বদলাইয়া কূল পাইবেন না। বাংলায় দুই তীরই সমান তীরন্দাজ। এক তীর হইতে তীর ছুড়িয়া অন্য তীরে নিতুই যাইতে পারেন।
রবীন্দ্রনাথ প্রাজ্ঞ বয়সে (পৌষ ১৩২৬) একবার স্বীকার করিয়াছিলেন, ‘অনধিকার চর্চায় অব্যসায়ীর যে বিপদ ঘটে আমারও তাই ঘটিয়াছে।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৩২)
যাহার বিপদ ঘটে এবং যিনি সেই বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া বয়ান করেন- দুইজন কি একই ব্যক্তি। যদি তাহারা দুইজনই হইয়া থাকেন, তাহাদের কি কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়? দোহাই ১. আকাদেমি বানান উপসমিতি (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ) সম্পাদিত, আকাদেমি বানান অভিধান, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫)।
২. আনিসুজ্জামান, পাঠ্য বইয়ের বানান, সংশোধিত ও পরিমার্জিত (জিয়াউল হাসান) সংস্করণ, (ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০০৫)।
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ২য় খণ্ড,তীর্থপতি দত্ত সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা : তুলি-কলম, ২০০১)।
৪. কৃষ্ণপদ গোস্বামী, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ২য় (পরিবর্ধিত) সংস্করণ, (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০০১)।
৫. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯২২-২১ মার্চ ১৯৩২, ১ম খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩)।
৬. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ২য় (পরিবর্ধিত) সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯)।
৭. টেকচাঁদ ঠাকুর, আলালের ঘরের দুলাল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ৮ম (পরিষৎ) সংস্করণ (কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪০৫)।
৮. দিনেন ভট্টাচার্য, বানানের রবীন্দ্রনাথ (কলকাতা : ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৪১০)।
৯. নির্মল দাশ, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ (কলকাতা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭)।
১০. নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, বানান বিতর্ক, ৩য় (পরিবর্ধিত, পবিত্র সরকার) সংস্করণ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭)।
১১. নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ২য় (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত) সংস্করণ, (কলকাতা : নব চলন্তিকা, ২০০১)।
১২. পবিত্র সরকার, বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, (কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৭)।
১৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙ্লা বানানবিধি, পরিবর্ধিত সংস্করণ (কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৮)।
১৪. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, বাংলাভাষা, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা : জিজ্ঞাসা এজেন্সিস, ১৯৯৮)।
১৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, ১৪শ মুদ্রণ (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৪০৯)।
১৬. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি, ২য় মুদ্রণ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪)।
১৭. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাংলা বানান, ৪র্থ (দে’জ) সংস্করণ (কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৪০৯)।
১৮. মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম, ৭ম মুদ্রণ (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮)।
১৯. মিতালী ভট্টাচার্য, বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন (কলকাতা : পারুল প্রকাশনী, ২০০৭)।
২০. মুনীর চৌধুরী, বাঙ্লা গদ্যরীতি, ২য় সংস্করণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৮৩)।
২১. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৪০৭)।
২২. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ভাষা ও সাহিত্য, ৩য় (সংশোধিত) সংস্করণ (ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ১৯৪৯)।
২৩. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা ব্যাকরণ, নতুন সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮)।
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলাভাষা পরিচয়, পুনর্মুদ্রণ (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৭৫)।
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা শব্দতত্ত্ব, ৩য় (স্বতন্ত্র) সংস্করণ (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯১)।
২৬. রমাপ্রসাদ চন্দ, ‘কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম’, বসুমতী, ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪৪।
২৭. রামমোহন রায়, ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’, রামমোহন গ্রন্থাবলী, ৭ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ (কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৮০)।
২৮. সলিমুল্লাহ খান, ‘বাংলা বানানের যম ও নিয়ম’, নতুনধারা, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭।
২৯. সুকুমার সেন, বুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩)।
৩০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মনীষী স্মরণে, দ্বিতীয় প্রকাশ (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা এজেন্সিস, ১৩৯৬)।
৩১. শফিউল আলম, প্রসঙ্গ : ভাষা বানান শিক্ষা (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০০২)।
৩২. হরনাথ ঘোষ ও সুকুমার সেন, বাঙ্লা ভাষার ব্যাকরণ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (কলিকাতা : ভিক্টোরিয়া বুক ডিপো, ১৩৫৬)।
৩৩. R.A. Close, A Reference Grammar for Students of English, 15th ed. (Burnt Mill, Harlow: Longman, 1990).
৩৪. G. A. Grierson, Maithili Dialect, Part 1, Grammar, 2nd ed., cited in জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯)।
৩৫. Roman Jakobson, ‘Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances,’ in R. Jakobson and M. Halle, Fundamentals of Language, pp. 54-82 (Leiden: Mouton, 1956). প্রথম প্রকাশ : শিল্পসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা ‘নতুনধারা’, ৮ম সংখ্যা, ১ আষাঢ় ১৪১৭/১৫ জুন ২০১০, সম্পাদক : নাঈমুল ইসলাম খান।
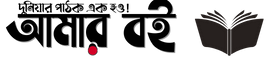

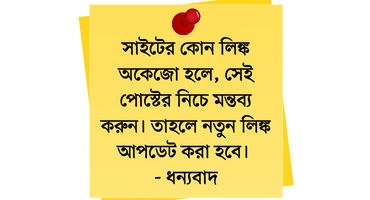







![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)








